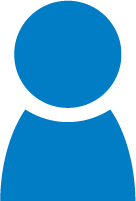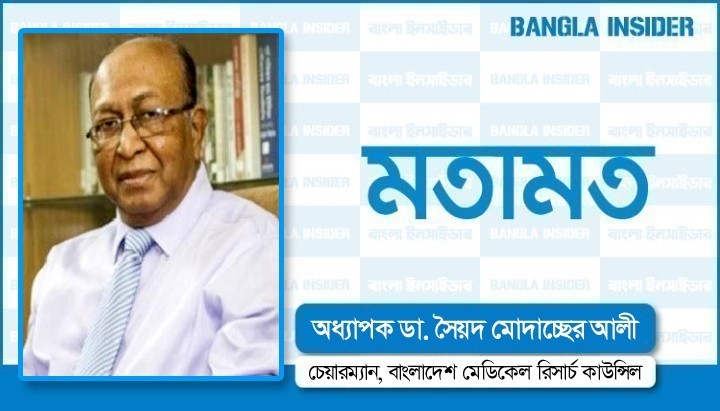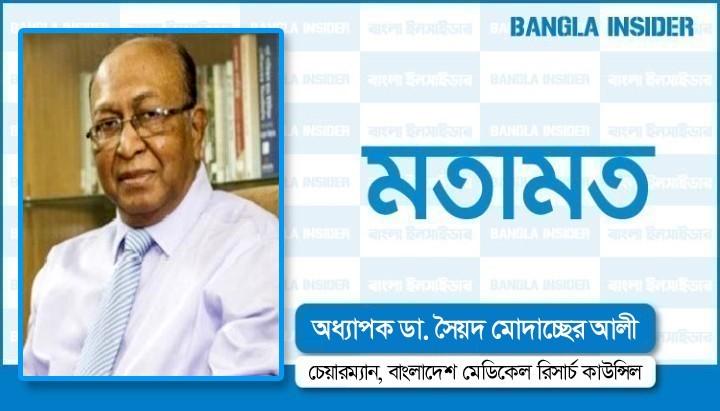‘এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।/তাপসনিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে/ বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক/যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে-যাওয়া গীতি/ অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক/ মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,/ অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।’ অর্থাৎ ১৪৩১ বঙ্গাব্দে পুরাতন স্মৃতি মুছে যাক, দূরে চলে যাক ভুলে যাওয়া স্মৃতি, অশ্রুঝরার দিনও সুদূরে মিলাক। আমাদের জীবন থেকে বিগত বছরের ব্যর্থতার গ্লানি ও জরা মুছে যাক, ঘুচে যাক; নববর্ষে পুরাতন বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক। রমজান ও ঈদের পর দেশের মানুষের জীবনে আরো একটি উৎসবের ব্যস্ততা নতুন বছরে মঙ্গল শোভাযাত্রায় উদ্ভাসিত।ফিলিস্তিনবাসীর উপর হামলা আর ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে এর মধ্যে মারা গেছেন অসংখ্য মানুষ।তবু মৃত্যুর মিছিলে জীবনের গান ফুল হয়ে ফুটেছে। যুদ্ধের সংকট আমাদের পরাস্ত করতে পারেনি কারণ পৃথিবীর মৃত্যু উপত্যকা পেরিয়ে এদেশে বৈশাখ এসেছে নতুন সাজে।
১৪ এপ্রিল বাংলাদেশের নববর্ষ। টি এস এলিয়টের ভাষায় ‘এপ্রিল নিষ্ঠুরতম মাস’, দেখা যাচ্ছে কবির কথাই সত্য। তাপদাহে এই এপ্রিলই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। তবে এই এপ্রিল আমাদের বৈশাখি/বৈসাবি/বিজু উৎসবের মাস- খররৌদ্র আর তীব্র ঝড়ের মাস হলেও। বৈশাখকে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন ‘মোহন ভীষণ বেশে’, দেখেছিলেন ‘অতলের বাণী খুঁজে পাওয়া মৌনী তাপসরূপে’। অন্য কবি লিখেছেন- ‘রৌদ্রতপ্ত বৈশাখে তুমি চাতকের সাথে চাহ জল/আম কাঁঠালের মধুর গন্ধে জ্যৈষ্ঠে মাতাও তরুতল/ঝঞ্ঝার সাথে প্রান্তরে মাঠে কভু খেল লয়ে অশনি।’ বৈশাখে এই ‘অশনি’র খেলা নিশ্চয় কারো কাছে প্রত্যাশিত নয়।
বিশ্ব পরিস্থিতির সংকট আমাদের বৈশাখি আয়োজনের মধ্যে গরল উগড়ে দিলেও অতি সহজ-সরল, প্রশান্ত কিন্তু উদ্দীপনাময় আয়োজন এবারও। এখন আমরা প্রাণিত, আমাদের চিত্ত আনন্দিত এবং আমাদের চেষ্টা অব্যর্থ। অতীতের মতো এবারও সকালে হালখাতা খুলে দোকানে বসবে ব্যবসায়ী, বৈশাখি মেলায় নাগরদোলা, পুতুলনাচের উৎসবে শিশুদের কোলাহল শোনা যাবে। প্রতিবছর যেসব থিম অনুসারে সারাদেশে মঙ্গলশোভা যাত্রা অনুষ্ঠিত হতো তাও এবার হবে। রমনার বটমূলের প্রত্যুষের ছায়ায় আয়োজিত ছায়ানটের অনুষ্ঠান এবারও হচ্ছে।আর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নতুন বছরকে বরণ করার জন্য তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানও শুরু হয়েছে।‘পাচন’ আর ‘পুণ্যাহে’র মতো নানাবিধ ব্রত ও বিধি পালনের সকল প্রথা অনুসৃত হচ্ছে।একসময় ভারতবর্ষে হিজরি পঞ্জিকা অনুসারে কৃষি ফলনের খাজনা আদায় করা হতো। ফলে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল কৃষিকাজে ফসল না থাকলেও নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা দিতে বাধ্য হতো কৃষকরা। খাজনা আদায়ের সময়টিকে কৃষকদের জন্য সহনীয় করতে প্রবর্তিত হয় ‘ফসলি’ সন। আসলে হিজরি সনের উপর ভিত্তি করে নতুন সনের নিয়ম প্রচলন করা হয়েছিল। ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১০ মার্চ বা ১১ মার্চ থেকে বাংলা সন গণনার শুরু। তবে এই গণনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয় আকবরের সিংহাসন আরোহণের সময় (৫ নভেম্বর, ১৫৫৬) থেকে। ক্রমান্বয়ে ফসলি সন বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষ নামে পরিচিত লাভ করে।
বাংলা নববর্ষ তথা পহেলা বৈশাখ বাঙালির সর্বজনীন উৎসব। বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনটি সূচনা হয় সূর্যোদয়ের প্রত্যুষে। কাজেই সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় বাঙালির পহেলা বৈশাখের উৎসব। ষাটের দশকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রতিবাদে ১৯৬৭ সাল থেকে ২০২৩ অবধি ছায়ানটের রমনার বটমূলে বর্ষবরণ আয়োজন হয়ে এসেছে। অন্যদিকে নব্বই দশক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে পহেলা বৈশাখ সকালে মঙ্গলশোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণের সূচনা হয়। মঙ্গল শোভাযাত্রাটি ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হওয়ার পর সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমানের উৎসাহে ২০১৩ সাল থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পহেলা বৈশাখের উৎসবের একটি অন্যতম আকর্ষণ হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে চৈত্র সংক্রান্তির দিন পালিত হয় চড়কপূজা অর্থাৎ শিবের উপাসনা। একইসঙ্গে ওইদিন গ্রামবাংলায় আয়োজিত হয় চড়ক মেলা।
নববর্ষের সকল আনন্দ, উৎসব ও অনুষ্ঠান আয়োজনের কথা স্মরণ করেও আমরা আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি, সংকটে আক্রান্ত বিশ্বে আমাদের কাছে এখন বেঁচে থাকার গৌরব অত্যন্ত বেশি। নিকট আত্মীয় হোক, দূরের বন্ধু হোক, দিনে হোক, দিনের অবসানে হোক, আমরা এখন ভালোভাবে বেঁচে থাকতে চাই। সংকট এলে কী করি, কীভাবে অগ্রসর হই, কোথায় যাই, কোথায় সেবা করে আত্মবিসর্জন করতে হবে, এটাই শান্তচিত্তে আমরা খুঁজছি। ১৪ এপ্রিল শুরু হওয়া নতুন বছরের আগে ছিল কাজ, অকাজ, অকারণ কাজ, যে উপায়েই হোক, জীবনের শেষ নিমেষপাত পর্যন্ত ছুটাছুটি করে, মাতামাতি করে বেঁচে থাকা। ওই কর্ম-নাগরদোলার ঘূর্ণিনেশা আমাদের পেয়ে বসেছে বলেই পৃথিবী হয়েছে শান্তিতে পূর্ণ। অবশ্য দুর্গম হিমালয়শিখরের নিরুদ্বিগ্ন প্রাণিদের জীবন বিপন্ন; জনশূন্য তুষারমরুর বিশ্বস্তচিত্ত সীল এবং পেঙ্গুইনদের নির্বিরোধে প্রাণধারণ করার সুখটুকু বিলীন এখন। বাণিজ্যপুঁজি ও শিল্পপুঁজির দাপটে আফ্রিকা আর দক্ষিণ-আমেরিকার প্রত্যন্ত দরিদ্র অঞ্চলেও আধুনিকতার নামে মৃত্তিকাসংলগ্ন সভ্যতার তিরোধান ঘটেছে। বিচিত্র কর্মের পিছনে মানুষের ছুটে চলার বিপরীতে রয়েছে নির্জন প্রকৃতির স্তব্ধতা। তার রূপ অক্লিষ্ট অক্লান্ত, তার সাজগোজ বিস্তীর্ণ নীলাকাশ থেকে অরণ্যের সবুজে প্রসারিত। প্রকৃতি নিজেকে চিরকাল প্রকাশমান রেখেছে, মানুষের মতো ঊর্ধ্বশ্বাস কর্মের বেগে নিজেকে অস্পষ্ট করে তোলেনি। মানুষের কর্মের চতুর্দিকে অবকাশ ও চাঞ্চল্যকে ধ্রুবশান্তির দ্বারা মথিত করে সে চিরনবীনের বার্তাবাহক। এই একুশ শতকেও গ্রামীণ জীবনের প্রাধান্যের মধ্যে বাঙালি হিসেবে রাতদিনের কর্মযজ্ঞে ইউরোপ-আমেরিকার মতো আমাদের ব্যস্ত থাকার কথা নয়। এখনো প্রকৃতির উদার শান্তি, বিশাল স্তব্ধতার মধ্যে আমরা পরিভ্রমণ করতে পছন্দ করি। এজন্যই বৈশাখের তপ্ত আকাশ, তার শুষ্ক ধূসর প্রান্তরের নীরব মধ্যাহ্ন, নিঃশব্দ রাত্রি অথবা ঝড়ো হাওয়ার আলিঙ্গনে আমাদের জীবন মুখরিত হয়।
আজকের দিনের বহু আড়ম্বর, আস্ফালন, করতালি, মিথ্যাবাক্য, যা আমাদের স্বরচিত, যাকে বাংলাদেশের মধ্যে আমরা একমাত্র সত্য, একমাত্র বৃহৎ বলে মনে করছি, সেই কর্পোরেট কালচারের ঢেউ থেকে বের হয়ে আসতে হবে। কারণ নববর্ষ সকলকে একই কাতারে নিয়ে আসে। সেখানে শ্রমজীবী আর বুদ্ধিজীবী একসঙ্গে চলেন, প্রত্যেকে নিজকে এবং জগৎকে ঠিকভাবে দেখতে পান, উৎসবের মধ্য দিয়ে সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে মিলনলাভ সম্ভব হয়। উৎসবের আয়োজনে ব্যক্তিগত ভোগের নিবিড়তা নেই বরং বৈশাখি আনন্দ আত্মীয়-স্বজন-প্রতিবেশীর মধ্যে ব্যাপ্ত করে দিয়েছে মহত্ত্ব। নববর্ষের আনন্দ আমাদের ঘরকে, মনকে, সমাজকে কলুষের ঘনবাষ্প থেকে অনেকটা পরিমাণে নির্মল করে রাখে, দূষিত বায়ুকে বদ্ধ করে রাখে না এবং মলিনতার আবর্জনাকে একেবারে গায়ের পাশে জমতে দেয় না। পরস্পরের কাড়াকাড়িতে ঘেঁষাঘেঁষিতে যে রিপুর দাবানল জ্বলে উঠে উৎসবে তা প্রশমিত থাকে; কর্মের সঙ্গে শান্তিকে জড়িত করে রেখে বৈষম্যহীন সমাজ তৈরি করে। উৎসব আমাদের শিখিয়েছে মানুষ বড়ো, পদ বড়ো নয়; দারিদ্র্য লজ্জাকর নয়, সকল কর্মে, সকল অবস্থাতেই সহজে মাথা তুলে রাখা যায়। আমাদের দেশে স্বস্থানের নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সকলেই আপনার নিশ্চিত অধিকারটুকুর মর্যাদা ও শান্তি লাভ করে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর ধনি হওয়ার প্রচেষ্টা অন্যকে ছোটো করে দেখার দৃষ্টি তৈরি করে দেয় না। এজন্য নববর্ষের উৎসব সর্বজনীন।
এসেছে পহেলা বৈশাখ, ৩০ চৈত্রে ১৪৩০ বঙ্গাব্দ বিদায় নিয়েছে। এজন্য- ‘উড়ে যাক, দূরে যাক বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা/বিপুল নিঃশ্বাসে।’ রবীন্দ্রনাথ ‘নববর্ষ’ প্রবন্ধে লিখেছেন- ‘পুরাতনই চিরনবীনতার অক্ষয় ভাণ্ডার।...নূতনত্বের মধ্যে চিরপুরাতনকে অনুভব করিলে তবেই অমেয় যৌবনসমুদ্রে আমাদের জীর্ণ জীবন স্নান করিতে পায়।’ এই ‘চিরপুরাতন’ হলো আমাদের চিরায়ত ঐতিহ্য। আজকের এই নববর্ষের মধ্যে বাঙালির বহুসহস্র পুরাতন বর্ষকে উপলব্ধি করতে হবে। কারণ সেখানে রয়েছে সম্রাট আকবর কর্তৃক বঙ্গাব্দ প্রচলনের ইতিহাস, সেখানে আছে গ্রামীণ বাংলার হালখাতা আর বৈশাখি মেলার আয়োজন, আছে বাঙালি জমিদারদের পুণ্যাহের উৎসব। ফসলের ঘ্রাণে গড়ে ওঠা আমার নববর্ষ শাশ্বত ও গৌরবের। নববর্ষে বৈশাখের খররৌদ্রে অগ্নিস্নানে শুদ্ধ হয়ে উঠুক আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র। ‘হে নূতন, এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি/পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে-/ ব্যাপ্ত করি, লুপ্ত করি, স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে/ ঘনঘোরস্তূপে।’ ‘ঘনঘোরস্তূপে’ নতুনের এই আহ্বান প্রকৃতপক্ষে সংকট কবলিত বাঙালির জীবনে প্রত্যাশার অভিব্যক্তি। এ মুহূর্তে আমরা পৃথিবীতে যতটুকু কাজ করি তা যেন সত্যসত্যই দায়িত্ব পালনের জন্য করি, ভান না করি। কারণ অক্ষমরা বৃহৎ কাজ করতে পারে না বরং বৃহৎ ভানকে শ্রেয়স্কর জ্ঞান করে। জানে না যে মনুষ্যত্বলাভের পক্ষে বড়ো মিথ্যার চেয়ে ছোটো সত্য ঢের বেশি মূল্যবান। এই সত্য পথে হেঁটে আমরা নববর্ষের চেতনায় সংকট জয় করব। আর এই বৈশাখেই মানবজীবনকে অশান্তি মুক্ত করার শপথ নিতে হবে। কারণ- বৈশাখে ‘মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে’।
লেখক: ড. মিল্টন বিশ্বাস, বঙ্গবন্ধু গবেষক, অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশিষ্ট লেখক, কবি, কলামিস্ট, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রগতিশীল কলামিস্ট ফোরাম, নির্বাহী কমিটির সদস্য, সম্প্রীতি বাংলাদেশ email-drmiltonbiswas1971@gmail.com)