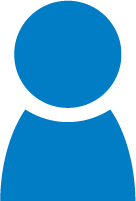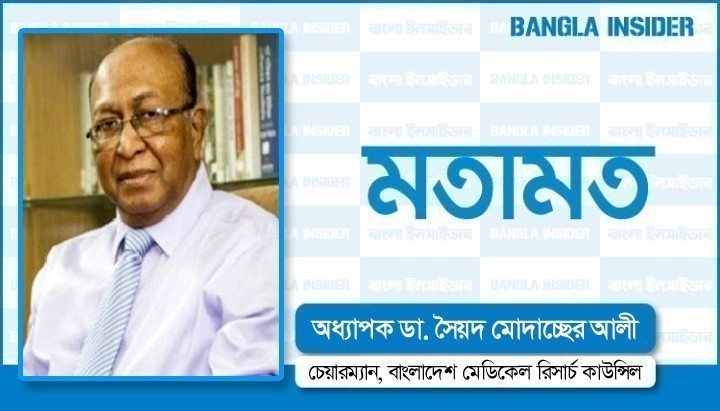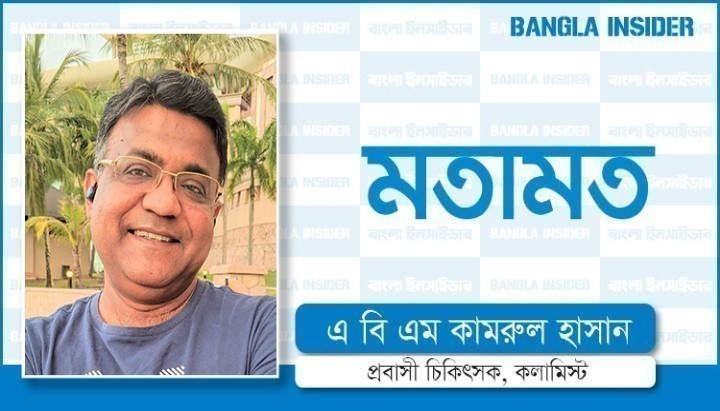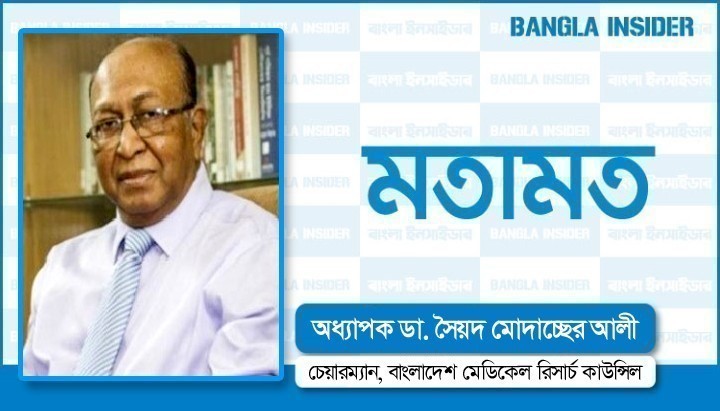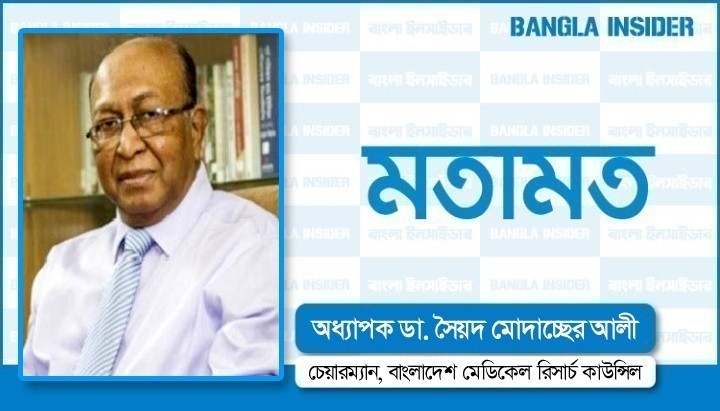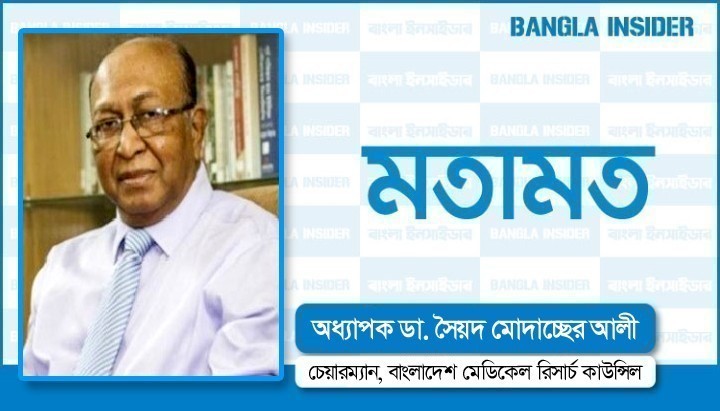বাংলাদেশের জাতীয় সংবিধান এদেশের জনগণকে দেশের মালিক বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। সংবিধানের ৭ নং অনুচ্ছেদে স্পষ্ট উল্লেখ আছে- প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। অনুচ্ছেদ ২১ এর (১) বলা আছে- সকল সময়ে জনগণের সেবা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। গণতান্ত্রিক বিধান অনুযায়ী সরকার ও তার প্রশাসন দেশের জনগণের সেবার উদ্দেশ্যেই তাদের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবে। মানুষের জান ও মালের ওপর কর্তৃত্ব করা নয়, বরং জনসাধারণের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সব ধরনের সেবা নিশ্চিত করাই সরকার ও তার প্রশাসনের কাজ। কিন্তু বর্তমান অভিজ্ঞতার চিত্র পুরো উল্টো। মালিক আজ নেমে গেছে কর্মচারী-শ্রমিকের কাতারে। উপনিবেশিক রাজত্বের মতো যেন কর্মচারী বনে গেছে যেন দেশের মালিক। জনসাধারণের ওপর কর্তৃত্বপরায়ণ প্রভুর মতোই ছড়ি ঘোরাচ্ছে তারা সব সময়। জনগণ শুধু নয়, খোদ সরকারও অনেকটা যেন জিম্মি হয়ে পড়েছে তাদের কাছে।
বলছি, দেশে চলমান আমলাতন্ত্রের আগ্রাসী অবস্থার কথা। আমলাদের সীমাহীন দৌরাত্মে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে যেন সবাই। সচিবালয় ও মাঠ পর্যায়ে আমলাতন্ত্রের দাপটে চারদিকে তৈরি হয়েছে চরম হতাশা। শোনা যায়, অনেক সচিবই মন্ত্রীদের গুরুত্ব দেন না (!)। সিদ্ধান্ত নেন নিজেদের মতো করে। এমন একটা ভাব নিয়ে চলাফেরা করেন তারা যে, মন্ত্রী যাবেন, মন্ত্রী আসবেন, কিন্তু তাদের ক্ষমতার কোনো কমতি হবে না তারা চিরস্থায়ী জমিদার সরকারী কর্মচারী। বরং দিনকে দিন পদ-পদবী আরো বাড়বে তাদের। বাড়বে আরো কর্তৃত্ব। উপেক্ষিত মন্ত্রী, এমপি ও জনপ্রতিনিধি দুঃখ করেন রাজনৈতিক মহলে। সচিবদের দৌরাত্মের কাছে যেন এক প্রকার অসহায় তারা। তাদের ক্ষমতা শুধুমাত্র সরকারী কর্মচারীদের কাছে তদবির করার মধ্যে সীমিত।
প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র সচিবালয়ের মতো মাঠ পর্যায়েও কর্মরত অনেক প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনপ্রতিনিধিদের তোয়াক্কা করেন না। সরকারের ভেতর তারা যেন সেজে বসেছে আরেক সরকার। তাদের ইচ্ছে ও অনুগ্রহ ছাড়া যেন কিছুই হয় না। জনপ্রতিনিধিদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে কেউ কেউ অতি উৎসাহ নিয়ে যোগ দেন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে। অনেক কর্মকর্তাই নিজের অতীত রাজনৈতিক অবস্থান তুলে ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রশাসনিক ক্ষমতার সাথে সাথে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রদর্শন করে নিজের কর্তৃত্ব আরো বাড়িয়ে নিতে চান। তারা আচরণে, কার্যক্রমে চলেন রাজনীতিবিদদের মতো করে। আমলাদের সীমাহীন ক্ষমতা প্রদর্শন করার কারণে মন্ত্রী, এমপি, সিটি মেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যান ও পৌর মেয়ররা অনেক সময় নিজের কর্মীদের কাছে অসহায়ত্ব প্রকাশ করেন। অথচ এদেশের সংবিধান সেই ক্ষমতা বা অধিকার কোনটাই দেয়নি আমলাদের।
বাংলাদেশের সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য (২) দফায় বলা হয়েছে: ‘সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।’ কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আমলারা জনগণের সেবা করার পরিবর্তে জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টায় মরিয়া সব সময়। নিজেদেরকে তারা সব সময়ই সাধারণ মানুষের তুলনায় সুপেরিয়র মনে করে। সাধারণ জনগণকে বাধ্য করে তাদেরকে ‘স্যার’ বলে সম্বোধন করতে। অথচ দেশের মালিক সাধারণ এ জনগণের পকেটের টাকাতেই তাদের বেতন হয়, স্ত্রীর শাড়ি-গয়না হয়, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ নির্বাহ হয়। কর্মচারী হিসেবে দেশের মালিক জনগণকে যেখানে ‘স্যার’ বলে সম্বোধন করার কথা তাদের, সেখানে নিজেরাই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ববলে স্যার সেজে বসে থাকে। শুধু বসেই থাকে না, চারপাশ নিয়ন্ত্রণ করে ব্যাপকভাবে।
সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জে একজন ইউএনও’র কার্যক্রমে দেশবাসী হতবাক হয়েছে। মাহামরি করোনার এ চলমান সংকটকালে অভাবে পড়ে ফরিদ আহমেদ নামের একজন লোক সরকারি তথ্যসেবা নাম্বার ৩৩৩ এ কল করে খাদ্য সহায়তা চেয়েছিলেন। ইউএনও সাহেব খাদ্য নিয়ে তার বাড়িতে পৌঁছেও ছিল। কিন্তু লোকমুখে উক্ত ব্যক্তির একটি বাড়ি আছে, এমন কথা শোনার সাথে সাথে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন ইউএনও সাহেব। খাদ্য সহায়তা তো তাকে করলেনই না, উল্টো ১০০ জনকে তার খাদ্য সহায়তা দিতে হবে মর্মে জরিমানা ঘোষণা করলেন কোনোরকম যাচাই বাছাই ছাড়াই! খাদ্যের অভাবে পড়া লোকটি বাধ্য হয়ে স্ত্রীর গয়না বন্ধক রেখে সুদের ওপর টাকা তুলে ষাট হাজার টাকা খরচ করে চোখের পানি মুছতে মুছতে সেই জরিমানা পরিশোধ করলেন। হ্যাঁ, বাড়ি তার একটি রয়েছে বটে। তবে সে বাড়ির মালিক তিনি একা নন। ভাইবোনদের সাথে এজমালি মালিকানা রয়েছে তার বাড়িটির ওপর। মাত্র তিনটি কক্ষের ওপর মালিকানা তার। তিনি একটি হোসিয়ারী ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে চোখ খারাপ হয়ে যায় এবং বিভিন্ন রোগের কারণে এখন ঠিকমত কাজ করতে পারেন না। এখন প্রায় মাসে ৫ হাজার টাকা আয় করেন। দীর্ঘ এক বছর ধরে চলমান করোনা সংকটের কারণে ব্যবসাপত্র বন্ধ থাকা কাজ হারিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ঘরে বসেছিলেন তিনি। নিতান্ত অনন্যোপায় হয়েই সরকারি সহায়তা নম্বরে কল দিয়েছিলেন। কিন্তু তার প্রকৃত অবস্থা যাচাই করার মতো এত সময় ও ধৈর্য ইউএনও মহোদয়ের কোথায়! বাড়িওয়ালা শুনেই তিনি জরিমানা করে বসলেন! অথচ এভাবে ১০০ জনকে খাদ্য বিতরণের নির্দেশ দেওয়ার মতো অধিকার দেশের আইন তাকে দেয়ই না। বিষয়টা নিয়ে সারা দেশে যখন নানারকম আলোচনা সমালোচনার জন্ম হলো, তখন করা হলো একটি তদন্ত কমিটি। জেলা প্রশাসনের করা সেই কমিটি নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা আরিফা জহুরাকে দায়মুক্তি দিয়ে স্থানীয় ইউপি মেম্বার আইয়ুব আলীকে দায়ী করে প্রতিবেদন জমা দিলো। উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে কাকে বলে আর। অন্যায় জরিমানাটা করলেন ইউএনও সাহেব আর এর জন্য দায়ী করা হলো স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ইউপি সদস্যকে!তাকে অভিযুক্ত করা হলো, তিনি নাকি সময়মতো প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহায়তা করেননি। কী অদ্ভুত এ তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন।
নারায়ণগঞ্জের এ ঘটনা শুধু ছোট্ট একটি উদাহরণ। সারা দেশে এমন ঘটনা অহরহ ঘটছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা মাঠ প্রশাসনের সামনে অসহায়। কী মেম্বার, কী চেয়ারম্যান, কী এমপি। ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তারা কাউকেই সমীহ করে না। শুধু সচিব নয়, যুগ্ম সচিব, মুখ্য সচিব, অতিরিক্ত সচিব, কারো প্রতাপের সমানেই যেন দাঁড়ানো যায় না। তাদের ভাবখানা এমন যেন, জনপ্রতিনিধি বা রাজনীতিবিদরা নয়, সরকারে টিকিয়ে রেখেছে তারাই। রাজনীতিবিদদের চেয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তারাই যেন সর্বেসর্বা।প্রথম আলোর সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের সাথে সচিবালয়ে ঘটা ঘটনাটা সাম্প্রতিক সময়ে সচিবদের দৌরাত্মের অন্যতম বাজে উদাহরণ। নিয়মিত সংবাদ অনুসন্ধান করতে গেলে নজিরবিহীনভাবে সচিবালয়ে ৬ ঘন্টাব্যাপী রোজিনাকে আটকে রাখেন একজন অতিরিক্ত সচিব সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। তার সাথে কী দুর্ব্যবহার যে তারা করেছেন সে সময়ে, তার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে বিভিন্ন মাধ্যমে। একজন নারী কর্মকর্তাকে দেখা গেছে, তিনি টুটি চেপে ধরছেন সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের। শুধু সাংবাদিক রোজিনার টুটি নয়, সেদিন তিনি যেন গোটা দেশের সব গণমাধ্যমের, সব মানুষের টুটিই চেপে ধরেছিলেন আদতে। শুধু টুটি চেপে ধরে তাকে নির্যাতন করেই ক্ষ্যান্ত হননি তারা। শেষপর্যন্ত অফিশিয়াল সিক্রেট এ্যাক্ট নামের এক ব্রিটিশ আইনে যারা শুধুমাত্র সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেই আইনে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তাকে। অথচ ব্রিটিশদের বানানো এ আইন খোদ ব্রিটিশরাও বাতিল করেছে বহু আগেই। কিন্তু এদেশের আমলারা সেই আইন ইতিহাসের আস্তাকূড় থেকে টেনে তুলে এনে তার জালেই আটকে দিলেন সাংবাদিক রোজিনাকে। কী এমন তথ্য নিয়ে পেয়েছিলেন রোজিনা! যে তথ্যের জন্য এমন মারমুখী হয়ে উঠলো আমলারা? হাজার রকম প্রশ্ন ঘুরপাক খায় জনমনে। কিন্তু এসব প্রশ্নের কে চাইবে কার কাছে। প্রজাতন্ত্রের দেশ হয়ে উঠেছে আজ আমলাতন্ত্রের দেশ। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ঐ অতিরিক্ত সচিব যিনি নাটের গুরু যার কানাডার ৩ টি বাড়ি, লন্ডনে ১ টি, ঢাকায় ৪ টি ফ্লাট রয়েছে আর রয়েছে ৮০ কোটি টাকার সঞ্চয়, কিন্তু তার কোনো শাস্তি হয়নি। শুধু বদলি হয়েছেন মাত্র অন্য মন্ত্রণালয়কে ধ্বংস করার জন্যে কোটি টাকা লুটপাটের জন্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের ড্রাইভারের শাস্তি হয় তবে তার কর্তা ব্যক্তি যেন তুলসী পাতা।
আমলাতন্ত্র এখানে এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, আমলাদের ছাড়া না হয় কোনো সিদ্ধান্ত, না হয় কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি। করোনার এ সংকটকালে মন্ত্রীদের বাদ দিয়ে জেলা পর্যায়ে কমিটি করা হয়েছে সচিবদের নিয়ে। সচিবরাই যদি সব করবে, তবে মন্ত্রী, এমপি বা জনপ্রতিনিধিরা রয়েছে কী জন্য? প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের এত ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব দিলে জনপ্রতিনিধিরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে সাধারণ মানুষ থেকে। লোকজন যখন বুঝবে, এমপি মন্ত্রীর আসলে কোনো কাজ নেই। কাজকর্ম, ক্ষমতা যা আছে, তা সব ওই প্রশাসনিক ব্যক্তিদের হাতে। তখন তারা বিভিন্ন প্রয়োজনে রাজনীতিবিদ-জনপ্রতিনিধিদের কাছে ছুটে যাওয়ার অভ্যাস বাদ দেবে। আবার আমলা-প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাছেও ভিড়তে পারবে না সহজে। উভয়দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে সাধারণ মানুষ। মধ্য থেকে আরো ফুলেফেঁপে উঠবে আমলাতন্ত্র। আর জনগণ সরকারের প্রতি আস্তা হারাবে জনরোষ পুনরুজ্জীবিত হবে।
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সব সময়ই আমলাতন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দানকালে তিনি বলেছিলেন, ‘সরকারি কর্মচারীদের বলি, মনে রেখো, এটা স্বাধীন দেশ। এটা ব্রিটিশের কলোনি নয়। পাকিস্তানের কলোনি নয়। যে লোককে দেখবে, তার চেহারাটা তোমার বাবার মত, তোমার ভাইয়ের মতো। ওরই পরিশ্রমের পয়সায় তুমি মাইনে পাও। ওরাই সম্মান বেশি পাবে। কারণ ওরা নিজেরা কামাই করে খায়।’ বঙ্গবন্ধু দেশের মানুষকে দেশের মালিক মনে করতেন। আর আমলাদের মনে করতেন মালিকদের সেবার উদ্দেশ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারী। কর্মচারীর কাজ সব সময় সেবা দিয়ে মালিককে সন্তুষ্ট রাখা।বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশিক দমনমুলক আইন-কানুন পরিবর্তন করে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রের রূপ দিতে। আমলাতন্ত্রের মূল দর্শন পরিবর্তন করে, স্বাধীন বাংলাদেশে একটি জনমুখী আমলাতন্ত্র তৈরি করতে, যার মূল চেতনাই হবে জনগণের সেবা করা। দমন বা শাসন করা নয়। সেই লক্ষ্যে, বঙ্গবন্ধু প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের গুরুত্ব কম দিয়ে জনসম্পৃক্ত মানুষদেরকে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়েছিলেন, যাতে সাধারণ মানুষ সরকারের সেবা পায়। বঙ্গবন্ধু তার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য- তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা কমিশন’ গঠন করেছিলেন। এ কমিশনই বাংলাদেশের প্রথম পাঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। সেই কমিটিতে আমলাদের আধিক্য দেখা যায়নি। ছিলেন চার বা তারও অধিক অর্থনীতিবিদ ও অধ্যাপক। বঙ্গবন্ধু অনেক রাজনৈতিক নেতা ও শিক্ষককে সে সময় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যেমন অধ্যাপক কবির চৌধুরীকে শিক্ষা সচিবের দায়িত্ব দিয়েছিলেন ডা: টি রহমানকে স্বাস্থ্য সচিবের দায়িত্ব দেন। ১৯৭২ সালে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয় সেগুলো পরিচালনা করার জন্যে অনেক ব্যবসায়ী ও দলীয় কর্মীকে নিয়োজিত করেছিলেন - যারা ইতোপূর্বে কখনো প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছিলেন না কিন্তু, জনগণের কাছের মানুষ ছিলেন। অথচ আজকের কর্মচারীরা এমনভাবে মালিকের আসনে চেপে বসেছে যে, চারপাশের সবাই রীতিমত কোণঠাসা হয়ে পড়েছে তাদের দৌরাত্মের কাছে। বঙ্গবন্ধু জেলায় জেলায় ” জেলা গভর্নর” নিয়োগ করেন যার অধিকাংশই ছিলেন জন প্রতিনিধি। বড় বড় দেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেন জনপ্রতিনিধিদের। যেমন লন্ডনে এডভোকেট সৈয়দ সুলতান, ওয়াশিংটন জনপ্রতিনিধি এম আর সিদ্দিকী, নয়াদিল্লীতে অধ্যাপক ড. এ আর মল্লিক প্রমুখ।
করোনা মহামারির এ সময়ে নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে দেশের মানুষের জন্য কাজ করছেন ডাক্তারগণ। পরিবার-পরিজন, ছেলে-মেয়ে সবার কথা ভুলে দিন রাত মানুষের সেবায় পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তারা। এমন একটি সময়ে মুভমেন্ট পাশ থাকার পরও একজন ডাক্তারকে পথে যেভাবে হেনস্তা করলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, যেভাবে তার পরিচয়পত্র প্রদর্শন করতে বলেন, তা কোনোভাবেই আইনের আওতার মধ্যে পড়ে না। সিনিয়র উক্ত ডাক্তার নিজেকে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বলে পরিচয় দেওয়ার পরও প্রকাশ্যে জনসম্মুখে তার সাথে যেভাবে আর্গুমেন্ট করলেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, তা তাদের ক্ষমতার দৌরাত্ম্যকে আরো একবার স্পষ্ট করে তোলে। কোন ক্ষমতার বলে এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেন একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা? তাকে হেয় করার জন্যে রাজাকারের ছেলে হয়েও জোর গলায় দাবী করেন তিনিও মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। তার জন্যে তার গুরুতর শাস্তি হওয়া উচিত। তবে তার শাস্তি হয়নি, তিনি শুধুমাত্র বর্তমান পদ থেকে বদলি হয়েছেন।
সরকার যখন লড়াই করছে করোনা মহামারি মোকাবেলায়, ডাক্তার ও অন্যান্য পেশাজীবীগণ আপ্রাণ চেষ্টা করছেন পরিস্থিতি মোকাবেলায়, তখনও থেমে নেই স্বাস্থ্যখাতের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দুর্নীতি ও দৌরাত্ম্য। আমলাতন্ত্রের মারপ্যাঁচে স্থবির হয়ে পড়েছে আজ দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। আমলাদের অতিরিক্ত খবরদারির কারণে দেশের করোনা চিকিৎসা বারবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এমনকি জনপ্রতিনিধিদের পাশ কাটিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে চাপিয়ে দেয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তে করোনা চিকিৎসাও ব্যাহত হয়েছে। বিশেষজ্ঞ কমিটিসহ বিভিন্ন টেকনিক্যাল কমিটিকে পাশ কাটিয়ে মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিরা ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত নেয়ায় আলোচনা-সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে সরকারকে বারবার। এ কাজগুলো করেছে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ কতিপয় স্বার্থান্বেষী কর্মকর্তা। তারা এতই দাপুটে যে মন্ত্রীকেও পাশ কাটিয়ে একের পর এক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যাতে মন্ত্রীকে হতে হয়েছে বিব্রত। বলতে হয়েছে তিনি এসব সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিছু জানেন না। তাকে না জানিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এমন বক্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী মিডিয়াতে বারবার দিয়েছেন। মন্ত্রী-সচিব দ্বন্দ্বে স্বাস্থ্য খাতে বিরূপ প্রভাব পড়েছে। সমন্বয়হীনতা এখন গোটা স্বাস্থ্যখাত জুড়ে। সচিবদের দৌরাত্বে এ সমন্বয়হীনতা যেন আরও বেড়েছে। বাংলাদেশের পাসপোর্ট থেকে ইসরাইল নাম বাদ পড়েছে যা কোনো মন্ত্রী মিনিস্টার জানেন না, বাদ দিয়েছেন আমলাকুল।
অদ্ভুত ব্যাপার হলো এসব আমলা-প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দৌরাত্ম্য যতই বাড়ুক, কিছুই হয় না তাদের। সব সময়ই ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যান তারা। নারায়ণগঞ্জের জরুরি খাদ্য সহায়তা কেলেঙ্কারিতে ইউএনওকে বাদ দিয়ে স্থানীয় জনপ্রনিধিকে অভিযুক্ত করা হয়, রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পে বালিশ দূর্নীতির দায়ে মামলা হয় ঠিকাদারের নামে। অথচ দায়িত্বপ্রাপ্ত আমলারা ছাড়া কারো বাপেরও সাধ্য নেই এসব প্রকল্পে কোনো দুর্নীতি করে। প্রকল্প পরিচালকসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের যোগসাজশ ছাড়া কারো পক্ষে কোনো প্রকল্প থেকে একটি সুতোও অন্যায়ভাবে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। যদি নেয়ও, তা দেখার দায়িত্ব কিন্তু ওইসব কর্মকর্তাদের ওপরই বর্তায়। যেকোনো প্রকল্পে দুর্নীতির দায় প্রকল্পের পরিচালক কখনোই এড়াতে পারেন না। কিন্তু দেখা যায়, যখনই এমন কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা সামনে আসে, তখন প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের আড়াল কেউ তৃতীয়পক্ষ বা অপেক্ষাকৃত দুর্বল পক্ষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এর দায়ভার।
করোনা ভাইরাসের এ মহামারির সময়ে দেশের জনগণের পাশে সবচেয়ে বেশি থাকার সুযোগ রয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিগণের। কিন্তু দেখা গেল, ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাহায্য প্রদান কার্যক্রমে জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত না করে জেলা পর্যায়ে সচিবদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ঠিক কীসের ভিত্তিতে এ দায়িত্ব পেলেন সচিবগণ? না তারা জনগণের সাথে সম্পৃক্ত, না আছে তাদের কোনো দায়বদ্ধতা জনগণের কাছে। মাঠ পর্যায়ে সাধারণ মানুষের প্রকৃত অবস্থা কী সরকারি অফিসে বসে থেকে সেটাও জানার কথা নয় তাদের। ফলাফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাদের হাতে ন্যস্ত করায় সাধারণ জনগণ বঞ্চিত হয়েছে কাঙ্ক্ষিত সুবিধা প্রাপ্তী থেকে। এর ফলে জনপ্রতিনিধিরা অসহায় জনগণকে ঠিকভাবে সহযোগিতা করতে পারেননি। সরকারের বরাদ্দ ঠিকই হয়েছে, কিন্তু সেই অনুযায়ী প্রকৃত অসহায়দের কাছে পৌঁছায়নি সহায়তা।
সরকারের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা, নানা মহতী উদ্যোগ সবকিছুই ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে আমলাতন্ত্রের এ লাগামহীন ঘোড়া। জাতির জনকের জন্মশতবার্ষিকী তথা মুজিববর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম মহতী উদ্যোগের একটি হলো গৃহহীনদের জন্যে একটি ঘর প্রকল্প। কিন্তু এই প্রকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ব্যাপক দুর্নীতির ফলে পুরো উদ্যোগটিই সমালোচনার মুখে পড়েছে। জনপ্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে সরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের এ প্রকল্পে দায়িত্ব দেওয়ায় নজির বিহীন দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে দুঃস্থ মানুষদের আশ্রয়ের নিমিত্তে নির্মাণ করা এসব ঘরে। বহু এলাকায় ঘর নির্মাণের পরপরই ধ্বসে পড়েছে, ভেঙে পড়েছে বহু ঘর। গৃহহীনদের ঘর প্রদানের এ প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে বলে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। অথচ এর জন্য কখনো কোনো আমলা বা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বিচারের আওতায় আনা হয়নি। সরকারের মহতী উদ্যোগের সুফল খেয়ে যাচ্ছে আমলাতন্ত্রের বিষপিঁপড়ারা!
আমলা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দুর্নীতির অসংখ্য ফিরিস্তি হাজির করা যায়। বলতে গেলে আমলাদের অধীনে ছেড়ে দেওয়া সকল প্রকল্পই যেন একেকটি দুর্নীতি ও লুটপাটের আখড়া। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি টাকা ব্যয় করে রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয় বাংলাদেশে। ইউরোপে একেবারে নতুন চার লেনের মহাসড়ক নির্মাণের খরচ পড়ে কিলোমিটার প্রতি ২৮ কোটি টাকা। চীনে কিলোমিটার প্রতি খরচ পড়ে মাত্র ১৩ কোটি টাকা, ভারতে ১০ কোটি টাকা! বাংলাদেশে একইরকম একটা সড়ক নির্মাণ করতে খরচ করা হয় কিলোমিটার প্রতি ১০৮ কোটি টাকা! ইউরোপের চেয়ে প্রায় ৪গুণ বেশি। চীনের চেয়ে ৮গুণ বেশি। ভারতের চেয়ে ১১গুণ বেশি। পৃথিবীর সকল দেশের চেয়ে বেশি খরচ করে রাস্তা বানালে কী হবে, এসব রাস্তার স্থায়িত্ব যে সব দেশের চেয়ে কম, সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এক দিকে নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার আগেই অন্যদিক থেকে ভাঙা শুরু হয় এসব রাস্তা! সড়ক নির্মাণের প্রতিটি প্রকল্পে কী পরিমাণ অর্থ নয়ছয় হয়, তা বিশ্বের অপরাপর দেশের নির্মাণ ব্যয়ের সাধারণ চিত্রের সাথে তুলনা করলে সহজেই বোঝা যায়। বছরের পর বছর ধরে একই কায়দায় সড়ক নির্মাণের নামে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করে চলেছে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ আর তাদের পাপের ফল ভোগ করেন জনপ্রনিধিগণ। ভাঙাচোরা রাস্তাঘাটের কারণে জনগণের মুখোমুখি হতে পারে না তারা।
কেন আমলারা থাকেন সব সময় ধরাছোঁয়ার বাইরে, কেন কোনোভাবেই তাদেরকে অভিযুক্ত করা যায় না, বা করা হয় না? নানা সময়ে এক স্বাস্থ্যখাতের যেসব দুর্নীতি অপকর্মের ফিরিস্তি প্রকাশিত হয়েছে, তার কোনটির জন্যই কখনো কোনো আমলা বা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে দেখা যায়নি। সব মন্ত্রণালয়, সব অধিদপ্তর গুলোর অবস্থাও স্বাস্থ্যখাতের মতোই। সব কলকাঠি নাড়েন আমলারা, অথচ তারা থাকেন সব সময় যেন তুলসী গাছের তলায়! পুতঃপবিত্র ভাব ধরে বসে থাকলেও আদতে তারা একেকজন তুলসী তলার ভূত!
কী শিক্ষক, কী ডাক্তার, কী উকিল, কী মোক্তার, কী সাধারণ মানুষ সবার উপরেই পড়েছে আমলাতন্ত্রের ভূতের আছর। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা যেন সব দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসেছেন।প্রকাশ্যে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান একজন ডাক্তারকে হেনস্তা করেন ম্যাজিস্ট্রেট! একবারও তার কর্তৃত্ব ও সীমার কথাটা মাথায় আসে না। একবারও তারা ভাবেন না, দেশের আইন তাদেরকে আদতেই এমন ব্যবহার করার অধিকার দেয় কি না। করোনার এ সংকটকালে কখনো ডাক্তারদেরকে ভয় দেখিয়ে নোটিশ দেয়া, কখনো টেলিভিশন মনিটরিংয়ের নামে প্রজ্ঞাপন জারি করা, কখনো বয়স্ক নাগরিকদের কান ধরে উঠবস করানো, জনগণের ট্যাক্সের টাকায় পুকুর কেটে সেই পুকুর নিজের নামে করে নেওয়া, আবার এই বিষয়ে প্রশ্ন করার দায়ে সাংবাদিককে ক্রসফায়ার দিতে চাওয়ার সাথে সাথে তথ্যমন্ত্রণালয়ের DSA আইনে নামে প্রচ্ছন্ন ভয় দেখিয়ে রাখা কিছুই বাদ নেই এখানে।
আমলাতন্ত্রের যে দৌরাত্ম চলছে দেশে, যেভাবে তারা দেশের সব কাজের কাজি হয়ে ছড়ি ঘোরাচ্ছে সাধারণ মানুষের ওপরে, এমনকি রাজনীতিবিদ, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরও বাদ দিচ্ছে না, দ্রুতই তাদের লাগাম টানতে না পারলে এ দেশের কপালে দুর্ভোগ আছে। সরকার যতই জনবান্ধব হওয়ার চেষ্টা করুক, যত বাজেটই বরাদ্দ দিক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে, আমলাতন্ত্রের কালো ছায়া সরাতে না পারলে কোনো সুবিধাই জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাবে না। ইঁদুর যেমন ঘরের মেঝের মাটি কেটে বাইরে নিয়ে ফেলে, দুর্নীতিবাজ আমলারাও তাই। ঘাড়ের ওপর বসে থেকে ভেতরটা শুষে খেয়ে ঝাঁঝরা করে দেওয়ার আগ পর্যন্ত কিচ্ছু টের পাওয়া যায় না।
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে দেশ পরিচালনার জন্য সরকার ব্যবস্থার যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন আছে আমলাদেরও। কিন্তু কোনভাবেই প্রশাসনিক কাজের বাইরে অতিরিক্ত কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তাদের দেওয়া চলবে না। জনগণের সেবা করাই হবে তাদের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও জনগণের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেখার জন্য দায়িত্ব পালন করবে সরকার ও তার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা এ কাজে তাদের দাপ্তরিক সহায়তা প্রদান করবে কেবল। রাষ্ট্রের অধীনে শ্রমিক হিসেবে অর্পিত দায়িত্বগুলোই কেবল পালন করবে তারা। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে জনগণের প্রকৃত কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য আগ্রাসী আমলাতন্ত্রের রাশ টেনে ধরার বিকল্প নেই।