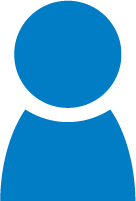১৭ জুলাই থেকে দেশে যা হয়েছে তা কোনো আন্দোলন না। এ ঘটনাকে এক কথায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতার সঙ্গে তুলনা করা যায়। আমি মনে করি, এটি উন্নয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে ধ্বংসস্তূপে ঢেকে দেওয়ার পরিকল্পিত সন্ত্রাস। কোনো শিক্ষার্থী তো নয়ই, ন্যূনতম বিবেকবান মানুষের পক্ষে এ ধরনের বীভৎসতা ঘটানো সম্ভব নয়। যারা এটা করেছে তাদের লক্ষ্য একটাই- বাংলাদেশকে ধ্বংস করা। প্রশ্ন হলো, কারা এটা করতে চায়? এটি কি শুধু স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি, জঙ্গি এবং বিএনপির নাশকতা? আমি অন্তত তা মনে করি না। বিএনপি-জামায়াত, ছাত্রদল-ছাত্রশিবির, জঙ্গি এবং সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো অবশ্যই এই জ্বালাও-পোড়াও, ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু হুট করে তারা এত ক্ষমতাবান কীভাবে হলো? কোথায় এত টাকা-পয়সা, অস্ত্রশস্ত্র পেল? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে নির্মোহভাবে। আর সে কারণেই এ আন্দোলনের শুরু থেকে এর গতি প্রবাহ এবং সময়কাল বিশ্লেষণ জরুরি।
কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালে। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে কোটাবিরোধী প্রচারণার উৎসকাল নব্বই দশক। ’৯০-এ এরশাদের পতনের পর দেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসে। বিএনপিকে ক্ষমতায় আসতে সহযোগিতা করে জামায়াত। এ সময় যুদ্ধাপরাধীদের শিরোমণি গোলাম আযম প্রকাশ্য তৎপরতা শুরু করে। জামায়াত মজলিসে শূরার মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধী এবং ’৭১-এর নরঘাতক গোলাম আযমকে আনুষ্ঠানিকভাবে দলের আমির ঘোষণা করে। ওই মজলিসে শূরায় আরেকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। সরকারি চাকরিতে ‘মুক্তিযোদ্ধা কোটা’সহ অযৌক্তিক সব কোটা বাতিল করে মেধাভিত্তিক নিয়োগের প্রস্তাব নেওয়া হয়। ১৯৯২ সালে জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির শিক্ষার্থীদের জন্য ২০ দফা দাবিনামা উপস্থাপন করে। এই ২০ দফার মধ্যে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার করে মেধাকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এ দাবিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রশিবিরের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত ৩২ বছর ‘কোটা সংস্কার’ নিয়ে কাজ করছে ছাত্রশিবির। ২০০৯ সালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে জামায়াত যখন লণ্ডভণ্ড, তখন শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাধীনতাবিরোধীরা আরও গভীরভাবে কাজ শুরু করে। বিশেষ করে, যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার ফাঁসির দাবিতে গড়ে ওঠা ‘গণজাগরণ মঞ্চ’ ছাত্রশিবির এবং জামায়াতকে নতুন করে পরিকল্পনা সাজানোর পথ দেখায়। ছাত্রশিবির তার কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়। আধুনিক জীবনাচার, তরুণদের আগ্রহগুলো রপ্ত করানো হয়। দাড়ি, টুপি ছেড়ে আধুনিক বেশভূষায় অভ্যস্ত হয় শিবির। দ্রুতই তারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে মিশে যেতে শুরু করে। মেধাবী, জনপ্রিয়, বন্ধুবৎসল তরুণদের মধ্যে কোটা নিয়ে অসাম্য তুলে ধরতে থাকে। এভাবেই ধীরে ধীরে কোটা সংস্কার শিক্ষার্থীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে। ২০১৮ সালে কোটা সংস্কার নিয়ে প্রথম ছাত্র বিস্ফোরণ হয়। এ সময় প্রধানমন্ত্রী দ্রুত পদক্ষেপ নেন। আন্দোলন থামাতে তাৎক্ষণিকভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরিতে কোটা বাতিল করা হয়। সরকারের ওই সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না। সুস্পষ্টভাবেই এ সিদ্ধান্ত সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এসময় আমলারা ‘মাথা ব্যথায় মাথা কেটে ফেলা’র সহজ সমাধান দিয়েছিল। আমলাতান্ত্রিক সমাধানের এটাই হলো সবচেয়ে বড় ব্যাধি। আমলারা একটি সমস্যা ধামাচাপা দিতে আরেকটি সমস্যা সৃষ্টি করেন। ২০১৮ সালে যদি কোটা নিয়ে আন্দোলনকারী এবং এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একটি স্থায়ী সমাধান করা হতো তাহলে হয়তো বর্তমান পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না। যাই হোক, ২০১৮ সালের ওই সরকারি পরিপত্রের পর কোটা আন্দোলন বন্ধ হয়। ছয় বছর দেশে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরিতে নিয়োগ হয়েছে কোনো রকম কোটা ছাড়াই। বছর তিনেক পর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের পক্ষ থেকে, মুক্তিযোদ্ধা কোটা পুনর্বহালের দাবিতে হাই কোর্টে একটি রিট পিটিশন করা হয়। এই রিট পিটিশন এত দূর গড়ালো কেন? ওই রিট পিটিশনের বিরুদ্ধে আইন মন্ত্রণালয় এবং অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস কি তখন এখনকার মতো অবস্থান নিয়েছিল? না নেয়নি। এমনকি, হাই কোর্টের রায়ের পরও আইন মন্ত্রণালয় এবং অ্যাটর্নি জেনারেল যদি দ্রুত আপিল বিভাগে গিয়ে হাই কোর্টের রায় স্থগিত চাইতেন, তাহলেও আন্দোলন এত দূর গড়াতো না। ধাপে ধাপে ছিল উপেক্ষা এবং উদাসীনতা। সবাই যেন পরিস্থিতিকে ভয়াবহ হতে সহায়তা করেছেন। অথবা পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধিই করতে পারেননি। ২০১৮ সালের আন্দোলনের তীব্রতা বুঝতেই পারেননি ক্ষমতাসীন সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। হাই কোর্টের রায়ের পরই কোটা আন্দোলন সংগঠিত হতে শুরু করে। বিক্ষিপ্তভাবে যখন আন্দোলন দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শুরু হয়, তখনই সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় বসার সুযোগ ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগের কিছু নেতার দম্ভ, দায়িত্বহীনতার কারণে সেটি সম্ভব হয়নি। টানা চতুর্থবারের মতো দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়া আওয়ামী লীগের কারও কারও মধ্যে কিছু জনবিচ্ছিন্নতার মারাত্মক ব্যাধি বাসা বেঁধেছে। সবকিছুকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, আত্মতুষ্টি, অহংকার দলের কিছু নেতাকে মোটামুটি ‘মানসিক প্রতিবন্ধীতে’ পরিণত করেছে। এসব নেতা মনে করেন, সবকিছু করবেন প্রধানমন্ত্রী। কিছু বাঁচাল নেতার কথাবার্তা জনবিরক্তি থেকে জনক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব নেতা মনে করেন তারা অমর, অবিনশ্বর। এরা আওয়ামী লীগ সংগঠনের যেমন বারোটা বাজিয়েছেন, তেমনি দেশকে ফেলেছেন সংকটে। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, কোটা আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠতে শুরু করে তার আগেই প্রধানমন্ত্রী শুরু করেন দুর্নীতিবিরোধী অভিযান। ব্যাংকিং খাতে দুরবস্থা, অর্থপাচার এবং কিছু ব্যক্তির সীমাহীন দুর্নীতি এবং ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণের কারণে অর্থনৈতিক সংকট গভীর হতে থাকে। অর্থনীতিকে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনতে প্রধানমন্ত্রীর দুর্নীতিবিরোধী অভিযান একটি সাহসী ও সময়োপযোগী উদ্যোগ। এ সময় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা বিভিন্ন ব্যক্তির লুটপাটের খবর বেরোতে থাকে গণমাধ্যমে। সাবেক পুলিশ প্রধান বেনজীরের ‘আলাদিনের চেরাগ’ কাহিনি গোটা জাতিকে স্তম্ভিত করে। সরকারের বিশ্বস্ত এবং ঘনিষ্ঠ হিসেবে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন বেনজীর। এসব পদে থেকে তিনি রীতিমতো লুণ্ঠন করেছেন। আদালতের নির্দেশে দুর্নীতি দমন কমিশন তার বিপুল সম্পদ জব্দ করে। কিন্তু সরকারের ভিতর থাকা বেনজীরের দুর্নীতির দোসরদের সহযোগিতায় বেনজীর দেশত্যাগ করেন। বেনজীরের পর তোলপাড় শুরু হয় এনবিআরের সদস্য মতিউরকে নিয়ে। ১৫ লাখ টাকায় ছাগল কেনার কাণ্ডে বেরিয়ে আসে মতিউরের রত্ন ভাণ্ডারের খবর। মতিউরের পরিবারের হাজার কোটি টাকার সাম্রাজ্য গোটা দেশে রীতিমতো ভূমিকম্প সৃষ্টি করে। এরপর থেকে একে একে বেরিয়ে আসতে থাকে নানা গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতির কেচ্ছাকাহিনি। দুর্নীতি দমন কমিশন একের পর এক সম্পত্তি জব্দ শুরু করে। দুর্নীতিবাজদের বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আসতে থাকে। কিন্তু বেনজীরের মতো মতিউরও ‘অদৃশ্য মানব’ হয়ে যান। দেশ ছাড়েন মতিউরের দ্বিতীয় স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী সবাইকে ম্যানেজ করে বহাল তবিয়তে আছেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর যুদ্ধে সরকারের মধ্যেই যেন দুটি পক্ষ। এক পক্ষ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুশাসন অনুযায়ী দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আরেক পক্ষ দুর্নীতিবাজদের বাঁচাতে তাদের পালাতে সহযোগিতা করে। দুর্নীতি নিয়ে সরকারের ভিতর চলছে দ্বৈতদ্বন্দ্ব। এর মধ্যেই চীন থেকে দেশে ফিরে দুর্নীতি নিয়ে ‘শূন্য সহিষ্ণুতা নীতি’র ঘোষণা দেন শেখ হাসিনা। গত ১৪ জুলাই চীন সফরের ওপর আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দেন, ‘কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।’ এ সময় শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের জানান চাঞ্চল্যকর তথ্য। বলেন, ‘আমার পিয়নও ৪০০ কোটি টাকার মালিক।’ পরে জানা যায়, ওই পিয়ন হলেন জাহাঙ্গীর। নোয়াখালীর চাটখিল থেকে হতদরিদ্র অবস্থায় ঢাকায় আসেন। শেখ হাসিনার ফাই ফরমায়েশ খাটতেন। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে জাহাঙ্গীর হয়ে যান প্রচণ্ড ক্ষমতাবান। আওয়ামী লীগের নেতা, মন্ত্রী, এমপি এমনকি আমলারাও জাহাঙ্গীরকে সমীহ করতেন। প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি জানার পর গত বছরই তাকে বাদ দেন। নিষিদ্ধ করেন গণভবনে। কিন্তু তারপরও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি কেউ। প্রধানমন্ত্রী এমন এক সময়ে তাঁর পিয়নের ৪০০ কোটি টাকার তথ্য জাতিকে জানান, যখন পিএসসির এক গাড়িচালকের শত কোটি টাকার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা নিয়ে দেশজুড়ে তুলকালাম চলছে। বছরের পর বছর ওই ড্রাইভার প্রশ্নপত্র ফাঁস করে সম্পদের পাহাড় গড়েছেন। আবেদ আলী এবং জাহাঙ্গীর যেন দুর্নীতির বৃত্ত পূরণ করেন। প্রমাণ হয়ে যায় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে ড্রাইভার-পিয়ন পর্যন্ত দুর্নীতির ক্যান্সারে আক্রান্ত। পরিস্থিতি এমন যে, সরকারের মাথাটি কেবল ঠিক আছে। যাকে দুর্নীতি স্পর্শ করেনি। আর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে দুর্নীতির ক্যান্সার। ওই সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দেন যে, ‘এসব দুর্নীতিবাজকে গ্রেপ্তার করলে সরকারের ইমেজ ক্ষুণ্ন হয় না। আমি এ ধরনের দুর্নীতির তথ্য জাতিকে জানাতে ভয় পাই না।’ আমার বিবেচনায় ওই সংবাদ সম্মেলনে এটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য। এর মাধ্যমে দুর্নীতিবাজদের প্রধানমন্ত্রী সুস্পষ্ট একটি বার্তা দিয়েছিলেন। এর ফলে চিহ্নিত দুর্নীতিবাজরা এবং সরকারের ভিতর ঘাপটি মেরে থাকা সহযোগীরা বুঝেছে পরিস্থিতি ভালো নয়। বাঁচার উপায় হিসেবে কোটা আন্দোলন এবং বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসীদের ওপর তারা ভর করে।
প্রধানমন্ত্রীকে ওই (১৪ জুলাই) সংবাদ সম্মেলনে কোটা নিয়েও প্রশ্ন করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যজনক হলো, প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নের চেয়ে চাটুকারিতাই বেশি হয়। অনেকে সাংবাদিকতা ভুলে আওয়ামী লীগের কর্মীর মতো মন্তব্য করেন, পরামর্শ দেন। ‘কোটা’ নিয়ে যে দুটি প্রশ্ন করা হয়েছিল, তা ছিল বর্ণনাধর্মী, মন্তব্যসূচক। রাজাকারের নাতি-পুতি আর মুক্তিযোদ্ধার নাতি-পুতি সমান যোগ্যতাসম্পন্ন হলে কাকে চাকরি দেবেন?-এটা কোনো প্রশ্ন হতে পারে না। সংবিধান অনুযায়ী চাকরি দেওয়ার এখতিয়ার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের। এরকম মতলবী প্রশ্নেরও বিচক্ষণ উত্তর প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে, প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতার কন্যা। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতার সন্তান। কাজেই তিনি তো বলবেনই মুক্তিযোদ্ধার নাতি-পুতিই এক্ষেত্রে চাকরি পাবে। সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা কখনো আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ‘রাজাকার’ বলেননি। কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য বিকৃত হয়ে গেল। তিলকে তাল বানানো হলো। রাতের মধ্যে অদৃশ্য ইশারায় মিছিল বের করল আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। ‘তুমি কে, আমি কে, রাজাকার, রাজাকার’ স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠল প্রায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলো। এই আন্দোলন যেন ‘রিমোট কন্ট্রোল’ চালিত আন্দোলন। এক ইশারায় নাচন শুরু হলো সর্বত্র। এ পরিস্থিতির মধ্যেই ক্যাম্পাসগুলোতে ঢুকে পড়লো ছাত্রশিবির এবং ছাত্রদলের সশস্ত্র ক্যাডাররা। তাদের লক্ষ্য কোটা সংস্কার নয়, আবাসিক হল দখল। ছাত্রলীগের ‘সোনার ছেলেরা’ বুঝতেই পারেনি কী হচ্ছে। বেধড়ক মার খেল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সম্পর্কহীন সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা। এরপর সারা দেশে শুরু হলো তাণ্ডব।
গত রবিবার (২১ জুলাই) বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এক ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন। জাতীয় সংকট নিরসনে আপিল বিভাগের এই অসাধারণ এবং সাহসী ভূমিকা বাংলাদেশের আইনের শাসনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সংবিধানের ১০৪ অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করে আপিল বিভাগ দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংকটের সমাধান করেছে। কোটা সংস্কার নিয়ে যারা আন্দোলন করেছেন তাদের এ রায়ের বিরোধিতা করার কোনো কারণ দেখি না। কিন্তু আমার মনে হয় না, এত দ্রুত এই আন্দোলন থেমে যাবে। সংকট থেকে সরকার হয়তো বেরিয়ে আসবে, তবে সময় লাগবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, সরকারের দুর্বলতাগুলো উন্মোচিত হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে অনেকে সুযোগ নেবে। নানা ইস্যুতে সরকারকে চাপে ফেলার চেষ্টা করবে। ভাঙা বেড়ার সন্ধান পেলে যেমন ‘শিয়াল’ বারবার বাড়িতে হানা দেয়, তেমনি দুর্বৃত্তরা সুযোগ খুঁজবে।
প্রশ্ন হলো, সরকার তার দুর্বলতা কাটিয়ে উঠবে কীভাবে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের আগে খুঁজে বের করতে হবে, এই বিপুল সন্ত্রাসী ও সহিংসতার মূল কারিগর কারা? নেপথ্যের ‘গডফাদার’ কে? এই অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির নেপথ্যের নীলনকশা কার? এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল কোটা আন্দোলন থেকেই। কিন্তু মেট্রোরেলে হামলা, বিটিভি ভবনে হামলা, সেতু ভবন, দুর্যোগ ভবনে অগ্নিসংযোগের ঘটনার চিত্রনাট্য সাধারণ শিক্ষার্থীদের রচিত নয়। এ ধরনের তৎপরতা চালানোর জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ এবং পেশাদারিত্ব লাগে। কাজেই ১৮ থেকে ২০ জুলাই সারা দেশে যে তাণ্ডব হয়েছে তা শিক্ষার্থীদের আন্দোলন নয়। এটা পেশাদার সন্ত্রাসীদের পরিকল্পিত অপকর্ম।
আওয়ামী লীগ এ ঘটনার জন্য বিএনপি-জামায়াতকে দায়ী করেছে। বিএনপির একাধিক শীর্ষনেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন। এসব ভাঙচুরের সঙ্গে গত ২৮ অক্টোবর প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা, পুলিশ হাসপাতালে অগ্নিসংযোগের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। বিএনপি এবং জামায়াতের কয়েক লাখ কর্মী কোটা আন্দোলনের ফায়দা লুটতে ঢাকায় ঢুকে ছিল। তারা আন্দোলন বেগবান করেছে। সহিংসতার মাধ্যমে সরকার উৎখাতের চেষ্টা করেছে। গুজব ছড়িয়েছে। পুলিশের ওপর ছাত্রদল এবং ছাত্রশিবিরের ক্যাডাররা চড়াও হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলা হয়েছে পরিকল্পিতভাবে। এ পরিকল্পনা ছাত্রদল, ছাত্রশিবিরের পক্ষে প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। নাশকতা পরিচালিত হয়েছে প্রশিক্ষিত কমাণ্ডের মাধ্যমে। এমন এক বা একাধিক ব্যক্তি এ সন্ত্রাসী পরিকল্পনায় জড়িত যিনি পুলিশের দুর্বলতা জানেন, পুলিশের কৌশল সম্পর্কে অবহিত। ঢাকা শহরের স্পর্শকাতর পয়েন্টগুলো তার নখদর্পণে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সম্পর্কে যিনি প্রচুর জ্ঞান রাখেন। সন্ত্রাসী তাণ্ডবের ভিডিও ফুটেজগুলো খুঁটিয়ে দেখলে প্রমাণ মিলবে অনেক কিছুরই। যেমন বিটিভিতে যখন আক্রমণ হয়েছে তখন দেখা যাচ্ছে, রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে লড়াই করছে ছাত্রদল, ছাত্রশিবির এবং ভাড়াটে বাহিনী। এদের মধ্যে থেকে প্রশিক্ষিত কিছু তরুণ পুলিশের ফাঁক গলে বিটিভিতে ঢুকে পড়ে এবং হামলা চালায়। একই ঘটনা লক্ষ্য করেছি সেতু ভবন এবং দুর্যোগ ভবনেও। এরা কারা? এখানেই আমি এই নারকীয় তাণ্ডবের সঙ্গে দুর্নীতিবাজদের সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পাই। এ সময়ের সবচেয়ে আলোচিত দুর্নীতিবাজ সাবেক পুলিশ প্রধান বেনজীর আহমেদ। তিনি বিদেশে অবস্থান করছেন। কিন্তু দেশের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। তার সাঙ্গপাঙ্গ আছে সর্বত্র। বেনজীর এক সময় ঢাকার পুলিশ কমিশনার ছিলেন। র্যাবের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন, পুলিশ প্রধান ছিলেন। পুলিশ বাহিনীর ভিতর তার নিজস্ব লোকজন এখনো আছে। তার চেয়েও বড় কথা তিনি পুলিশের দুর্বলতা জানেন, জানেন কীভাবে তাদের চাপে ফেলা যায়। সন্ত্রাসীদের সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকাটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে জঙ্গি দমন করতে গিয়ে তিনি অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ করেছেন। অনেককে বাঁচিয়েছেন। কাউকে কাউকে সোর্স হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এই নেটওয়ার্ক তার অজানা নয়। সরকারকে উৎখাত করতে পারলে তার ‘দুর্নীতি’ নিয়ে চর্চা হবে না। তিনি নিরাপদ হয়ে যাবেন। এ ভাবনা থেকে এ আন্দোলনে তার সম্পৃক্ততা কি সরকার উড়িয়ে দিতে পারবে? বেনজীর আহমেদের যেসব ঘটনা ও অপকর্মের কাহিনি সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত হয়েছে তাতে নিঃসন্দেহে তাকে ‘গডফাদার’ বলা যায়। এ নারকীয়তার গডফাদার বেনজীরসহ দুর্নীতিবাজরা নয় তা কে হলফ করে বলতে পারবে?
এ তাণ্ডবে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ হয়েছে। বিএনপি-জামায়াত এত টাকা খরচ করবে তা আমি বিশ্বাস করি না। এরকম অর্থ খরচ করতে পারলে ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের আগেই তারা করত। এ রাষ্ট্রবিরোধী সন্ত্রাসে এ সময় আলোচিত দুর্নীতিবাজ বেনজীর, মতি, জাহাঙ্গীরের বিনিয়োগ আছে কি না তা খতিয়ে দেখা দরকার।
নরসিংদী কারাগারে হামলা হয়েছে। নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলা চেয়ারম্যান কে? প্রত্যেকটি ঘটনার যোগসূত্র খুঁজতে হবে, সমীকরণ মেলাতে হবে। শুধু ‘বিএনপি-জামায়াতের কাজ’ বলে সকাল-সন্ধ্যা কাকের মতো চিৎকার করলে আসল শত্রুকে চিহ্নিত করা যাবে না। ভবিষ্যতে আবার সরকার উৎখাতের চেষ্টা হবে আরও ভয়ংকরভাবে। তাই এখনই সাবধান। আসল শত্রু চিহ্নিত করতে হবে সবার আগে।
সৈয়দ বোরহান কবীর, নির্বাহী পরিচালক, পরিপ্রেক্ষিত
ই-মেইল: poriprekkhit@yahoo.com