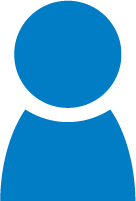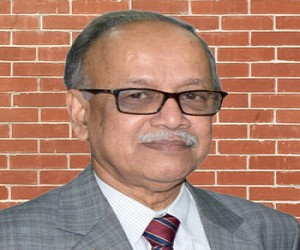‘‘এরকম শান্তিপূর্ণ একটি আন্দোলন কীভাবে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর, সহিংসতা এবং লুটপাটের আন্দোলনে পরিণত হল? কারণ যথারীতি বিএনপি ও জামায়াত জোট তাদের নিজস্ব একটি সহিংস আন্দোলন চালানোর জন্য মূলত একটি অরাজনৈতিক ও অহিংস আন্দোলনকে ব্যবহার করেছে। স্বার্থান্বেষী মহলের সম্পৃক্ততা উপলব্ধি করে, প্রতিবাদকারীরা নিজেরাই সহিংসতায় লিপ্ত থাকার কথা অস্বীকার করে বেশ কয়েকটি বিবৃতি দিয়েছে এবং নিশ্চিত করেছে যে, এসব কর্মকাণ্ডের পেছনে একটি তৃতীয় পক্ষ জড়িত রয়েছে, যার সঙ্গে প্রতিবাদকারীদের কোনও সম্পর্ক নেই।...
দেশের শিক্ষার্থীরা মোটেও সন্ত্রাসী নয়। বিএনপি-জামায়াত চক্র তাদের বাংলাদেশ ভাঙার দলীয় এজেন্ডার আড়ালে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করেছে।’’
কোটা দাবি নিয়ে ঘটে যাওয়া নাশকতা ও সহিংসতা সম্পর্কে ২৫ জুলাই(২০২৪) প্রকাশিত সজীব ওয়াজেদ জয়ের মন্তব্যের সূত্র ধরে তাঁর জন্মদিন নিয়ে কিছু প্রসঙ্গের অবতারণা করা হলো।
২৭ জুলাই আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার সজীব ওয়াজেদ জয়ের ৫৪ তম জন্মদিন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় দেশের যে কোনো ঘটনায় সামনে এসেছেন, দিক-নির্দেশনামূলক কথা বলেছেন- দেশকে নিয়ে তাঁর অনুভূতি প্রকাশের ভাষাও অনন্য।তিনি বাংলাদেশের সমান বয়সী। ১৯৭১ সালের এই দিনে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন।রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান এবং সরকারের একজন উপদেষ্টা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন।এদেশের অফিস-আদালত থেকে শুরু করে টেন্ডার কিংবা ব্যাংকের লেনদেনের যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে সেই ডিজিটালাইজেশনের নেপথ্যে তাঁর অবদান রয়েছে।এজন্য কোভিড-১৯ এর প্রভাবে মহামারি ও লকডাউনে যখন বিশ্বজুড়ে অনলাইন যোগাযোগ একমাত্র মাধ্যম হয়ে উঠেছিল তখন এদেশের কৃতি সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয়কে বেশি করে মনে পড়েছে।ব্যাধির সংক্রমণ রোধে গৃহবন্দি থেকে অনলাইনে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা কিংবা মোবাইল ব্যাংকিং-এ বেতন ও সহায়তা পাওয়ার দৃষ্টান্ত আমরা তখন ভালভাবে আত্মস্থ করে নিয়েছিলাম।কৃষিভিত্তিক সমাজ ক্রমান্বয়ে প্রযুক্তি নির্ভর সমাজে পরিণত হয়েছে।কেবল সজীব ওয়াজেদ জয়ের দিক-নির্দেশনায় কাজ করে প্রযুক্তির প্রসার ঘটেছে এদেশে। ফলে আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে।এজন্যই তাঁকে আমরা অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশেরও অন্যতম কাণ্ডারী তিনি।
জয় ভারত থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারে বিএসসি ডিগ্রি এবং যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোক-প্রশাসনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০০৭ সালে তিনি ২৫০ জন তরুণ বিশ্ব নেতার মধ্যে একজন হিসেবে সম্মানিত হন। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পাওয়া তিনি অনেক আগে থেকেই রাজনীতিসচেতন। ২০০৮ সালের জুন মাসে শেখ হাসিনাকে সামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কারাগার থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়ে থাকে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ হাসিনা আর তার সফল রূপকার হলেন সজীব ওয়াজেদ জয়।
জয়ের ভেতর রয়েছে বঙ্গবন্ধুর মতো প্রচণ্ডতা। রয়েছে পরিশ্রমী ও তারুণ্যের প্রাণময়তা। এজন্য আমেরিকা থেকে তাঁর ফিরে আসা, রাজনীতিতে যোগ দেয়া আমাদের জন্য শুভ সূচনা ছিল। দেশের মধ্যে যারা একসময় দুর্নীতি ও নাশকতার পৃষ্ঠপোষকতা করেছে তাদের মসনদ কেঁপে উঠেছিল তাঁর দেশকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে। তিনি মূলত বঙ্গবন্ধুর মতোই মানুষকে আশাবাদী করে জাগিয়ে তোলার জন্য কথা বলেন ও কাজ করেন। একসময় তাঁর মতো বয়সে বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষকে জাগিয়েছিলেন; জয়ও তেমনি সরকারের সঙ্গে থেকে দেশের সামগ্রিক সমস্যার সমাধান করে আওয়ামী লীগকেও গড়ে তুলতে চান। ভাষণ দেবার সময় তাঁর ভেতর থেকে বঙ্গবন্ধুর মতোই সম্মোহনী চেতনা স্ফুরিত হয়। তিনি ২০০৯ সাল থেকে নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত অভিজ্ঞতা দিয়ে এদেশের আইসিটি সেক্টরকে উন্নতির শিখরে নিয়ে গেছেন। তরুণদের উজ্জীবিত করছেন মৌলিক গবেষণায়। বিএনপি-জামায়াতের গাত্রদাহের কারণ এজন্য যে জয় উচ্চশিক্ষিত এবং যে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন তার পুরোভাগে তিনি আছেন। শেখ হাসিনা যেমন নির্লোভ, মানুষকে ভালোবাসেন নিজের অন্তর থেকে, জয়ও তেমনিভাবে এগিয়ে চলেছেন। বিরুদ্ধ মানুষের মন জয় করতে হয়েছে তাকে। এজন্য তার সাথে ছাত্রলীগ-যুবলীগ নেতারা কাজ করেছেন। সাধারণ মানুষকে শেখ হাসিনা সরকারের কর্মসূচি, সাফল্য বর্ণনা করতে হয়েছে ডিজিটালকরণের জন্য। অনেকে ভাবতে পারেন তিনি আমেরিকান সিটিজেন। এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, শেখ হাসিনাও যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাবেন। যেহেতু জয়ের মা নিজে এই মাটি, মানুষের নিকটজন সেহেতু তিনিও তারই ধারাবাহিকতায় মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবেন।
সজীব ওয়াজেদ জয় ভিশনারি লিডার। তিনি ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে ২০০৯ সালে দেখতে পেয়েছিলেন বলেই আজ দেশে ১০ কোটির বেশি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন। শিক্ষাখাতে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ বেড়েছে। বিশেষত করোনা মহামারিতে সকল প্রতিষ্ঠান এখন প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল। পাঠসূচিতে যেমন শিশুরা আইসিটি অধ্যয়ন করছে তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি হয়েছে বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার। এমনকি দেশের বিপিও খাতে বর্তমানে ১০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি রপ্তানি করা হচ্ছে; ৫০ হাজারের বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সাড়ে ছয় লাখ মানুষ এই মুহূর্তে আইসিটি সেক্টরে চাকরি করছেন। ২০২৫ সালের মধ্যে ১০ লাখ মানুষের কাজ করার সুযোগ হবে এই খাতে। আর এসবই সম্ভব হয়েছে সজীব ওয়াজেদ জয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী। গত সাড়ে ১৫ বছরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যেমন এগিয়ে গেছে তেমনি তার পুত্রের দূরদর্শী সিদ্ধান্তে এদেশ প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠেছে।
অতীতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জয় বলেছেন, ভবিষ্যতের নেতা এদেশের তরুণরাই। উল্লেখ্য, ঢাকার সাভারে শেখ হাসিনা যুব কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উন্নয়নে ভূমিকা রাখা তারুণ্যনির্ভর ৩০টি সংগঠনের হাতে ‘জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড’ তুলে দেওয়ার সময় তাদের এই অভিধা দেন তিনি। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসে নিজেদের উদ্যোগে দেশের উন্নয়নে এগিয়ে আসা তরুণ-তরুণীদের বাংলাদেশের আগামী দিনের নেতা অভিহিত করার কারণ তার জনসম্পৃক্ততা।নিজে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন শেখ হাসিনার সঙ্গে। আর সেই কাজে তরুণ প্রজন্ম তাঁর অনিবার্য লক্ষ্য। এর আগে তিনি দেশের ভেতর ও বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের অগ্রগতির কথা, তরুণ জনগোষ্ঠীর ইতিবাচক অর্জনের গল্প শুনিয়েছেন বিশ্বের মানুষকে। তাঁর মতে, ‘আমাদের দেশের তরুণরা এখন দেশের জন্য কাজ করতে যেভাবে এগিয়ে এসেছে, আগে সেটা দেখা যেত না। দেশের সমস্যা আমরা সমাধান করতে পারব কি না, দেশকে এগিয়ে নিতে পারব কি না, সেই বিশ্বাস আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম। কারণ স্বাধীনতার চেতনা আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম।’ কিন্তু ‘এখন আমাদেরকে শাইনিং স্টার বলা হচ্ছে। ‘নেক্সট ইলেভেন’-অর্থনীতির দেশের একটি আমরা।’ সজীব ওয়াজেদ জয় সেদিন যে কথা বলেছেন, তা একজন তরুণ নেতার আদর্শ ও বিশ্বাসের কথা। তিনি নিজে নতুন প্রজন্মের নেতা, তাই যুবসমাজের কাছে আলোকবর্তিকা হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছেন।
রাজধানীতে অনুষ্ঠিত অপর এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সজীব ওয়াজেদ জয় বলেছিলেন, ‘সৎ সাহস ও নিজের আত্মবিশ্বাস থাকলে যে কোনো কঠিন কাজ করা যায়। আমরা কারও চেয়ে কম নই। বিদেশের সঙ্গে আমরা সমানে সমান। সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ে বিদেশী সাটিফিকেট প্রয়োজন নেই।’ অর্থাৎ এই তরুণ নেতৃত্বের কাছে নিজেদের টাকায় পদ্মাসেতু তৈরির ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছে সততা এবং আদর্শের কোনো বিকল্প নেই। সৎ না থাকলে মানুষের ভালোবাসা পাওয়া যায় না। আর মানুষের ভালোবাসা ছাড়া ক্ষমতায় আসা যায় না। তিনি বিশ্বাস করেন, নিজের দেশকে টেনে উঠাতে দেশপ্রেম দেখাতে হবে। বিশ্বের সামনে বাংলাদেশকে টেনে তোলার মধ্যেই দেশপ্রেম নিহিত রয়েছে।
প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে যে গণতান্ত্রিক ধারা বহমান তা বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে সজীব ওয়াজেদ জয় এই তৃতীয় প্রজন্মের নতুন নেতৃত্বের প্রতি আমাদের সকল আকর্ষণ এখন কেন্দ্রীভূত। বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার পর বাংলাদেশে নেতৃত্বের বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। উপমহাদেশের রাজনীতিতে পারিবারিক ঐতিহ্য একটি ব্যাপক বিস্তারি প্রসঙ্গ। ভারতের দিকে তাকালে বর্তমান রাজনীতির পারিবারিক ধারা সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। জওহরলাল নেহেরু গান্ধীর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী তাঁর পিতার যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর সময় মোরালি দেশাইয়ের মতো অনেক যোগ্য নেতা থাকলেও ইন্দিরা গান্ধীই হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। জুলফিকার আলী ভুট্টো, তাঁর কন্যা বেনজীর ভুট্টো, বেনজীরের স্বামী ও ছেলের রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা যেমন সত্য তেমনি শ্রীলঙ্কার বন্দরনায়েক পরিবারের রাজনৈতিক পরিচয় লক্ষণীয়। ঠিক একইভাবে আওয়ামী লীগের ত্যাগী নেতারা ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনাকেই রাজনৈতিক মঞ্চে নিয়ে এসেছিলেন। পঁচাত্তর পরবর্তী তোফায়েল আহমেদ, প্রয়াত আবদুল জলিল, আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ বড় বড় নেতারা দেশ পরিচালনায় শেখ হাসিনাকেই জনগণের সামনে দাঁড় করান।
খালেদা জিয়া যেভাবে তারেক জিয়াকে রাজনীতিতে এনে দলের পদে সমাসীন করেছিলেন জয়ের জীবনে তেমনটি ঘটেনি। বরং জয় রাজনীতিতে নামতে পারেন ধরে নিয়ে ২০০৪ সালে ‘হাওয়া ভবনে’র মালিক তারেক জিয়াকে বিএনপি লুফে নিয়েছিল।
জয় বাংলাদেশের মৃত্তিকার সন্তান। তাঁর রাজনীতিতে আসাটা আকস্মিক হলেও দলকে সংগঠিত করা, দলের কোন্দল মেটানো, দলকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ রাখা প্রধান কাজ হিসেবে গণ্য হয়েছে প্রতিটি নির্বাচনের আগে। মহাজোট সরকারের সময় পাঁচ সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে পরাজয়ের পর আওয়ামী লীগের সামনে নতুন নেতৃত্বের দরকার ছিল। তাই তাঁর মতো কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে সামনে আনা আমাদের জন্য মঙ্গলজনক বলে গণ্য হয়েছিল। ২০১০ সালে তিনি আওয়ামী লীগের নিয়মিত সদস্য পদ গ্রহণ করেন।
ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সজীব ওয়াজেদ জয় সবসময়ই বলেছেন, উন্নয়নের অসমাপ্ত বিপ্লব শেষ করতে হলে আওয়ামী লীগকে সুযোগ দিতে হবে। তাঁর মতে, নতুন ও আধুনিক একটি বাংলাদেশের জন্য উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে। বাংলাদেশের জন্য এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। মহামারি মোকাবেলায় প্রযুক্তি আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল করে রেখেছে। এজন্য বিরোধী দলের অপপ্রচার মোকাবেলা ও সরকারের সফলতা জনগণের সামনে তুলে ধরতে ভিন্ন রকম কৌশল নিতে হবে। কারণ জয়ের বিরুদ্ধেও অপপ্রচার চালানো হয়েছে।
প্রকৃতপক্ষে সজীব ওয়াজেদ জয় বাংলাদেশের উন্নয়নে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রাণবন্ত উপস্থিতি আমাদের তরুণদের সামনে এগিয়ে যাবার প্রত্যাশায় উজ্জীবিত করেছে। একাধিক বেসরকারি টেলিভিশন-এ প্রচারিত অনুষ্ঠানে দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি নানা প্রসঙ্গে গঠনমূলক রাজনৈতিক কথা বলেছেন। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ‘লেটস টক’ শিরোনামে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সজীব ওয়াজেদ জয় বলেছেন, ক্ষমতাসীন সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অনেকটা এগিয়েছে। তিনি কেবল প্রযুক্তি নিয়ে ভাবেন না, তিনি মানুষকে মূল্য দেন। মানুষের দুঃখে সমব্যথী হন। আসলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং পিতা-মাতা বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ ও শেখ হাসিনার মতো আন্তরিক হৃদ্যতায় সাধারণ মানুষকে কাছে টানার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে তাঁর। তিনি দেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অনেক ভাবেই- যুবলীগ, ছাত্রলীগ কিংবা বিশেষ দিবসের অনুষ্ঠানে প্রাণবন্ত বক্তৃতা দিয়ে। দেশে দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দূর করার ক্ষেত্রে শেখ হাসিনা যেমন সক্রিয় উদ্যোগ নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তেমনি জয়ের পরামর্শে প্রযুক্তি পণ্য উৎপাদনে ৯৪টি যন্ত্রাংশের ওপর থেকে উচ্চ আমদানি শুল্ক উঠিয়ে ১ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। জয় জানেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবে সকল দুর্যোগ মোকাবেলা করে।
জয়ের মতো নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব আমাদের রাজনীতিতে যেমন ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা ঘটিয়েছে তেমনি উন্নয়নে সার্বিক অগ্রগতি সম্পন্ন করেছে। রাজনীতিতে নতুন প্রজন্মের পদচারণা আমাদের এগিয়ে চলার পথে বাড়তি প্রাপ্তি। নির্বাচন কমিশনের তথ্য মতে প্রতিবছর ভোটার তালিকায় তরুণ ভোটার আসে প্রায় ২৩ লাখ। ৯ কোটি ২১ লাখ ভোটারের মধ্যে ৪ কোটি ভোটারের বয়স ৪০ বছরের নিচে। মোট ভোটারের প্রায় ৪০ শতাংশ নতুন প্রজন্মের। তাদের জন্য নতুন প্রজন্মের নেতা অনিবার্য। সজীব ওয়াজেদ জয় এসব নতুন ভোটারদের প্রত্যাশার ভাষাকে ঠিকই বুঝতে পারেন। ভবিষ্যতে সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে জয়ী করার কৌশলও তিনি জানেন। কারণ আওয়ামী লীগ এদেশের যে উন্নয়ন করেছে বিগত জামায়াত-বিএনপি চারদলীয় জোট সরকার তা করেনি। অথচ বিএনপির মিথ্যা প্রচার প্রচারণা এখনও মোকাবেলা করতে হচ্ছে।
রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান হিসেবে জয় রাজনীতিতে সক্রিয় অন্তরালে থেকেই। নিজের প্রচারে বিশ্বাসী নন তিনি। তিনি রাজনৈতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যোগ দিয়েছেন কিন্তু প্রকাশ্যে বিচরণ তার কম। বঙ্গবন্ধুর নাতি এবং শেখ হাসিনা ও ড. ওয়াজেদ মিয়ার পুত্র হিসেবে পারিবারিক সূত্র গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তিনি যে মানুষের জন্য আত্মত্যাগ করতে এসেছেন তা বোঝার ক্ষমতা থাকতে হবে এদেশের মানুষের। প্রকৃত দেশপ্রেমিকের পক্ষে দেশ ও জাতির কল্যাণ করাই স্বাভাবিক।
আওয়ামী লীগের যে গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য রয়েছে তা অন্য কোনো দলের নেই। সজীব ওয়াজেদ জয় সেই গৌরবকে কাজে লাগিয়ে ২০০৯ সালে থেকে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন। মধ্যবিত্তের সন্তান বঙ্গবন্ধু মানুষের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। পাকিস্তানি শাসকদের ফাঁসির ভয়কে উপেক্ষা করেছেন। জেল খেটেছেন মাসের পর মাস। সেই ত্যাগী নেতার নাতি হিসেবে জয়কে মনে রেখেছেন- এই সব মূঢ়, মূক মানুষের মুখে দিতে হবে ভাষা। তাদের কাছে পৌঁছাতে হবে বঙ্গবন্ধুর পরিচয় নিয়েই। জাতির পিতা নিজের সন্তানকে (শেখ মনি, শেখ কামাল) রাজনীতিতে এনেছিলেন। আর তা ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাকে টিকিয়ে রাখার জন্য। পারিবারিক পর্যায়ে তিনি যা করেছিলেন তা ছিল দেশের স্বার্থে, মানুষের মঙ্গল চিন্তা করে। অনেকেই তাঁর বাকশাল প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধাচারণ করেন কিন্তু বঙ্গবন্ধুর দেশের জন্য মমত্ববোধকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না।
আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় দেশের কাজে এগিয়ে এসেছেন মানুষের আকর্ষণে। মাতার সান্নিধ্য তাঁকে রাজনীতির শিক্ষায় শিক্ষিত করেছে। তাঁর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে আওয়ামী সমর্থক সকলেই খুশী হবেন। কারণ তিনি মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে পারেন। আওয়ামী লীগকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে নেতৃত্ব ও উন্নয়নকে একইসঙ্গে আলিঙ্গন করতে হবে। জয় হঠাৎ আবির্ভূত নেতা নন। তিনি রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান। তাঁর আছে দৃঢ় চেতা অভিভাবক। যিনি সকল বিষয়ে সুপরামর্শ দিতে পারঙ্গম। কখনও পথ চলতে ছিটকে পড়লে শেখ হাসিনা পরামর্শ দিয়ে ঠিক পথে আনতে পারবেন তাঁকে। কারণ জয় একান্তই মাতৃ অনুগত। সকলেই জানেন, জয় আওয়ামী লীগের একজন সাধারণ সদস্য। এর বাইরে তিনি প্রধানমন্ত্রীর তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা। এই অর্থে তিনি দলের নীতি-নির্ধারক না হলেও বিভিন্নভাবে দল ও দলের নেতৃত্বকে অনেকরকম সহযোগিতা দিচ্ছেন। এখন এগিয়ে যাচ্ছেন বিচক্ষণতার সঙ্গে। স্বাধীনতার চেতনায় মথিত সজীব ওয়াজেদ জয়ের জীবন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জনের পরও বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হওয়ার জন্য জাতির পিতাকে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীত দিকে হাঁটা দায়ী। তাঁর বক্তব্য হলো- ‘আমরা লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। ৪ বছরেই নিজেদের পায়ে দাঁড়াচ্ছিলাম। সেই সময়ে আসে ৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট। এরপর স্বাধীনতার বিরুদ্ধ শক্তি ক্ষমতায় আসে।’ সজীব ওয়াজেদ জয় তরুণদের মূল্যবান কথা বলেছেন, ‘স্বাধীনতার চেতনা কোনোদিন ভুলবেন না। ভুলতে দেবেন না। আর কাউকে শহীদদের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে দেবেন না। এমন মিথ্যা প্রচারের সুযোগ দেবেন না, যাতে জাতি শহীদদের ভুলে যায়।’ তাঁর মতে, ‘যারা স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না, তারা বাংলাদেশের উপর কী বিশ্বাস রাখবে?’
শেখ হাসিনা সরকার পরিচালনায় সজীব ওয়াজেদ জয় যেমন তৎপর তেমনি ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ার ক্ষেত্রে নিজের নতুন নতুন ভাবনা-চিন্তা নিয়ে জনসমক্ষে হাজির হচ্ছেন। আওয়ামী লীগের নতুন কাণ্ডারী সজীব ওয়াজেদ জয়কে জন্মদিনে অভিবাদন। মূলত বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখতে হবে- একথা সজীব ওয়াজেদ জয় বারবার বলে এসেছেন। এজন্য দরকার যুবসমাজের পরিশ্রম। তরুণ নেতৃত্বের ওপর আস্থা রাখতে হবে আমাদের। শেখ হাসিনা সরকার এক নাগাড়ে ক্ষমতায় থাকায় উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ উন্নীত। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর দেশের অর্থনীতি অভূতপূর্বভাবে এগিয়েছে। বিশ্বে আমাদের অর্থনীতি এখন ভাল অবস্থানে। কারণ তরুণরাই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে একের পর এক ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করছে আওয়ামী লীগ সরকার। বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে (কোটা দাবিকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত) সর্ব প্রকার ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার দূর করার জন্য সজীব ওয়াজেদ জয়ের নেতৃত্ব সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। কারণ দেশপ্রেমিক জয়ের রয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা।তিনি তরুণ প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণার অনন্ত উৎস।
লেখক : ড. মিল্টন বিশ্বাস, বঙ্গবন্ধু গবেষক, বিশিষ্ট লেখক, কবি, কলামিস্ট, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রগতিশীল কলামিস্ট ফোরাম, নির্বাহী কমিটির সদস্য, সম্প্রীতি বাংলাদেশ এবং অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, email-drmiltonbiswas1971@gmail.com)