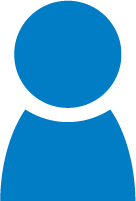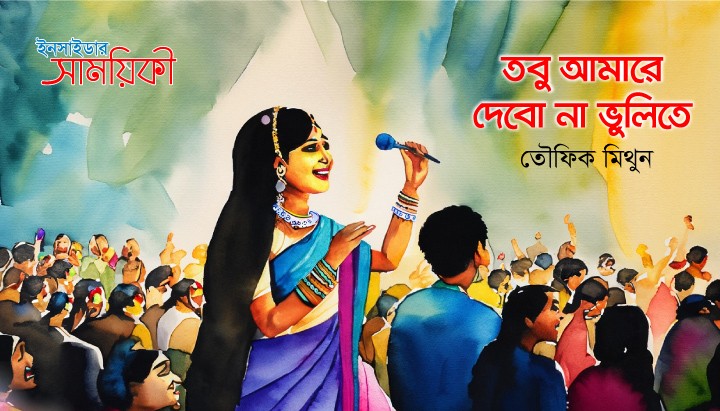নিতুর সাথে প্রথম দেখা কলেজের নবীন বরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। নজরুল গীতি গাইছিল সে।
'শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে, বাহিরে ঝড় বহে, নয়নে বারি ঝরে।'
অপূর্ব সেই কণ্ঠ। প্রথম দেখায় প্রেম বলে যে একটা ব্যাপার সত্যিই আছে, এটা নিতুর সাথে দেখা না হলে হয়তো কখনোই জানা হতো না জাহিদের। ঠিক যেন একটা পুতুল। সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। গান গাইছে। বিশেষ করে গানের ওই লাইনগুলো, 'ঝড়িবে পূবালী বায় গহন দূর বনে, রহিবে চাহি তুমি একেলা বাতায়নে।' ঠিক যেন জাহিদের মনের কথাগুলোই লিখেছে কাজী নজরুল, আর গাইছে নিতু।
সেই দিন থেকেই জাহিদের মাথা খারাপের মতো অবস্থা হলো। এই মেয়েকে তার চাই-ই চাই।
মনে প্রেম প্রেম ভাব এলেই তো হলো না, কথাটা নিতুকে তো জানাতে হবে।সেই উপায় নেই। বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে সে। খুবই আদরের। তার উপরে সুন্দরী।বাসা থেকে কলেজ, সার্বক্ষণিক মায়ের সাথেই দেখা যায় তাকে।ক্লাসেও যে কথা বলবে সেই উপায়ও নেই।জাহিদ এইচএসসি বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র আর নিতু মানবিক বিভাগের।জাহিদ একবার ভেবেছিল লুকিয়ে লুকিয়ে মানবিক বিভাগের ক্লাসে ঢুকে যাবে কি না।কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তাটা মাথা থেকে বাদ দিতে হলো।ধরা পড়লে কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত হবে। ভাইস প্রিন্সিপাল জয়নাল স্যার বাবার পরিচিত।নির্ঘাত বাবাকে ফোন দিয়ে বসবেন।এমনিতেই লেখাপড়ার অবস্থা ভালো না, এর মধ্যে বাবাকে খবর দিলে কেয়ামত নেমে আসবে।
মন খারাপের এমন দিনে হুট করেই সমাধান নিয়ে হাজির হলো বন্ধু শ্যামল। সে বলল, 'তুই এক কাজ কর, গানের ক্লাসে ভর্তি হয়ে যা।'
'গান! আমি?'
'হ্যাঁ, তুই। তোর গানের গলা ভালো।নিতু যেখানে গান শেখে, ওস্তাদ আকমল আলী মৃধার ওখানে ভর্তি হয়ে যা।মন দিয়ে গানটা রপ্ত কর, তাহলে নিতুর সাথে ডুয়েট গাইতে পারবি।আর সেই অযুহাতে কাছাকাছি আসার সুযোগ পাবি।এটা ছাড়া আপাতত আর কোনো উপায় দেখি না।তাছাড়া ওর এএসপি বাবা যদি জানতে পারে, তোর খবর আছে।'
কথাটা মনে ধরলো জাহিদের।কী দরকার পুলিশ ক্ষেপিয়ে? এএসপি সাহেবকে এড়িয়ে প্রেম জমাতে হলে ওস্তাদ আকমল আলী মৃধার ওখানে নজরুল গীতি শেখা ছাড়া আপাতত উপায় নেই।
নজরুল গীতির কল্যাণে জাহিদের কপাল খুলে গেল। টুকটাক কথা শুরু হলো।কবি নজরুলকে নিয়ে নিতুর পাশাপাশি তার মায়েরও অনেক আগ্রহ।সুযোগটা লুফে নিলো সে। কবি নজরুলকে নিয়ে যেখানে যত লেখা পায়, সব পড়ে।আর সেই গল্প দিয়ে নিতু এবং তার মাকে মুগ্ধ করে।নিতুর চেয়ে তার মা রেহানা বেগম মুগ্ধ হয় বেশি। ছেলেটা মেধাবী। প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে তাকান তিনি। মুগ্ধতার পাশাপাশি বিস্মিত হয় আরও একজন।ওস্তাদ আকমল আলী মৃধা।এত বছর নজরুল গীতি শেখাচ্ছেন, কিন্তু এতটা আগ্রহ নিয়ে শিখতে কাউকে দেখেননি আগে। এই ছেলে অনেকদূর যাবে।নিজের ভেতরের সবটুকু জ্ঞান উজাড় করে দিতে কার্পণ্য করেন না তিনি।
কবি নজরুলকে নিয়ে পড়তে পড়তে জাহিদের একরকম নেশার মতো হয়ে যায়।বিচিত্র এই কবি জীবন। ছেলেবেলা থেকেই সংগ্রামের, দ্রোহের, প্রেমের।বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ জন্ম নেয়া মানুষটা ছেলেবেলা থেকেই লড়েছেন দারিদ্রের সঙ্গে। নজরুলের বড় আরও তিন ভাই ছিল কিন্তু তারা জন্মের কিছুদিন পরপরই মারা যায় ।সন্তান হওয়ার পরপরই অন্যান্য ছেলেরা মারা যাওয়ায় নজরুলের দাদি তার নাম রেখেছিল দুখু মিয়া। এই দুখু মিয়াই একদিন মহাকবিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস, কী লিখেননি তিনি? নিজেই লিখতেন গান, দিতেন সেইসব গানের সুর এবং সেই সাথে গাইতেনও।এছাড়াও সাংবাদিক হিসেবে ধরেছিলেন কলম এবং রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য করেছিলেন নানা আন্দোলন।ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থানের কারণে কাজী নজরুল ইসলামকে “বিদ্রোহী কবি” হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়।
এরইমধ্যে নিতুদের বাসায় যাওয়া-আসা শুরু হয়েছে জাহিদের। পুলিশ কোয়ার্টার।নজরুলবিষয়ক আড্ডার পরে শুরু হয় গান। জাহিদের কণ্ঠ দারুণ।দরদ দিয়ে নজরুল গীতি গায়। আশেপাশের অনেকেই শুনতে আসে।যেন তার কণ্ঠের জন্যই কবি নজরুল গানগুলো লিখেছেন।মায়ের পাশাপাশি নিতুও যে ধীরে ধীরে তার ভক্ত হয়ে উঠছে সেটা জাহিদের বুঝতে কষ্ট হয় না।একদিন সে বলে, জাহিদ ভাই 'আলগা করো গো খোপার বাঁধন' এই গানটা করেন তো! ওওই দিনগুলো খুবই আনন্দে যায় জাহিদের। অন্যরকম ভালো লাগা কাজ করে।
এভাবেই একসময় হুট করে এইচএসসি পরীক্ষার সময় চলে এলো।কলেজের বিদায় অনুষ্ঠানে জাহিদ গাইলো 'আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন, খুঁজি তারে আমি আপনায়।'
নিতুকেও গাইতে হলো, 'আমি চিরতরে দূরে চলে যাব, তবু আমারে দেব না ভুলিতে।'
দুজনই নিজেদের কণ্ঠের মুগ্ধতা ছড়িয়ে দিলো সবার মাঝে।
সেটাই ছিল জাহিদের সাথে নিতুর শেষ দেখা। নিতুর বাবার সরকারি চাকরি।বদলি হয়েছিল অন্য জেলায়। পরীক্ষা দিয়েই তারা চলে যায় দিনাজপুর।জাহিদ থেকে গেল, কুমিল্লায়। একা।
বাইশ বছর পর...
জাতীয় শিশু-কিশোর সংগীত প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে অতিথি বিচারক হিসেবে এসেছেন স্বনামধন্যনজরুল গীতি গায়ক জাহিদ হাসান। চিরকুমার মানুষটার অনেক ব্যস্ততা।দেশে-বিদেশে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে থাকা এই মানুষটাকে অনুষ্ঠানে আনতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে আয়োজকদের।স্বয়ং সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী ফোন করে শিডিউল নিয়েছেন।সেরা দশজনের গান শুনবেন তিনি। এখান থেকেই নির্বাচিত করবেন সেরা গায়ক।
বেশ কিছু গান হয়ে যাওয়ার পরে, হঠাৎ একটা কণ্ঠে চমকে উঠলেন জাহিদ হাসান।বাচ্চা একটা মেয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইছে, 'আমি চিরতরে দূরে চলে যাব, তবু আমারে দেব না ভুলিতে।'
একী! এ তো সেই কণ্ঠ! এত বছর পরেও সেই কণ্ঠ চিনতে ভুল হয় না জাহিদের।মেয়েটা নিশ্চয়ই তার মায়ের কণ্ঠ পেয়েছে। তার চোখ দুটো দর্শক সাড়িতে এদিক-সেদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। দেখা হলে শুধু একটিবার জিজ্ঞেস করবে, ‘কেমন আছো নিতু? আসলেই তোমাকে ভুলতে দাওনি।'
নিতুকে দেখা যাচ্ছে না। তবুও তিনি খুঁজে যাচ্ছেন।পেছনে ভেসে আসছে নজরুলের গান।
'আমি চিরতরে দূরে চলে যাব, তবু আমারে দেব না ভুলিতে।'
[তৌফিক মিথুন : কথাসাহিত্যিক ও কবি]