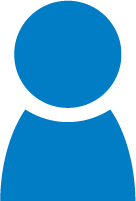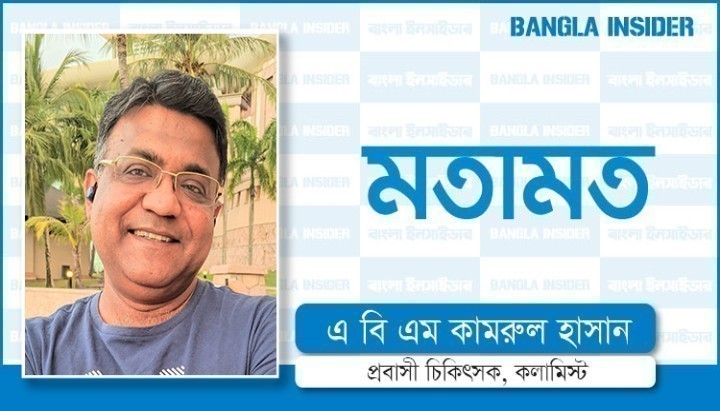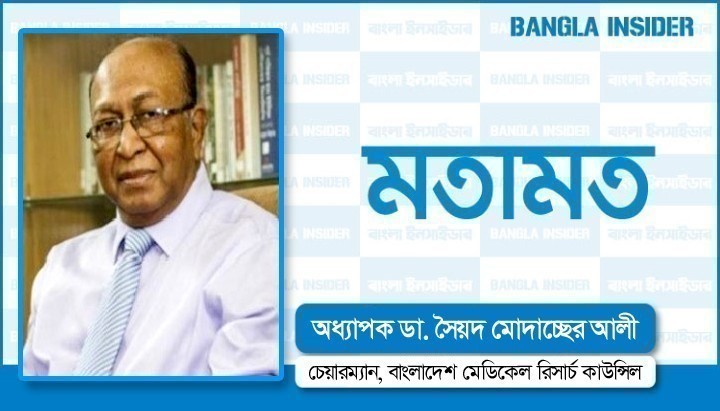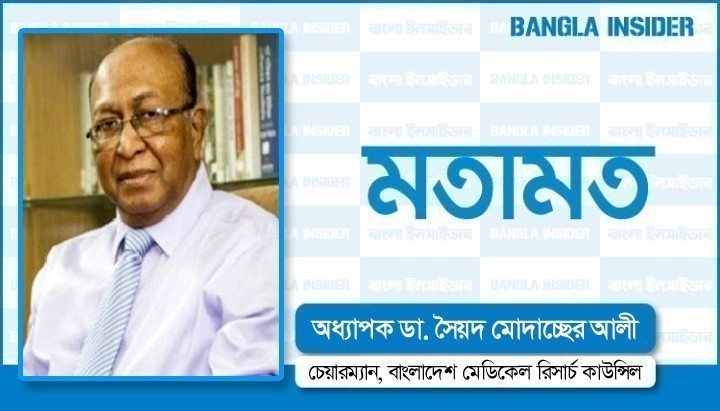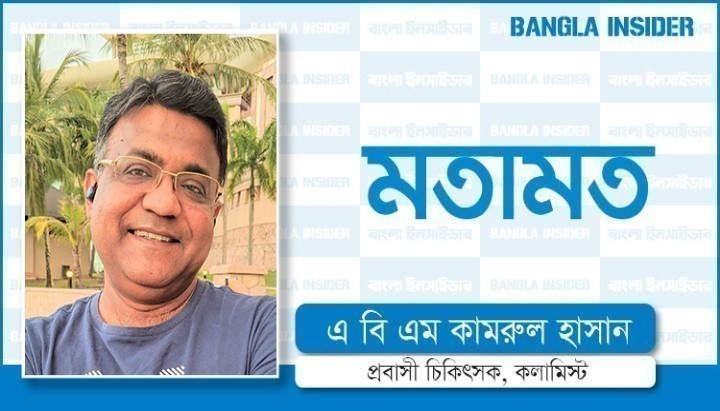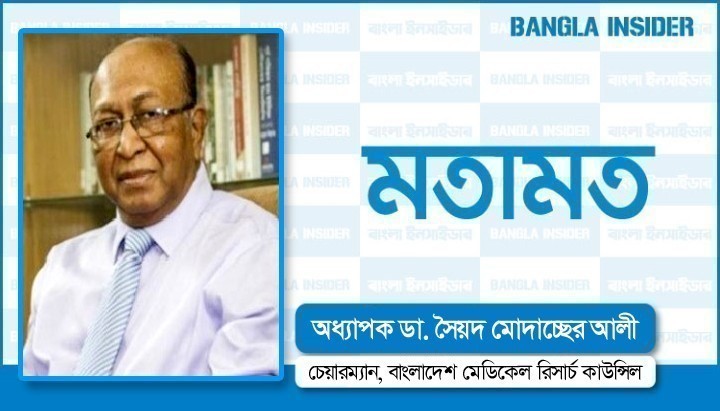‘আমি মায়ের কাছে যাব’। শেখ রাসেলকে মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর মায়ের লাশ দেখে অশ্রু সিক্ত কণ্ঠে মিনতি করেছিলেন- ‘আমাকে হাসু আপার (শেখ হাসিনা) কাছে পাঠিয়ে দিন’।
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট প্রতুষ্যে হায়েনারুপী বিপদগামী একদল সেনা কর্মকর্তা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্য এবং তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারীদের সাথে শিশু শেখ রাসেলকেও হত্যা করে। হত্যার পূর্বে খুনীরা বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত কর্মচারী আব্দুর রহমান রমাসহ শেখ রাসেলকে আটক করে। আতঙ্কিত হয়ে শিশু রাসেল কান্নাজড়িত কণ্ঠে উপরোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন, বাঁচার জন্য আকুলভাবে কাকুতি-মিনতি করছিলেন, কিন্তু পাষন্ড খুনীরা তাঁকে বাঁচতে দেয়নি।
পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারে একজন নতুন অতিথির আবির্ভাব হয়। শেখ ফজিলাতুন্নেচ্ছা মুজিবের কোলে হেমন্তের প্রহরে ভূমিষ্ঠ হয় ফুটফুটে এক পুত্র সন্তান, আনন্দে উদ্ভাসিত পুরো শেখ পরিবার, খ্যাতিমান ব্রিটিশ লেখক ও দার্শনিক, নোবেল বিজয়ী ব্যক্তিত্ব বার্ট্রান্ড রাসেলের নামানুসারে ছোট্ট শিশুটির নাম রাখা হয় রাসেল আর শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় তাঁর নাম হলো শেখ রাসেল। ১৮ অক্টোবর ২০২১, সরকারি উদ্যেগে প্রথমবারের মত ‘শেখ রাসেল দিবস’ উদযাপন করা হয় তাঁর আদর্শ, মানবিক গুণাবলি, মূল্যবোধ, আবেগ ও ভালোবাসা বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য। দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ‘ শেখ রাসেল, দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্ববিশ্বাস’ এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁকে বিশেষভাবে উপস্থাপন করাই ছিল উদ্দেশ্য।
শিশু শেখ রাসেলের গন্ডি ছিল বাবা মা, অর্থাৎ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বেগম মুজিব। একই সাথে তাঁর সময় কাটাতো দুইবোন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা এবং দুইভাই শেখ জামাল ও শেখ কামালের সাথে। সেই আদরের শিশুটির জীবন খুব ছোট পরিক্রমার মধ্যে বেড়ে উঠছিলো। যে রাসেল ছোটবেলা থেকে খেলার সাথীদের নিয়ে প্যারেড করতো, স্বপ্ন দেখতো সে বড় ভাই শেখ জামালের মতো সেনা অফিসার হবে। আজ বেঁচে থাকলে হয়তো সে সেনাবাহিনীর বড় অফিসার হতো। বেঁচে থাকলে আজ ৮ নভেম্বর ২০২১ তাঁর বয়স ৫৭ পেরিয়ে আরো ২০ দিন হতো। কিন্তু সে চিরদিন ১১ বছরের শিশু শেখ রাসেল হয়েই বেঁচে থাকবেন ইতিহাসের পাতায় ।
১৯৭২ সালে জাপানী চলচ্চিত্রকার Nagisa Oshima নির্মিত `Rahman, Father of Bengal` স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে জাপানি সাংবাদিক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় প্রশ্ন করেছিলেন-, ‘লক্ষ করছি একটি ছোট্ট ছেলে সবসময় আপনার চারপাশে ঘুরঘুর করে। ছেলেটি কে? কেন তিনি সবসময় আপনার চারপাশে থাকে?’
উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন-,‘ছেলেটির বাবা সবসময়ই কারাগারে থাকতো। ফলে সে তার বাবার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমি তার বাবা, তাই সবসময় তাকে কাছে রাখি।’
শেখ রাসেল, এক অনন্ত বেদনার কাব্য আলেখ্য। জেলজীবনে বঙ্গবন্ধুর দৈনন্দিন স্মৃতিকথা ‘কারাগারের রোজনামচা’ গ্রন্থেও তাকে নিয়ে লেখা আছে অনেক দুঃখগাঁথা। ১৯৬৬ সালের ৬ জুলাই বঙ্গবন্ধু লিখেছেন-, ‘বাচ্চারা দেখতে চায় কোথায় থাকি আমি। বললাম, বড় হও, মানুষ হও, দেখতে পারবা।’ মায়ের কোলে চড়ে মাত্র দেড় বছর বয়সে বাবাকে একনজর দেখার জন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার যেতো শেখ রাসেল। তার কাছে জেলখানাটি ছিল আব্বার বাড়ি। ১৫ দিন পরপর বেগম মুজিব তার সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে তাদেও আব্বার বাড়ি অর্থাৎ জেলখানায় যেতেন। শেখ রাসেল বাবাকে রেখে আসতে চাইতো না। কিন্তু একবুক ব্যথা নিয়ে প্রতিবার তাকে ফিওে আসতে হতো, বাবা থেকে যেতেন তার বাড়িতে। একটি শিশু ও একটি পরিবারের ক্ষেত্রে এই গল্পগুলো অনেক কঠিন। এটি একটি পরিবারের হাসি কান্না, সুখ-দুঃখ এবং সেই পরিবারের মানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পেয়েছি।
বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু যখন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেন, প্রথমবারের মতো মুক্ত জীবনের স্বাদ পেলো শিশু শেখ রাসেল। ভর্তি হলো ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলে। কচিকাঁচার দলের সঙ্গে ছিল তার অবাধ মেলামেশা। সুস¤পর্ক ছিল শিক্ষক থেকে গৃহকর্মী, সবার সঙ্গে। জাতির পিতার সন্তান হিসেবে তার মধ্যে কোনো অহংকার ছিল না। স্কুলের গেট থেকে খানিকটা দুরে গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে স্কুলে প্রবেশ করতেন যেন অন্য সতীর্থরা কষ্ট না পায়। বাড়ি থেকে দেওয়া টিফিন ভাগ করে খেতেন বন্ধুদের সঙ্গে।
শেখ রাসেলের জীবনকাল স্বল্প কিন্তু ঘটনাবহুল ও উদ্দীপনাময়। এ সময়ে তিনি কিছু লিখে যাননি বা বলে যাননি। কিন্তু তার দৈনন্দিন কর্মকান্ড ও আচার-আচরণ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে বিশেষ করে শিশুদের। তিনি প্রধানমন্ত্রীর ছেলে হিসেবে তিনি কোনো সুবিধা নেননি বা প্রকাশ করেননি। এ ব্যাপারে তাঁর প্রিয় ‘হাসু আপা’ অর্থাৎ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একাধিক স্মৃতিচারণে তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী তুলে ধরেছেন। এ ছাড়া তাঁর গৃহশিক্ষক গীতালি দাশগুপ্তাও অনেক স্মৃতি রোমন্থন করেছেন।
২০১৯ সালে শেখ রাসেলের জন্মদিনের আলোচনা সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মৃতিচারণ করে বলেন, ‘বন্দিখানায় থাকা অবস্থায় যখন যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, সেই যুদ্ধের সময় যখন আক্রমণ হতো, রাসেল পকেটে সব সময় একটু তুলা রাখতো। নিজের কানে দেওয়ার পাশাপাশি ছোট্ট জয়ের কানেও তুলা দিয়ে দিতো, যেন ওই আওয়াজে জয়ের কোনও ক্ষতি না হয়। রাসেল জয়ের প্রতি খুব খেয়াল রাখতো । সব সময়ই তার সেদিকে বিশেষ নজর ছিল।’ অপর এক আলোচনায় রাসেলের জীবনের ইচ্ছে এবং তার কোমল হৃদয়ের চাওয়া নিয়ে বলতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, ‘রাসেলের খুব শখ ছিল সে বড় হয়ে আর্মি অফিসার হবে এবং সেভাবে কিন্তু সে নিজেকে তৈরি করতো। ছোট ছোট গরিব শিশুর প্রতি তার দরদ ছিল, যখন সে গ্রামে যেতো, গ্রামের অনেক শিশুকে সে জোগাড় করতো। সে কাঠের বন্দুক বানাতো। শিশুদের জন্য মাকে বলতো কাপড় কিনে দিতে হবে। মা ঠিকই কিনে দিতেন। বাচ্চাদের সে প্যারেড করাতো।’
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তি জীবনের অজানা-অদেখা গল্প নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র ‘হাসিনা: অ্যা ডটারস টেল’-এ ছোট্ট রাসেল সম্পর্কে বলেছেন-, ‘রাসেল হওয়ার পরে আমরা ভাইবোনেরা খুব খুশি হই। যেন খেলার পুতুল পেলাম হাতে। ও খুব আদরের ছিল আমাদের। একটা ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলতো। ওইটুকু একটা মানুষ, খুব স্ট্রং পার্সোনালিটি।’ শেখ হাসিনা রচিত আমাদের ছোট রাসেল সোনা বইয়ে স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন, ‘আমাদের পাঁচ-ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট রাসেল। ছোট্ট রাসেল আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। মা রাসেলকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সংসারের কাজ করতেন, স্কুল বন্ধ থাকলে তার পাশে শুয়ে আমি বই পড়তাম। আমার চুলের বেণি ধরে খেলতে খুব পছন্দ করতো ও। আমার লম্বা চুলের বেণিটা ওর হাতে ধরিয়ে দিতাম। ও হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হাসতো । কারণ, নাড়াচাড়ায় মুখে চুল লাগতো তাতে খুব মজা পেতো।’
অন্যদিকে শেখ রাসেলের গৃহশিক্ষক গীতালি দাশগুপ্তা তাঁর স্মৃতিচারণে বলেন-, ‘পড়ানোর জন্য একটু নিরিবিলি জায়গা পাওয়া সহজ ছিল না। তদুপরি রাসেল ছিল দূরন্ত। পড়ানো শুরুর মাস খানেক পর শেখ হাসিনা একটি শাড়ি গৃহশিক্ষকের হাতে তুলে দিয়ে বলেন, ‘রাসেলকে টানা এক মাস পড়াতে পারার জন্য এই নাও উপহার। এর আগে কোনো শিক্ষক এক মাস টেকে নাই।’
গীতালি দাশগুপ্তা বলেন, ‘একবার শেখ জামালের ঘরে পড়াচ্ছি। গৌতম বুদ্ধের একটি পিতলের মূর্তি দেখিয়ে তাঁর জীবনের নানা ঘটনা বলি। মহাপুরুষদের জীবনী খুব উৎসাহ নিয়ে শুনত। পরদিন পড়াতে গেলে বঙ্গবন্ধু আমাকে বলেন, ‘মাস্টর, এত বড় সর্বনাশ করলি।’ স্বাভাবকিভাবেই শিক্ষক উদ্বিগ্ন হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর ছোট ছেলেকে কোনো ভুল শিক্ষা দিয়েছে কী? বঙ্গবন্ধু তাকে কাছে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, তুই গৌতম বুদ্ধের জীবন কাহিনী রাসেলকে বলেছিস? ও গত রাতে একটা পর্যন্ত জেগেছিল। আমি কাজ শেষে ঘুমাতে গেলে বুদ্ধদেব সম্পর্কে আরও জানতে চায়।’ এমন অদম্য কৌতূহল ছিল শেখ রাসেলের।
১৯৭২ সালের জুলাই মাসে বঙ্গবন্ধু চিকিৎসার জন্য লন্ডন যান। সেখানে অস্ত্রোপচারের সময় পরিবারের অন্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিল। বঙ্গবন্ধু সুস্থ হলে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বাজারে আসা নতুন সিনথেটিক শাড়ি কিনলে রাসেল বায়না ধরে তার শিক্ষকের জন্যও একটা কিনতে হবে। দুই বোন শাড়ি নিয়ে ফিরলে রাসেলের মনে হয় যে, তাঁর শিক্ষকের জন্য কেনা শাড়িটির চেয়ে দুই আপার শাড়ি সুন্দর। এ নিয়ে অভিমান করে, কান্নায় বুক ভাসায়। শিক্ষক শাড়ি পেয়ে খুব খুশি হয়েছে এটা জানানোর পরই কেবল রাসেলের মন ভাল হয়। শিক্ষকের প্রতি তার এই অগার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নতুন প্রজন্মের জন্য মাইলফলক হয়ে থাকবে।
শেখ রাসেলের হাসু আপু ১৫ আগস্টের ভয়াবহ কালরাতের মাত্র কয়েকদিন পূর্বেই সুদূর জার্মানে স্বামীগৃহে চলে যান, সাথে আরেক বোন শেখ রেহানাও। হাসু আপু জার্মান যাওয়ার সময়, ‘আমি হাসু আপুর সাথে যাবো, দেনা আপুর সাথে যাবো’ বলে খুব কেঁদেছিল রাসেল। শেখ রেহানাকে ‘দেনা আপু’ বলে ডাকতেন শেখ রাসেল। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও সেই হাসু আপুর কাছে যাওয়ার জন্যেই আকুতি-মিনতি করেছিল, মায়ের পর হাসু আপুকেই নিরাপদ আশ্রয় মনে করেছিলেন তিনি।
শেখ রাসেল দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক একান্ত সচিব ওয়াহিদা আক্তার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, ‘শেখ রাসেল এর হাসু আপু স্বামীর কর্মস্থল জার্মানে গিয়ে ছোট ভাই রাসেলের পছন্দের খেলনা কিনেছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজও ঐসকল খেলা সামগ্রী আগলে রেখেছেন।’
বাঙালি জাতির জাগরণকালে সৌভাগ্যের প্রতীক হয়ে জন্মেছিল যে শিশু, জান্তাদের দানবীয় ষড়যন্ত্র তাকে নিয়ে গেছে ইতিহাসের ভাগ্যহত নক্ষত্রদের কাতারে। সেই দেবশিশুর নাম শেখ রাসেল, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র। বন্দি পিতার দীর্ঘ জেলজীবনের সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে মায়ের কোলে চড়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়মিত যেতো ছোট রাসেল। কিন্তু বেগম ফজিলাতুন্নেচ্ছা মুজিবকে গোয়েন্দারা কোলের শিশু রাসেলকে নিয়ে জেরা করতেন। বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেচ্ছা বিরুক্তি ও প্রচন্ড ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, ‘বাপের পিছনে গোয়েন্দা লেগেছিল ২৮ বছর বয়সে, আর ছেলের পেছনে লাগলো দেড় বছর বয়সেই?`
ছোট্ট রাসেলের আর বড় হওয়া হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের ৬৭৭ নম্বর বাড়িতে, বাবা-মা ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। মাত্র দশ বছর দশ মাস বয়সের এক নি¯পাপ শিশু, কী দোষ ছিল রাসেলের! সেই বিভিষীকাময় রাতে, ঘাতকরা যখন বিশ্ব ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিলো, প্রাণে বাঁচার জন্য মিনতি জানিয়েছিল ছোট্ট রাসেল। মায়ের কাছে যাবে বলে যার আকুতি, গলা শুকিয়ে যাওয়া কান্না যার চোখেমুখে ছিল, ভয়ে থরথর করে যে কাঁপছিল তাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাবে বলে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে নরপিশাচদের একজন। বাঁচতে দিল না রাসেলকে, সীমারদের মনে বিন্দুমাত্র দয়ামায়া ছিল না।
সকলের এতো আদরের ছোট্ট শেখ রাসেল ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের কালো রাতের শেষ প্রহরে আতঙ্কিত হয়ে মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করতে থাকলে নরপিশাচরা, মায়ের কাছে নিয়ে যাবে বলে, গৃহকর্মী আব্দুর রহমান রমার হাত থেকে হেঁচকা টান দিয়ে শেখ রাসেলকে ছিনিয়ে নেয়। এরপর মৃত্যু পর্যন্ত পরবর্তি সময়টুকু তাঁর কেমন কেটেছিল, কতটুকু মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক হয়েছিল তা ঐ ঘাতকেরাই জানে। তবে মনের চোখ দিয়ে যদি দেখি বা অনুমান করি তবে হয়তো এভাবে বলা যায়-, ‘মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়ার পথে রাসেল দেখলো সিঁড়িতেই পড়ে আছে তাঁর পিতার লাশ । হতভম্ব সে। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলো না। এ কি করে হয়? স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে বাঙালি জাতির পিতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লাশ পরে আছে সিঁড়িতে? কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই হায়েনারা তাঁকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গেল মায়ের কাছে। মায়ের লাশ দেখে, মায়ের নিথর বুকে আছড়ে পড়ে মা, মা বলে বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে আর্তনাদ করেছিল সে। না, মায়ের কোন সাড়া শব্দ নেই। মা তাঁকে বুকে জড়িয়ে আদর করে বলেনি, ‘ভয় নাই বাবা। কিচ্ছু হবে না। আমিতো আছি তোমার কাছে’। মা-বাবার পর ঐ ছোট্ট শিশু দেখলো তাঁর বড় ও মেঝ ভাই ও ভাবীদের লাশ।’
আমরা পরিবারের একজন নিকটাত্মীয়র মৃত্যুতে ভেঙ্গে পরি, চাপা ব্যথা অনুভব করি, সেই ব্যথা প্রশমনে আর্তনাদ করি, নীরবে অশ্রু ত্যাগ করি। তাহলে শিশু শেখ রাসেল অল্পক্ষণের মধ্যে বাবা-মা সহ নিজ পরিবারের এতজন সদস্যের মৃত্যু এবং তাঁদের সারিসারি লাশ দেখে কী অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করেছেন? হয়তো ভেবেছেন, হাসু আপু, দেনা আপুর সাথে জার্মানি বেড়াতে গেলেই ভালো হতো। হয়তো ভেবেছেন, হাসু আপু আমাকে নিয়ে গেল না কেন? এমনি অবস্থায়ই হঠাৎ গর্জে উঠে ঘাতকের আগ্নেয়াস্ত্র, ঝাঁঝড়া হয়ে যায় শেখ রাসেলের বুক, ঘাতক বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সাঙ্গ করে দেয় তাঁর জীবন প্রদীপ ।
স্বল্প ফুটেই সুরভী ছড়াতে শুরু করেছিল যে ফুল, সেটি অকালে ঝরে যাওয়ার শোকে আজও প্রতি ভোরে বাঙলার মাঠে-ঘাটে অজস্র বকুল ফুটে, ঝরে শেফালী-হাসনাহেনা। ঝরা বকুলের প্রতিবিম্বে বাংলার প্রতিটি শিশুর প্রাঞ্জল হাসির শব্দ ভেসে ওঠে- ভেসে ওঠে রাসেলের মায়াবী মুখখানি, শিশুদের ভেজা কপোল ছুঁয়ে নামে রাসেলের চোখের পানি। এ পানিতে পবিত্র হয়ে বর্তমান প্রজন্ম শহীদ শেখ রাসেলের আদর্শ, মানবিক গুণাবলী, মূল্যবোধের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করবে, ব্যক্তি জীবনে বয়ে আনবে ইতিবাচক পরিবর্তন সেই প্রত্যাশা সকলের।
১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের কালো রাতের শেষ প্রহরে শেখ রাসেল আতঙ্কিত হয়ে মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য কাকুতি-মিনতি করেছিল, সে দৃশ্য কল্পনায় আমার নিবেদন নিচের কাব্য-কথা।
আমি মায়ের কাছে যাবো
তোমরা আমাকে মেরো না
আমি মায়ের কাছে যাবো
তোমরা আমার দুবাহু ছাড়ো
আমি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবো।
আমি ভোরের শিশির হবো
আগুনমুখার শুভ্র ঢেউ হবো
ধানের কচি ডগার বিন্দু হবো
স্নেহসুধায় বাংলাদেশকে ভরিয়ে দেবো।
তোমরা আমাকে মেরো না
আমি বন্ধুদের কাছে যাবো
নাড়ার আগুনে ছোলা পুড়িয়ে
বাংলার মাঠে বসে খাবো।
আজান দিয়েছে, ভোর হয়েছে
পড়াশোনার টাইম হয়েছে, স্কুলেতে যাবো
তোমরা আমাকে মেরো না
আমি আমার মায়ের কাছে যাবো।
লেখক: সহযোগী অধ্যাপক
সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা