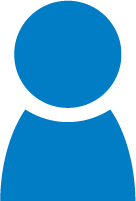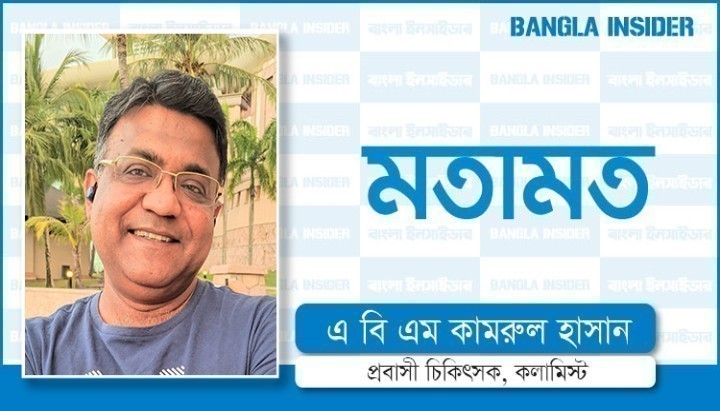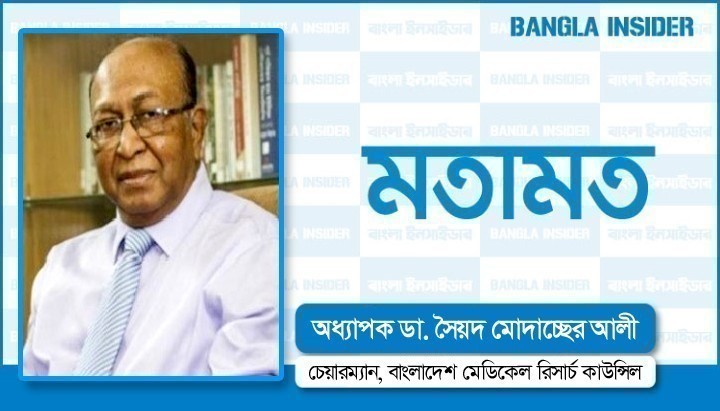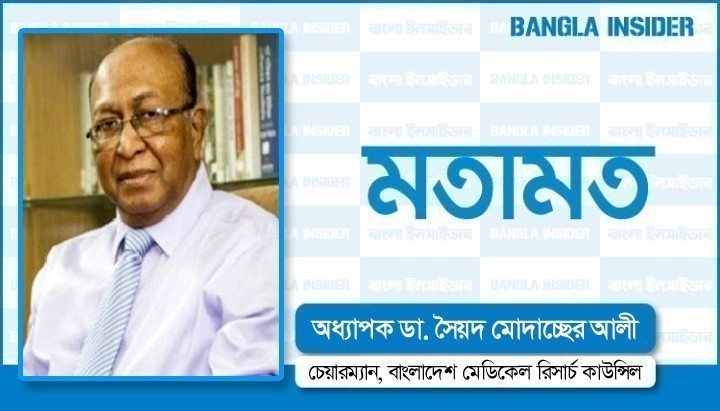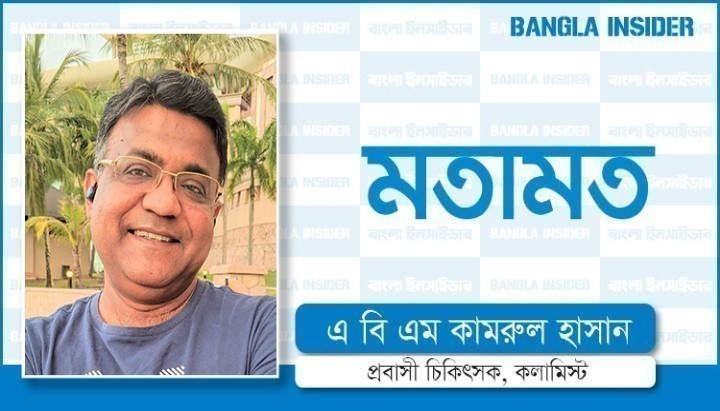আজকাল গণমাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগনের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, অনিয়ম, দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি নিয়ে প্রায়শঃ খবর প্রকাশিত হতে দেখছি। আমিও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। কোন কোন গণমাধ্যমের খবরে আমার নামটিও রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে এই লেখা। লেখাটির শিরোনাম কি দেব বুঝতে পারছি না। অগত্যা ‘একজন উপাচার্যের কৈফিয়ত’ এই নাম দিয়েই লেখাটি শুরু করলাম।
আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা থেকে অবসর নেয়ার পর পরই ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করে আসছি। আমার দায়িত্ব পালনের প্রথম দিকে প্রায় এক/দেড় বছর ছিল করোনাকাল। সে সময় আমি ও আমার স্ত্রী দু’জনই দু’বার করোনা আক্রান্ত হয়েছিলাম। করোনাকালে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যয় এই বিশ্ববিদ্যলয়েও কম-বেশী সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও উপাচার্যের অফিস চলতো প্রায় স্বাভাবিক সময়ের মত। এসময়ে আমাদের প্রধান চেষ্টা ছিল অনলাইন এবং পরবর্তীতে অনলাইন-অফলাইন সমন্বিত মোডে কি করে ক্লাস-পরীক্ষা চালু রাখা যায়। আমার একটি তৃপ্তির অনুভূতি যে, তখন থেকে এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষনা কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে অব্যহত রয়েছে; নানারকম প্রতিকুলতা সত্বেও ক্লাস-পরীক্ষা একদিনের জন্যও বন্ধ থাকেনি কিম্বা তেমন কোন অস্থিরতাও তৈরী হয়নি।
গত এক/দেড় বছর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে দৃশ্যপট পাল্টাতে শুরু করেছে। এখানে বিশেষ করে কিছু সংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন যাঁরা কম-বেশী সব আমলে উপাচার্যের প্রীতিভাজন হয়ে প্রশাসনকে কব্জায় নিয়ে নিজেদের মত করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করতে চান। এমনটি না হলে সাধারনতঃ কোন উপাচার্যই তাঁদের মেয়াদ পূর্ণ করতে সক্ষম হন না। জন্মকাল থেকে ১৩ জনের মধ্যে এ পর্যন্ত এক/দু’জন উপাচার্য কেবল মেয়াদ শেষ করতে পেরেছেন। যাহোক এই শিক্ষকগণের কেউ কেউ সুবিধা করতে না পেরে অন্তত এক-দু’জন শিক্ষক আমাকে এমনও বলেছেন যে, পূর্বে কম-বেশী সকল উপাচার্য তাদের নিয়ে চলেছেন, অথছ আমার সময়ে তিনি/তারা একটু ঝাড়ুদারের দায়িত্বও পাচ্ছেন না। এরপর থেকে দিনে দিনে শুরু হয়েছে অনলাইন ও বিভিন্ন ডিজিটাল প্লাটফর্মে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার আর অপপ্রাচারের প্লাবন। একটি একটি করে তা’ পাঠকের জন্য তুলে ধরতে চাই।
প্রায় দেড় বছর পূর্বে হঠাৎ করে একদিন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ভ্যানে মাইক লাগিয়ে আমার কণ্ঠ-সাদৃশ্য বাক্যাংশের একটি অডিও বাজিয়ে কে বা কারা প্রচার করতে থাকে যে, উপাচার্য হিসেবে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ বানিজ্য করছি। মূলত : ঘটনাটি ছিল এমন যে, ওই সময়ে শিক্ষক শুন্য একটি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিল। সেখানে মাত্র তিনটি আবেদনপত্র জমা পড়েছিল এবং নিয়োগ পরীক্ষায় দু’জন প্রার্থী উপস্থিত হয়েছিলেন। আমরা প্রার্থী স্বল্পতার জন্য ওই পরীক্ষা বাতিল করে পুনঃবিজ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত নেই। এর কয়েকদিন পর আমি আমার এক ছাত্রকে (যিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও বটে) অনুরোধ করি যে, তোমরা ঢাকায় থাকো, আমাদের শিক্ষক দরকার। তুমি আমাদের একটু সাহায্য করো- তোমার বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিতজনদের বলো তারা যেন এখানে দরখস্তকরে। উত্তরে সে জানায় যে, স্যার ওখানে কেউ যেতে চায় না। তাছাড়া একটা দরখস্ত করতে গেলে ৫/৬ হাজার টাকা ব্যয় হয়-তাই কেউ দরখস্ত করতেও উৎসাহি হয় না। আমি তখন জবাবে বলি-ওরা তোমাদেরই বন্ধুবান্ধব, প্রয়োজনে টাকা পয়সা দিয়ে সহায়তা করে তাদের দরখস্তকরতে একটু উদ্বুদ্ধ করো। এই কথোপকথনের ‘টাকা-পয়সা দিয়ে’ এই বাক্যাংশটুকু নিয়ে কিভাবে তারা একটি অডিও বানিয়ে প্রচার আরম্ভ করে যে, উপাচার্য নিয়োগ বানিজ্য করছেন। শুনেছি এভাবে তারা একাধিক অডিও [যা’ শুধুমাত্র একজন অর্থাৎ আমার কন্ঠ সাদৃশ্য এবং তা’ মিথ্যা, বানোয়াট, খÐিত, এক পক্ষীয় (অন্য প্রান্তে কে কি বলছেন তার কোন হদিস নেই) এবং হয়তোবা সুপার এডিটেড] বানিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে উপাচার্যকে কিভাবে হেনস্থা করে তাদের অপ-ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করানো যায় সে চেষ্টাই তারা অনবরত করে যাচ্ছে।
আমি আমার কণ্ঠ সদৃশ্য আরও একটি অডিও’র বক্তব্য শুনেছি। এটিও ছিল এক পক্ষীয় এবং খÐিত। আমার আলাপন সেখানে পূর্ণাঙ্গ নেই। অপর প্রান্তে কে কথা বলছেন তারও কোন অস্তিত্ব নেই। অডিও’র বিষয়টি হলো-আমি কোন একজনকে বলছি যে, ‘আপনার নির্দিষ্ট প্রার্থীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবেন’ ....................আমি দেখবো। সাধারণত: কোন নিয়োগের আগে অনেকেই অনুরোধ করেন যাতে তার প্রার্থীকে যেন একটা চাকুরী দেয়া হয়। বিশেষ করে জনপ্রতিনিধিগণ অথবা কোন রাজনীতিক/সামাজিক ব্যক্তিত্ব ১টি পদের জন্য কখনও কখনও ৩/৪ জন প্রার্থীর রোল নম্বর পাঠিয়েও এ ধরনের অনুরোধ করেন। ধরা যাক, এদের মধ্যে একজনেরই চাকুরিটি হয়েছে। অধিকাংশ সময়ে সে ফিরে গিয়ে তার জন্য অনুরোধকারীকে সুখবরটি জানায় কি-না তা’ আমার জানা নেই। কিšদ প্রায়শ এমনটি ঘটে যে, বাকী যাদের চাকারী হয় না তারা গিয়ে তাদের স্ব-স্ব নেতা বা অনুরোধককারীকে এই বলে বিষিয়ে তোলে যে, উপাচার্য আপনার অনুরোধের কোন দামই দিলেন না। এমন পরিস্থিতিতে মন খারাপ করে জনপ্রতিনিধিগণ বা রাজনৈতিক/সামাজিক নেতৃবৃন্দ টেলিফোন করে আমাকে হয়তো বলে থাকেন-আপনি আমার একটা অনুরোধ রাখলেন না। এমতপরিস্থিতিতে আমাকে জবাব দিতে হয় যে, এরপর তাহলে আপনার সুনির্দিষ্ট প্রার্থীকে আমার সাথে দেখা করতে বলবেন ............. আমি দেখবো। এই ‘দেখা করতে বলা’ কি নিয়োগ বানিজ্যের সাথে যায়? এভাবে একটি গোষ্ঠী কেবলই মিথ্যাচার করে উপাচার্য হিসেবে আমাকে নাজেহাল করার অনবরত চেষ্টা করে যাচ্ছে যাতে আমি নতি স্বীকার করে তাদের হাতের পুতুল হয়ে কাজ করি। মিথ্যার কাছে নতি স্বীকার করে চেঁচে থাকার ইচ্ছে বা অভিপ্রায় আমার নেই।
আমার বিরুদ্ধে না-কি অভিযোগ রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের নির্মাণ কাজে আমি অতিরিক্ত কাজ দেখিয়ে ৬ থেকে ৮ কোটি টাকার বিল বানিয়ে অর্থ-আত্মসাৎ করেছি বা করার চেষ্টা করেছি। রুচিহীন এবং উদ্ভট এসব অভিযোগের জবাব দিতেও আমি ইতস্তবোধ করছি। উল্লেখ্য নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি পরিমাপ করে ৩/৪ মাস অন্তর পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর বিল ঠিকাদারের প্রদান করা হয়। এই কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে সাইট ইঞ্ছিনিয়ার-সহকারী ইঞ্জিনিয়ার-নির্বাহী বা তত্ত¡াবধায়ক ইঞ্জিনিয়ার-প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক প্রমুখ কর্তৃক পরীক্ষিত ও নীরিক্ষিত কাজের পরিমাপ এবং প্রস্তাবিত বিল ঠিক থাকলে তা’ চলে যায় ট্রেজারার মহোদয়ের কাছে। তখন তাঁর নেতৃত্বে গঠিত ভিজিলেন্স টিম সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন করে সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে তা’ উপাচার্যের নিকট অনুমোদনের জন্য উপাস্থাপন করা হয়। বর্নিত ক্ষেত্রে আমার নিকট ফেবরিকেটেড ওই বিল অনুমোদনের জন্য কোন ফাইলই উপস্থাপিত হয়নি। বরং ৪/৫ মাস পূর্বে আমার দপ্তরে একটি বেনামী চিঠি আসে যে, নির্মান কাজ বেশী দেখিয়ে আট কোটি টাকার একটি বিল প্র¯দত করে তা’ প্রক্রিয়া করা হয়েছে। এই চিঠির সাথে ফটোকপিকৃত কিছু ডকুমেন্ট ছিল যা’ দেখে অভিযোগের সত্যতা থাকতে পরে বলে আমার কাছে মনে হয়েছিল। আমি তাৎক্ষনিকভাবে এই চিঠির ভিত্তিতে একজন সিন্ডিকেট সদস্যকে আহবায়ক এবং খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপককে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করি। ইতোমধ্যে কমিটি তাদের রিপোর্ট প্রদান করেছে। পরবর্তী সিন্ডিকেট সভায় তা’ উপস্থাপিত হবে এবং সিন্ডিকেট সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। এখানে উপচার্য হিসেবে আমি কি দূর্নীতি করেছি আশাকরি পাঠকবর্গ তা’ উপলব্ধি করতে পারছেন।
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যাপারে দু’একটি অনলাইন পত্রিকায় নিউজ করানো হচ্ছে যে, প্রকল্প সাইটে মাটির নিচে পাইলিং এর জন্য যে রড ঢোকানো হয়েছে সেখানেও না-কি উপাচার্য হিসেবে আমি দূর্নীতি বা অনিয়ম করেছি। যেকোন নির্মাণে পাইলিংয়ের জন্য মাটির নিচে রড কতটুকু ঢুকাতে হবে তা’ নির্ভর করে সয়েল টেস্ট রিপোর্টের উপর। আমি উপাচার্য হিসেবে যোগদানের বহু পূর্বেপ্রকল্পটি অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় সয়েল টেস্ট করে প্রকল্প দলিল প্রনীত ও অনুমোদিত হয়েছিল।
আমার সময়ে এসে প্রকল্পের কাজ শুরুর পর যখন পাইলিং আরম্ভ হয় তখন সংবাদকর্মীদের মাধ্যামে আমি জানতে পারি যে, প্রকল্প দলিল অনুযায়ী মাটির নিচে যে পর্যন্ত রড ঢোকানোর কথা (ধরা যাক ৫০’) তার চেয়ে কম গভীরতায় রড ঢুকিয়ে পাইলিং এর প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। আমি সাথে সাথে প্রধান প্রকৌশলীকে বিষয়টি দেখতে বলি এবং ভিজিলেন্স টীম পাঠিয়ে তাদের ব্যবস্থা নিতে বলি। ভিজিলেন্স টীমের সদস্য এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসের কর্মকর্তাগণ আমাকে এসে রিপোর্ট করেন যে, সয়েল টেস্টিং এর ভিত্তিতে যেভাবে পাইলিং এর রড প্রকল্প অনুযায়ী মাটির নিচে ঢোকানোর কথা বাস্তবে তা’ ঢোকানো যাচ্ছে না। রড ঢুকছে তার কম (কম-বেশী ৪০’)। এ পর্যায়ে সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে পুনরায় সয়েল টেস্ট ও তা’ ভেটিং করিয়ে টেস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী সেই গভীরতায় রড ঢুকিয়ে পাইলিং এর কাজ করা হয়েছে। এই বিষয়টি প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটির (যেখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আই এম ই ডি, ইউ জি সি-র প্রতিনিধিগণ থাকেন) সভায় অবহিত করা হয়েছে। এখানে উপাচার্য কিভাবে রড কম গভীরতায় ঢুকিয়ে দূর্নীতি বা অনিয়মের আশ্রয় নিয়েছেন সে বিবেচনার ভার পাঠকদের উপর ছেড়ে দিলাম।
আমি প্রায়শঃ শুনি যে, আমার বিরুদ্ধে না-কি আরও একটি অভিযোগ যে, আমি অবৈধভাবে কর্মকর্তাদের উচ্চতর বেতন স্কেল প্রদান করেছি। বিষয়টি আমি নিচেয় ব্যাখ্যা করছি। তার আগে বলে রাখা দরকার যে, এটি ডেপুটি এবং এসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার পর্যায়ের সকল কর্মকর্তার জন্য একটি আর্থিক সুবিধা প্রদানের বিষয়। এটি প্রদানের ক্ষেত্রে আর্থিক নিয়মের কোন ব্যত্বয় ঘটলে ইউ জি সি অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা বছরে একাধিকবার অডিট করেন তারা আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন। কিন্তু উপাচার্যের দূর্নীতির উপাদান এখানে কি থাকতে পারে তা’ আমার বোধগম্য নয়।
ঘটনাটি ছিল এমন যে, ২০১৫ সালের জাতীয় বেতন স্কেল কার্যকর হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি এবং এসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার পর্যায়ের কর্মকর্তাদের একটি নির্দিষ্ট সময় পরে একধাপ উচ্চতর স্কেলে বেতন উন্নীত করে তা’ প্রদান করা হতো। ২০১৫ সালের বেতন স্কেল কার্যকর হওয়ার পর এই সুযোগ রহিত করা হয়। আমি ২০২০ সালের শেষ দিকে করোনাকালে যখন এখানে উপাচার্য হিসেবে যোগদান করি তার কয়েকদিনের মধ্যে ওই পর্যায়ের কর্মকর্তাদের একটি অংশ এসে আমার সাথে দেখা করে দাবী জানায় যে, এই স্কেল উন্নীতকরণ ঘটবে উপ-রেজিস্ট্রার ও সহকারী রেজিস্ট্রার পর্যায়ের সকল কর্মকর্তার ক্ষেত্রে। কিšদ পূর্বের প্রশাসন ২০১৯ সালে বেছে বেছে তাদের অনুগত কর্মকর্তাদের এই সুযোগ প্রদান করেছেÑ কাজেই অবশিষ্টদেরও এটি দিতে হবে। বিষয়টি নিয়ে ২০২২ সালের দিকে তারা একটি বড় আন্দোলন গড়ে তোলে এবং প্রায় ২ মাস ধরে কর্মবিরতি পালন করে। এক পর্যায়ে গিয়ে এবিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি দেখতে পায় এই সুবিধাটি ২০১৫ সালের পে-স্কেলের সময় রহিত করা হলেও ঢাকাসহ রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীর নগর, মওলানা ভাষানী বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি তখনও চালু রয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সুবিধা পূর্বে অলরেডি কর্মকর্তাদের একটি অংশকে দেয়া হয়েছে এবং কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনও এই সুবিধা প্রদান বহাল রয়েছে। এই বিবেচনায় কর্মকর্তাদের আর একটি অংশ যাতে বঞ্চিত না হয় (অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনকার পরিস্থিতি) সেসব বিবেচনায় নিয়ে কমিটি বঞ্চিতদের জন্য স্কেল উন্নীত করণের সুপারিশ করে। এই সুপারিশ ফিন্যান্স কমিটি এবং সিন্ডিকেটে এই শর্তে অনুমোদন দেয়া হয় যে, এব্যাপারে ভবিষ্যতে কখনও যদি অডিট আপত্তি উত্থাপি হয় তাহলে এই উন্নীতকরণ বাতিল হবে এবং কর্মকর্তাদের দেয়া অর্থ ফেরত দিতে হবে। বিষয়টি সে সময় এভাবে ফয়সালা করা হয়েছে। এখানে উপাচার্য হিসেবে আমার দূর্নীতির জায়গাটি কোথায় তা’ আমার বোধগম্য নয়। আমি মনে করি এটি বড়জোর একটি অডিট আপত্তি/অনাপত্তির বিষয়। ব্যক্তি বা সামস্টিক দূর্নীতির সংগার সাথে এটি যায়-কি?
উপাচার্য হিসেবে আমার বিরুদ্ধে আরও একটি অভিযোগ সম্পর্কে দু’একটি অনলাইন পত্রিকা এবং নষ্ট-ভ্রষ্ট ওই গোষ্ঠীর প্রচার-প্রপাগাÐা থেকে জেনেছি যে, আমি আমার ঢাকার বাসার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকায় সিকিউরিটি নিয়োগ দিয়েছি। এটি সর্বৈব মিথ্যা রটনা। ঢাকায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রেস্ট হাউজ রয়েছে। সেখানে মাত্র ২ জন কর্মী (একজন কুক, একজন সাধারণ) কাজ করে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিদিন গড়ে ১৫/২০ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা (কখনও কখনও তাদের পরিবার-বিশেষ করে চিকিৎসার জন্য) ঢাকায় গিয়ে রেস্ট হাউজে অবস্থান করেন। উল্লেখ্য এসময়ে বেশ কয়েকমাস ধরে রেস্ট হাউজ ভবনের সংস্কার কাজ চলছিল। রেস্ট হাউজে ইবি পরিবারের সদস্যগণ দিনে-রাতে (কোন ধরাবাধা সময় নেই) যাতায়াত করেন। তাদের জন্য বার বার গেট খোলা এবং লাগানোর মত কোন জনবলই সেখানে ছিল না। অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী স্থায়ী জনবল নিয়োগেরও তেমন কোন সুযোগ ছিল না। সেসময় এস্টেট অফিস থেকে আমাকে জানানো হয় যে, ঢাকা রেস্ট হাউজে কিছু সিকিউরিটি ডেপুট (নিয়োগ নয়) করা দরকার। ইবি ক্যাম্পাসের কয়েকজন আনসার দিয়ে সেটা করা যায় কি-না সে ব্যাপারে এস্টেট অফিস আমাকে অবহিত করে যে, আনসার ডেপুট করা অনেক খরচের ব্যাপার এবং বারো জনের নিচেয় আনসার কর্তৃপক্ষ জনবল দিবে না। বিকল্প হিসেবে স্বল্প সংখ্যক (৫/৬ জন) জনবল বরং সিকিউরিটি সংস্থা থেকে ডেপুট করা যায়। সে অনুযায়ী যথাযথ বিধি বিধান প্রতিপালন করে ফিন্যান্স কমিটি এবং সিন্ডিকেটের অনুমোদন নিয়ে ঢাকা রেস্ট হাউজের জন্য ছয়জন সিকিউরিটির সেবা হায়ার করা হয়েছে। উপাচার্য হিসেবে প্রায়শ আমাকে শিক্ষা মন্ত্রনালয়, ইউ জি সি, ধর্ম মন্ত্রনালয় (ইসলামী ফাউন্ডেশন), এ ইউ বি-র সভা এবং গুচ্ছের সভাসমূহে যোগাযোগসহ প্রভৃতি কারণে ঢাকায় যেতে হয়। সেকারণে শিফট অনুযায়ী সিকিউরিটি সদস্য যারা রেস্ট হাউজে ডিউটি করে তাদের একজন রেস্ট হাউজে এবং একজনকে উপাচার্যের বাসায় ডিউটি বন্টন করা হয়েছে মাত্র। উপাচার্যের বাসার জন্য কোন সিকিউরিটি সদস্য নিয়োগ দেয়া হয়নি। উপাচার্যের বাসার জন্য সিকিউরিটি নিয়োগ দেয়া হয়েছে এটাও একটি মিথ্যা প্রচারণা।
প্রকৃতপক্ষ আমি জানিনা উপাচার্য হিসেবে আমার বিরুদ্ধে আর কি কি অভিযোগ রয়েছে? অভিযোগগুলো কিসের ভিত্তিতে করা হয়েছে? অভিযোগগুলো কারা করেছে তা’ও আমার জানা নেই। যাহোক একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রচার প্রপাগান্ডার কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে ইউ জি সি-কে দিয়ে একটি তদন্ত কমিটি করিয়েছে। কমিটির সদস্যবৃন্দ আমাকে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে লিখিত মতামত/বক্তব্য দিতে বলেছিলেন। আমি তাঁদের নিকট লিখিত ভাবে (ডকুমেন্টসহ) আমার বক্তব্য প্রেরণ করেছি।
আশাকরি পাঠকবৃন্দ বিষয়সমূহ অবহিত হয়ে একজন উপাচার্যকে কিভাবে কেবল রসালো, মিথ্যা, বানোয়াট এবং বস্তনিষ্ঠহীন অভিযোগ তুলে তাঁকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে তা’ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। উপাচার্য এবং ব্যক্তি মানুষ হিসেবে আমি শুধু এতটুকুই বলবোÑআমি কোন দূর্নীতি করে উপাচার্যের এই চেয়ারকে কলুসিত করিনি; আমি স্বার্থান্বেষী নষ্ট-ভ্রষ্ট কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে মাথা নত করবো না।
অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম
উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।