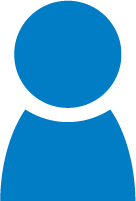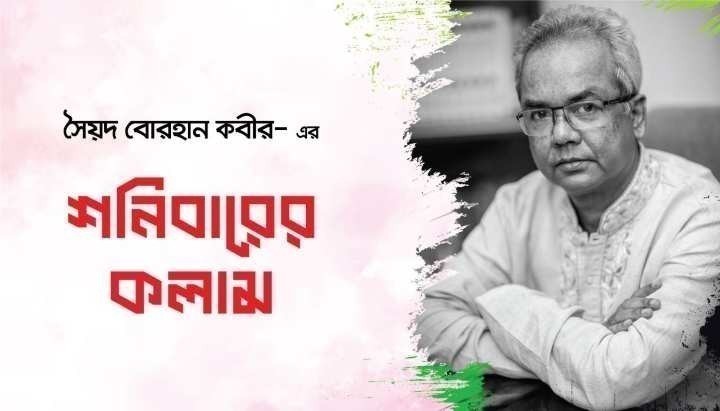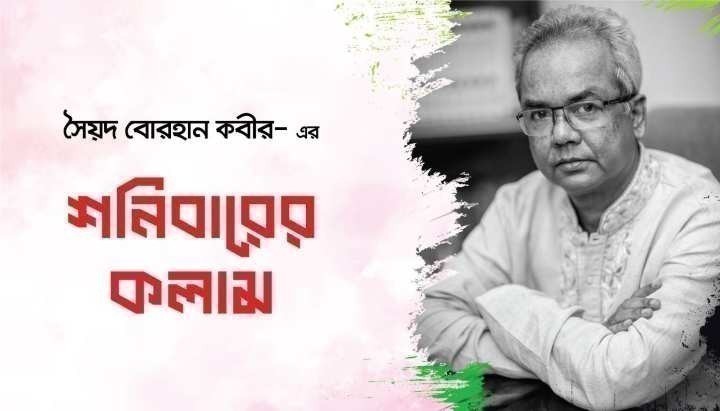‘চাটার গোষ্ঠীর যন্ত্রণায় মানুষ শেষ হয়ে গেল। যারে যেদিকে পাঠাই কেবল চুরি করে।... দুর্নীতি, দুর্নীতি, উহঃ আল্লাহ। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি পাগল হয়ে যাব। এত দুর্নীতিবাজ যে আগে কোথায় ছিল, জানি না।’ না, এটি সাম্প্রতিককালের কোনো রাজনৈতিক নেতার বক্তব্য নয়। ১৯৭৩ সালের ১২ নভেম্বর ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এই মন্তব্য করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এই উক্তি যেন বাংলাদেশের আজকের বাস্তবতা।
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যদি এখন কোনো অনুষ্ঠানে বা জনসভায় একই বক্তব্য দেন, তাহলে তিনিও বিপুল করতালিতে অভিষিক্ত হবেন, সন্দেহ নেই। শুক্রবার রাতে টেলিভিশনে বিমানবন্দরে মালয়েশিয়া যাওয়ার অনিশ্চিত অপেক্ষায় থাকা মানুষের কান্না দেখেছিলাম। নিজের অজান্তেই কখন অশ্রুসজল হয়েছিলাম, জানি না। এই গরিব মানুষের সঙ্গে কারা প্রতারণা করেছে? সরকারের ভেতরে থাকা কিছু সংসদ সদস্য, তাদের স্ত্রী ও কন্যা। এই ৩০ হাজার মানুষকে পথে বসানোর দায় কে নেবে? প্রতারিত এই মানুষের আর্তনাদ শুনে বঙ্গবন্ধুর উক্তি মনে পড়ল।
শুধু এই বক্তব্য নয়, বঙ্গবন্ধু তার সাড়ে তিন বছরের সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্নে বারবার দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। চারপাশের দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে চিৎকার করেছেন। কারণ তিনি জানতেন, দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরতে না পারলে ‘সোনার বাংলা’ গড়া সম্ভব হবে না। জাতির পিতা তার জীবদ্দশায় পালিত শেষ স্বাধীনতা দিবসের বক্তব্য দেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। ১৯৭৫ সালে ২৬ মার্চের এই বক্তৃতায় দুর্নীতির স্বরূপ উন্মোচন করেন জাতির পিতা।
শুধু আর্থিক অনিয়মকারীরাই নয়, আদর্শচ্যুত মতলববাজদেরও দুর্নীতির সংজ্ঞায় এনেছিলেন বঙ্গবন্ধু। ওই ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ‘আজ কে দুর্নীতিবাজ? যে ফাঁকি দেয় সে দুর্নীতিবাজ। যে ঘুষ খায় সে দুর্নীতিবাজ। যে স্মাগলিং করে সে দুর্নীতিবাজ, যে ব্ল্যাক মার্কেটিং করে সে দুর্নীতিবাজ। যারা বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে তারাও দুর্নীতিবাজ। যারা বিদেশের কাছে দেশকে বিক্রি করে তারাও দুর্নীতিবাজ।
এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে। ... ঘরে ঘরে আপনাদের দুর্গ গড়তে হবে। সে দুর্গ গড়তে হবে দুর্নীতিবাজদের খতম করার জন্য। বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের দুঃখ মোচন করার জন্য। এই দুর্নীতিবাজদের যদি খতম করতে পারেন, তাহলে বাংলাদেশের মানুষের শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ দুঃখ চলে যাবে। এত চোরের চোর, এই চোর যে কোথা থেকে পয়দা হয়েছে, তা জানি না। পাকিস্তান সব নিয়ে গিয়েছে, কিন্তু এই চোরদের তারা নিয়ে গেলে বাঁচতাম।’
কে বলে বঙ্গবন্ধুর এই বক্তব্য পঁচাত্তরের? মুখে বলুন আর না বলুন-প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই এই বক্তব্যের সত্যতা প্রতিমুহূর্তে অনুভব করেছেন। শুধু জনগণ নয়, তিনিও এখন ‘চাটার গোষ্ঠীর’ যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ। শেখ হাসিনা ‘যারে যেখানে পাঠাচ্ছেন কেবল চুরি করছে’। সাম্প্রতিককালে আজিজ আহমেদ, বেনজীর আহমেদ, মালয়েশিয়ায় রিক্রুটিং সিন্ডিকেট থেকে প্রধানমন্ত্রীর চুনোপুঁটি ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের যেসব কেচ্ছা-কাহিনি বেরোচ্ছে, তাতে বঙ্গবন্ধুর মতো তার কন্যাকেও ইদানীং অসহায় মনে হচ্ছে। পার্থক্য শুধু এটুকু, বঙ্গবন্ধু তার রাগ, ক্ষোভ, অভিমান প্রকাশ্যে বলতে পারতেন। বঙ্গবন্ধু প্রকাশ্যে আর্তনাদ করতেন, শেখ হাসিনা নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। তিনি ‘নীলকণ্ঠী’। চারপাশের দুর্নীতিবাজদের অত্যাচার সহ্য করেন, যতক্ষণ না তারা সীমা লঙ্ঘন না করে।
সাবেক পুলিশপ্রধান বেনজীর আহমেদের কথাই ধরা যাক। যোগ্যতা, দক্ষতা এবং বিশ্বস্ততার বিবেচনায় বেনজীর তার চাকরি জীবনে সবকিছু পেয়েছেন। চাকরি জীবনের একটা বড় সময় ধরে মেধাবী কর্মকর্তা হিসেবে তার সুনাম ছিল। কিন্তু তিনি পদোন্নতির সিঁড়ি বেয়ে যত ওপরের দিকে উঠছেন, ততই বেপরোয়া এবং দুর্নীতিবাজ হয়ে উঠেছিলেন। দুর্নীতি দমন কমিশন এখন তার যে সম্পদের হিসাব প্রকাশ করছে, তা রীতিমতো ‘রত্নভান্ডার’। শীর্ষ পদে একজন ব্যক্তি যখন লোভে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন, তখন সরকার বা রাষ্ট্র কী করবে? শীর্ষ পদে গিয়ে লাগামহীন দুর্নীতি একজন ব্যক্তির একান্তই নিজস্ব সিদ্ধান্ত। তারা রাষ্ট্র এবং সরকারের জন্য ক্ষতিকর।
তবে এ কথা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই, সরকার বেনজীরের কথিত দুর্নীতির দায় এড়াতে পারে না। দেশে রিকশাওয়ালা, চায়ের দোকানদার পর্যন্ত সাবেক এই পুলিশপ্রধানের দুর্নীতির কেচ্ছা-কাহিনি জানত। তাহলে সরকার এই অপকর্মের বিন্দু-বিসর্গও জানত না, এটা হতে পারে না। সরকার কি বেনজীর আহমেদকে ভয় পেত? তিনি কি সরকারের চেয়েও ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছিলেন? নাকি সরকার জেনেশুনে এসব অন্যায় প্রশ্রয় দিয়েছে। সবাই নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখেছে। কদিন আগে সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বিস্মিত এবং হতবাক। বলছিলেন, ‘চুরি কমবেশি সবাই করে। কিন্তু এটা তো লুণ্ঠন! এতটা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি।’ এ রকম বক্তব্য অনেকের। তারা বলেছেন, বেনজীরের এই অধ্যায় তাদের অজানা ছিল।
আমি মনে করি, এটি সুশাসন এবং জবাবদিহির ব্যর্থতা। বেনজীর আহমেদকে পুলিশপ্রধান করে কি তাকে পুলিশ বাহিনীর জমিদারি বা ঠিকাদারি দেওয়া হয়েছিল? তিনি কি জবাবদিহির ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছিলেন? কেউ কেন তাকে চ্যালেঞ্জ জানায়নি। ক্যাসিনোবিরোধী অভিযানের সময় বেনজীর আহমেদের নাম এসেছিল। কিন্তু সেটিকে ধামাচাপা দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। একজন সরকারি কর্মকর্তা চাকরিতে থেকে কীভাবে বোট ক্লাবের হর্তাকর্তা হন, এ নিয়েও কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু সে প্রশ্ন আমলে নেওয়া হয়নি। সীমা লঙ্ঘনের সব সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর সবার ঘুম ভেঙেছে। এখানেও সন্দেহ। বেনজীর যখন বিদেশে সপরিবারে পালিয়ে গেলেন, তারপর শুরু হলো হৈচৈ? সরকারের ভেতর থেকেই কি কেউ তাকে আগাম তথ্য দিয়েছে? পালিয়ে যেতে সহযোগিতা করেছে? তার পরও দুদক এবং সরকারের এই অবস্থানকে আমি স্বাগত জানাই। এর ফলে আমাদের দুটি উপকার হলো।
প্রথমত, বেনজীরের বিরুদ্ধে এখনকার তৎপরতা সুস্পষ্টভাবে সবার জন্য একটি স্পষ্ট বার্তা। অন্যায় করলে একদিন না একদিন কাঠগড়ায় দাঁড়াতেই হবে-এই চিরন্তন সত্যটা সামনে এলো। বেনজীর একজন না। বেনজীর একটি ব্যক্তি না। বেনজীরের মতো বহু বিতর্কিত ব্যক্তি রাষ্ট্রযন্ত্রের নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে বসে আছেন বা ছিলেন। বেনজীররা রাষ্ট্রের জন্য দানব। তারা কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করতেন না। এ ঘটনা এসব দানবের জন্য একটা সতর্কবার্তা। বেনজীর আহমেদের যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে যে কোনো দুর্নীতিবাজের যে কোনো সময় একই পরিণতি হতে পারে। ‘ক্ষমতা’ জোয়ার-ভাটার মতো। ভাটার সময় কেউ পাশে থাকে না। যেমন বেনজীর, আজিজ, তুষার, লিকুর পাশে কেউ নেই। এর ফলে দুর্নীতির লাগাম কিছুটা হলেও টেনে রাখা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি। এই ঘটনার পর শীর্ষপদে দুর্নীতি করার আগে যে কেউ দশবার চিন্তা করবে।
দ্বিতীয়ত, জনগণের বিচার। যে কোনো বিচারের দুটি দিক আছে। একটি আইনি প্রক্রিয়ায় বিচার, যা দুদক এখন করছে। সাবেক পুলিশপ্রধানের অবৈধ সম্পদের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়েছে। অনুসন্ধানে যখন সম্পদের অস্বাভাবিক স্ফীতি লক্ষ করেছে, তখন কমিশন আদালতের আশ্রয় নিয়েছে। দুই দফায় বেনজীর এবং তার পরিবারের বিপুল সম্পদ জব্দ করার আবেদন করেছে। দুদক ৬ জুন সাবেক পুলিশপ্রধানকে তলব করেছে। ৯ জুন তলব করেছে স্ত্রী ও সন্তানদের। এভাবেই ধাপে ধাপে আইনি প্রক্রিয়া এগোবে। দুদক তদন্ত শেষে অভিযোগগুলো আদালতে জমা দেবে। চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ, যুক্তি-তর্ক, সাক্ষ্য-প্রমাণের পর বিচারক রায় দেবেন বেনজীর আহমেদ দোষী না নির্দোষ। এর আগে আইনের দৃষ্টিতে তাকে অপরাধী বলা যাবে না। কিন্তু আইনের এই প্রক্রিয়ার বাইরেও একটি বিচার আছে, তা হলো জনভাবনা, জনমত। যেটাকে আমরা বলি ‘পাবলিক ট্রায়াল’। যে কোনো একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের নাগরিক ওই ঘটনা সম্পর্কে তাদের নিজস্ব একটি মতামত গ্রহণ করে। জনগণের মধ্যে একটি সামষ্টিক অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে। আইনের প্রক্রিয়ার আগেই সিংহভাগ জনগোষ্ঠী কাউকে দোষী বা নির্দোষ হিসেবে রায় দেয়। বেনজীর আহমেদের ব্যাপারে জনরায় তার বিরুদ্ধে। সপ্তাহজুড়ে এ ঘটনায় জনগণের মধ্যে একটি বিজয়ী ভাব লক্ষণীয়। তারা মনে করে, বেনজীর আহমেদ দুর্নীতিবাজ। দুদকের অ্যাকশনে তারা খুশি। জনতার আদালতে বিচারের আগেই বেনজীর অপরাধী। আমি মনে করি, এ ধরনের মানুষের জন্য এটাই সবচেয়ে বড় শাস্তি। এই সামাজিক ঘৃণা দুর্নীতির বিরুদ্ধেও মানুষের সম্মিলিত কোরাস।
বেনজীর কি একা? তিনিই কি উচ্চপদে থাকা একমাত্র কর্মকর্তা, যার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ? না। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন স্তরে এ রকম অনেক বেনজীর আছেন। যাদের দুর্নীতির ফিরিস্তি দীর্ঘ। এসব ব্যক্তিকে সবাই চেনে, জানে। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, শুধু বেনজীরকে কেন আইনের আওতায় আনা হচ্ছে, অন্যরা কেন ধরাছোঁয়ার বাইরে? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ‘শূন্য সহিষ্ণুতা নীতি’ ঘোষণা করেছে। তাই ঘোষণার বাস্তবায়ন দেখতে চায় জনগণ। শুধু একটি ঘটনা নিয়ে হৈচৈ হলে তার পেছনে অন্য উদ্দেশ্য আছে বলে ধরে নিতে হবে। জনগণ শুধু এক বেনজীর আহমেদের দুর্নীতির তদন্ত চায় না, সব দুর্নীতিবাজের মুখোশ উন্মোচন চায়। ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের শাস্তি চায়, অর্থ পাচারকারীদের বিচার চায়। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ‘দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট।’
প্রধানমন্ত্রীর প্রভাবশালী উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানও একই রকম বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘অপরাধী যত প্রভাবশালী হোন, সরকারের সাপোর্ট পাবে না।’ বেনজীর আহমেদের ঘটনায় আশাবাদী হয়ে সাবেক সেনাপ্রধান আজিজ আহমেদের বিরুদ্ধেও তদন্ত দাবি করেছেন কয়েকজন আইনজীবী। তারা দুদকে এ ব্যাপারে চিঠিও দিয়েছেন। দুদকের চেয়ারম্যান বলেছেন, ‘দুর্নীতি দমন কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত বিষয় হলে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।’ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের জোরালো অবস্থান এখন নানাভাবে দৃশ্যমান।
গত বুধবার (২৯ মে) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দুজন কর্মকর্তার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে। এ দুজনের চুক্তি নবায়ন করা হয়েছিল টানা চতুর্থবার আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হওয়ার পর। চুক্তি নবায়নের মাত্র চার মাসের মাথায় তাদের চুক্তি বাতিল করা হলো। অনেকেই মনে করেন, এটাও অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থানের আরেকটি প্রকাশ। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়েও শুদ্ধি অভিযান হচ্ছে-এমন সংবাদে আমরা আন্দোলিত। কিন্তু আমরা ঘর পোড়া গরু। সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পাই। বিভিন্ন সময়ে নানা রকম দুর্নীতির বিরুদ্ধে হৈচৈ হয়েছে। তারপর সবকিছু থেমে গেছে। ক্যাসিনোকাণ্ডের সময় সারা দেশে তোলপাড় হলো। আওয়ামী লীগের অঙ্গ এবং সহযোগী সংগঠনের অনেক নেতা পদ হারালেন। অনেকে গ্রেপ্তার হলেন। গণমাধ্যমে কয়েকদিন তাদের অবৈধ বিপুল সম্পদের ফিরিস্তি প্রকাশিত হলো। তারপর সব সুনসান। সে সময় যারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাদের কারও সাজা হয়েছে? এ নিয়ে কেউ এখন কথা বলে না।
বেসিক ব্যাংক কেলেঙ্কারি, বিসমিল্লাহ গ্রুপের ব্যাংক লুণ্ঠনের পর ব্যাংক লুটেরাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো। কিন্তু কী হয়েছে তার পরিণতি? আমরা কি আবদুল হাই বাচ্চুর কিছু করতে পেরেছি? খেলাপি ঋণ এখন এভারেস্টের চেয়েও উঁচু। কারও কিছু হয়নি।
সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠানো নিয়ে যে কেলেঙ্কারি হলো, এর সঙ্গে জড়িত সরকারের ঘনিষ্ঠরা। যাদের কারণে ৩০ হাজার মানুষ পথে বসল, তাদের কি বিচার হবে? অর্থ পাচার নিয়ে কথা তো কম হলো না। কিন্তু একজন অর্থ পাচারকারীকেও এখনো আইনের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। দুই বছর আগে সরকারি কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সম্পদের হিসাব দেওয়ার আইনটি বাস্তবায়নের ঘোষণা দেওয়া হলো। কিন্তু আমলারা এতই ক্ষমতাবান, ১৯৭৯ সালের আইনটি তারা বন্দি করে রেখেছেন। এই আইন যদি কার্যকর থাকত, তাহলে কি বেনজীর এত বেপরোয়া হতেন? দুর্নীতিবাজদের এক সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে। আগে রাজনীতিবিদরা কিছু দুর্নীতিবাজ পুষতেন। নির্বাচন, রাজনৈতিক খরচ মেটানোর জন্য। এখন দুর্নীতিবাজরা রাজনীতিবিদ পোষেণ, তাদের অবৈধ সম্পদ পাহারা দেওয়ার জন্য। রাজনীতিবিদদের কেউ কেউ এখন দুর্নীতিবাজদের পালিত, অনুগত। তাই বেনজীর, আজিজ নাটকের সমাপ্তি কোথায়, তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। কিছুদিন ঢাকঢোল পিটিয়ে আমরা আবার অন্য এক ইস্যুতে ঝাঁপ দেব? দুর্নীতিবাজরা বুক ফুলিয়ে আবার ঘুরে বেড়াবে?
আমরা যেন দুর্নীতির এক দুষ্টচক্রের জালে বন্দি। দুর্নীতির এক বীভৎস প্রতিযোগিতা চলছে দেশজুড়ে। বঙ্গবন্ধুর মতোই প্রধানমন্ত্রী যাকে যে দায়িত্বে দিচ্ছেন, তিনিই যেন দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে উঠেছেন। ‘চাটার গোষ্ঠীর যন্ত্রণায় মানুষ’ শেষ হয়ে যাচ্ছে। কার ওপর আস্থা রাখবেন শেখ হাসিনা?
লেখক: নির্বাহী পরিচালক, পরিপ্রেক্ষিত
ইমেইল: poriprekkhit@yahoo.com