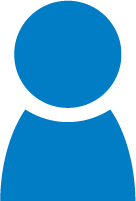রাজনৈতিক দলে গণতন্ত্র চর্চা হয় কিনা তা নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক চলছে। কোন দল কিভাবে চলে, দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা হয় কিনা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে কিনা, নেতা নির্বাচন কিভাবে হয় অনেক আলোচনাই চলে। আমি আমার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কিভাবে সাংগঠনিক কার্যক্রম চলে সেটা নিয়ে আলোচনা করব।
২০০২ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় নেতাদের অনেকের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও কাউন্সিল করি। ২০০১ সালের নির্বাচনের পর বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট ক্ষমতা দখল করে। নির্বাচনের পর থেকেই আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী, সমর্থক ভোটারদের ওপর অমানবিক অত্যাচার নির্যাতন শুরু করে।
আমি যে সমস্ত এলাকায় নির্যাতন হয়েছি সে সমস্ত এলাকায় সফর করি। অনেক বাধা আসে চারদলীয় জোট সরকারের পক্ষ থেকে। আমার দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগীতায় চারদলীয় জোটের সন্ত্রাসী বাহিনী আক্রমন চালাতে থাকে। এ অবস্থায় দলকে সংগঠিত করা একান্তভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়ে।
আমি যখন সরকারে ছিলাম তখন প্রত্যেক জেলা তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের নিয়ে সভা করেছি। এক একদিন এক এক জেলার উপজেলা, ইউনিয়ন ও সহযোগী সংগঠনের নেতাদের নিয়ে মতবিনিময় করি। কেন্দ্রীয় কমিটি, সভাপতিম-লী, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত মতবিনিময়ের সভা করেছি। বিভাগীয় সম্মেলন করেছি। এই বিভাগীয় সম্মেলনে ইউনিয়ন, উপজেলা নেতারা বক্তব্য রেখেছে।
২০০১ সালের নির্বাচনের পর যে নির্যাতন চলছিল তার প্রতিবাদে একটি আন্তর্জাতিক কনভেনশন করা হয়। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ কনভেনশন উপলক্ষে সমগ্র দেশ থেকে নেতৃবৃন্দ ঢাকায় আসে ও অংশগ্রহণ করে। নির্যাতিতদের তথ্য সরবরাহ করে ও নির্যাতিতদের নিয়ে আসে।
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। কানাডা থেকে মানবাধিকার কর্মী মি: স্লোন, নেদারল্যান্ডের সাবেক মন্ত্রী ... যোগ দেন। পাকিস্তান থেকে আসমা জাহাঙ্গীরের আসার কথা ছিল কিন্তু বাংলাদেশ তাঁকে ভিসা দেয় নাই বলে আসতে পারেন নাই।
২০০২ সালের ২২ ও ২৩ অক্টোবর আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র দেশ থেকে কাউন্সিলার ও ডেলিগেট পাঁচ হাজার এবং সেই সাথে নেতাকর্মী মিলে চল্লিশ হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকে। প্রত্যেক জেলার পক্ষ থেকে কাউন্সিলার ও ডেলিগেটরা বক্তব্য রাখেন ও লিখিত প্রতিবেদন পেশ করেন। অত্যন্ত বৈরী পরিবেশ ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সফল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী সম্মেলনের পূর্বে কতগুলো সাব কমিটি গঠন করা হয়। যেমন ১. গঠনতন্ত্র সাব কমিটি, ২. ঘোষণাপত্র সাব কমিটি, ৩. অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি, ৪. সম্মেলন পরিচালনা কমিটি, ৫. অভ্যর্থনা কমিটি, ৬. আপ্যায়ন কমিটি, ৭. অর্থ কমিটি, ৮. মঞ্চ কমিটি, ৯. প্রচার ও প্রকাশনা, ১০. নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি, ১১. সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটি। কমিটিগুলো স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করে। তিন সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। নির্বাচন পরিচালনা, নীতিমালা গ্রহণ ও সম্মেলনে নির্বাচনের দায়িত্ব এই কমিশনের। সমঝোতা না হলে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন হয়। এই নিয়মে আওয়ামী লীগের সম্মেলন কেন্দ্র থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত নির্বাচন হয়ে থাকে।
গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র এবং অর্থনৈতিক নীতিমালা কমিটির সুপারিশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির কাছে পেশ করা হয়। এর পূর্বে প্রত্যেক জেলা কমিটির কাছ থেকেও মতামত সংগ্রহ করা হয়, তারই আলোকে কমিটি খসড়া প্রস্তাব কার্যকরী সংসদের কাছে পাঠায়। সেখানে বিস্তারিত আলাপ করে প্রস্তাব প্রস্তুত করা হয় কাউন্সিলের জন্য। যেকোনো সংশোধন কাউন্সিল পাস করবে। কেন্দ্রীয় সংসদ সংশোধনীর সুপারিশগুলো প্রস্তুত করবে। সেখানে কাউন্সিলারদের আপত্তি থাকলে তা আমলে নেওয়া হয়ে থাকে। সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী কাউন্সিলে আয় ও ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে হবে এবং বাজেট পাস করতে হবে। কেন্দ্রীয় সংসদ ও জাতীয় কমিটি বাজেট অনুমোদন করলে কাউন্সিলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
এই সকল নিয়ম যথাযথভাবে মানা হয়। গঠনতন্ত্র মেনেই সংগঠন পরিচালনা করা হয়। সদস্য সংগ্রহ অভিযান চালানো হয়।
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একটা উপদেষ্টাম-লী আছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার বিশিষ্টজনদের সম্মতি সাপেক্ষে উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য করা হয়। উপদেষ্টা পরিষদ নিয়মিত বৈঠক করে থাকে। সভানেত্রীর সভাপতিত্বে সাধারণত বছরে এক বা দুবার সভা হয়। ২০০২ সালের পর ছয়টা সভা করা হয়েছে। এসব সভায় উপদেষ্টাম-লীর সদস্যদের নিয়ে তিনটি সেল গঠন করা হয়। যথা
১. রাজনৈতিক সেল,
২. অর্থনৈতিক সেল ও
৩. সামাজিক সেল।
উপদেষ্টাম-লী থেকে একজন চেয়ারম্যান বাকি সবাই সদস্য। ২০০২ সালের কাউন্সিলের পর যে তিনটি সেল গঠন করি তার চেয়ারম্যান ছিলেন রাজনৈতিক সেল সামসুল হুদা হারুন (প্রয়াত), অর্থনৈতিক সেলÑ শাহ এ এম এস কিবরিয়া (নিহত) এবং সামাজিক সেল এ এস এইচ কে সাদেক (প্রয়াত)।
এসব সেলের কাজ হল সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করা, দলের করণীয় সম্পর্কে উপদেশ দান ও ভবিষ্যাৎ কর্মসূচী কি হবে, রাষ্ট্রে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও দলকে তা সরবরাহ করে থাকেন। এই সেলগুলোর মিটিং নিয়মিত করা হয়। লিখিত মন্তব্য, সুপারিশ দলকে দিয়ে থাকে।
কুড়িটা সাব কমিটি আছে। উপদেষ্টাম-লীর সদস্যদের মধ্য থেকে চেয়ারপারসন ও কো-চেয়ারপারনস নির্বাচন করা হয়। কার্যকরী সংসদের বিষয়ভিত্তিক সম্পাদক, সদস্যসচিব হিসেবে কাজ করেন। পার্লামেন্টারি পার্টির সদস্য, যিনি জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য তিনি সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য হবেন পদাধিকার বলে। যেমন জাতীয় সংসদের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির যে সদস্য থাকবেন তিনি দলের এই সাব কমিটির সদস্য থাকবেন। এর ফলে দলের সাথে সংসদের গৃহীত কার্যক্রম ও দলের নীতিমালার আদান প্রদান সহজ হয়। দেশ ও জাতির উন্নয়নের কাজ দ্রুত করা যায়। এতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকে। কুড়িটা সাব কমিটি হচ্ছে:
১. অর্থ ও পরিকল্পনা,
২. আন্তর্জাতিক,
৩. আইন বিষয়ক,
৪. কৃষি ও সমবায়,
৫. তথ্য ও গবেষণা,
৬. ত্রাণ ও সামাজকল্যাণ,
৭. দপ্তর,
৮. ধর্ম,
৯. প্রচার ও প্রকাশনা,
১০. বন ও পরিবেশ,
১১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি,
১২. মহিলা বিষয়ক,
১৩. মুক্তিযুদ্ধ,
১৪. যুব ও ক্রীড়া,
১৫. শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক,
১৬. শিল্প ও বাণিজ্য,
১৭. শ্রম ও জনশক্তি,
১৮. স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা,
১৯. সংস্কৃতি,
২০. স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচন বিষয়ক।
২০০২ সালের কাউন্সিলের পর ২০০৬ পর্যন্ত যে সভাগুলো হয়েছে:
প্রেসিডিয়াম সভা-৫৫, কার্যকরী সংসদের নিয়মিত সাধারণ সভা-১৭, কার্যকরী সংসদের জরুরী সভা-৫১, সম্পাদকম-লীর সভা-১৭, মোট=১৪০।
উপদেষ্টাম-লী, তিনটি সেল ও সাব কমিটিগুলোর মিটিং, সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক অগণিত হয়েছে। দেশের যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বা উদ্ভূত যেকোনো পরিস্থিতি সভা করে সুপারিশ কেন্দ্রকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে এবং করেছে। সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে নিয়মিত বৈঠক হয়েছে, মতবিনিময় হয়েছে।
সমমনা রাজনৈতিক দল বিশেষ করে ১৪ দলের সাথে নিয়মিত বৈঠক হয়েছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে। কোন কোন সময় ইস্যুভিত্তিক বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং তাদের সুনির্দ্দিষ্ট এজেন্ডা দেওয়া হয়েছে। যেমন কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিল তখন কমিটি করে দুর্যোগ মোকাবিলার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
২০০৫ সালের ৩০ ও ৩১ আগস্ট চারদলীয় জোট সরকারের অত্যাচার, নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে জাতীয় কনভেনশন করা হয়েছে। এই কনভেনশন চলার সময় নেতৃবৃন্দ তাদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পেয়েছে।
আমি আমার দলের মনোনয়ন বিষয়ে ফিরে আসি।
২০০১ সালের নির্বাচনের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সকল তথ্য সংগ্রহ করে নেই। এরূপ একজন সাবেক ভিসি ড. আলাউদ্দীন আহমেদ সংসদ সদস্যকে দায়িত্ব দেই। এর মধ্যে সকল ভোট কেন্দ্রের ফলাফল ডাটাবেজ করে রাখি। সেখান থেকে ৩০% ভাগের কম ভোট কোন কোন কেন্দ্রে আমরা পেয়েছি তা আলাদা করি। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনের সকল ভোট কেন্দ্রের ফলাফল থেকে ৩০% ভাগের কম ভোটপ্রাপ্ত কেন্দ্রের নামগুলো সংগ্রহ করি। এছাড়া কোন আসন, ইউনিয়নে কেন্দ্রে কি পরিমান ভোট বেড়েছে, কমেছে ইত্যাদি তথ্যও সংগ্রহ করে প্রত্যেক আসনের আলাদা ফাইল তৈরি করা হয়। ড. আলাউদ্দিন, কম্পিউটার পারদর্শী কয়েকজন কর্মী নিয়ে কাজ করেন।
এই ভোটারদের মধ্যে নারী ভোটার, পুরুষ ভোটার, প্রত্যেক উপজেলা ও ইউনিয়নের নামসহ সকল তথ্য সংগ্রহ করি। ২০০১ সালের পর থেকে প্রতি ছয় মাস পর পর সমগ্র বাংলাদেশে সার্ভে করাই, তথ্য সংগ্রহ করি। এই তথ্য সংগ্রহের কাজ এককভাবে কাউকে দেই নাই। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনাসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দিয়ে টিম করে দেই। শিক্ষকরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিমে ভাগ করে দেন, যাঁরা দিন রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তারপর তারা ইউনিয়ন, ওয়ার্ড, গ্রাম পর্যন্ত সফর করেন এবং তথ্য সংগ্রহ করেন। শিক্ষকদের এই একনিষ্ঠ, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সহযোগিতার জন্য আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তাদের তথ্য সংগ্রহ অব্যাহত থাকে।
আর একটা গ্রুপ করা হয় সরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারা যাঁরা অবসরপ্রাপ্ত। বিভিন্ন সময় তাদের পূর্বের কর্মক্ষেত্র যার যেখানে ছিল সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আনেন। প্রাইভেট কোম্পানী-যারা তথ্য সংগ্রহ করার পেশায় নিয়োজিত এ ধরনের দুটো গ্রুপ একটা দেশি ও অন্যটা বিদেশি-এদের দ্বারাও তথ্য সংগ্রহ করাই। আমেরিকার একটা গ্রুপ তথ্য সংগ্রহ করেছিল সিট হিসেবে এলাকা ভিত্তিক। কোন দলের কোন সিটে সমর্থক বেশি, ভোটার বেশি ইত্যাদি সে তথ্যও সংগ্রহ করি।
কতকগুলো ফরম তৈরি করা হয়। কমপক্ষে পাঁচ জন প্রার্থীর নাম, দশটা প্রার্থী সম্পর্কে। মোট নম্বর ১০০ প্রত্যেক প্রশ্নের সাথে নম্বর নির্দ্দিষ্ট করা হয়। এভাবে কোন প্রার্থী কত নম্বর পেল তা তালিকা করা হয়।
দলের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদকের নামে একটা চিঠি জেলা, উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত পাঠানো হয়। উপজেলাকে বলে দেওয়া হয় ইউনিয়ন থেকে মতামত সংগ্রহ করতে। তাদেরকে কতকগুলো প্রশ্ন পাঠানো হয় প্রশ্নগুলোরও সার্বিক অবস্থা বিশেষ করে যোগ্য প্রার্থীর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সকল তথ্য সংগ্রহ করে প্রথমেই আমি যে তিনশত প্রার্থীকে ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন দিয়েছিলাম তাদের সাথে সভা করি। প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ছোট ছোট গ্রুপ করে বসি। প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের ভোটের পরিমাণ ও প্রতিদ্বন্দীর সাথে কম বা বেশি ব্যবধান এবং ৩০% ভাগের কম ভোট কোন কোন কেন্দ্রে পেয়েছেন তার তালিকাটা প্রার্থীকে সরবরাহ করি আলোচনার সুবিধার জন্য।
এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে প্রেসিডিয়াম সদস্য, সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত থাকতে পারতেন। তাঁরা কখনো থাকতেন কখনো থাকতেন না। সংশ্লিষ্ট এলাকার কেন্দ্রীয় নেতা এবং সাংগঠনিক সম্পাদককে উপস্থিত থাকতে হতো। তাঁরা সাক্ষাৎকার স্থানে অথবা পাশের কামরায় তাদের সুবিধমত থাকতেন। কোনো প্রশ্ন দেখা দিলে তথ্য সরবরাহ করে সাহায্য করতেন। প্রায় তিন থেকে চার মাস সময় লাগে এই সাক্ষাৎকারের। প্রতিটি প্রতিবেদন দিয়েও সাহায্য করেন। যা পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হয়। পরবর্তী বৈঠক শুরু করি প্রতিটি জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশনের নেতাদের সাথে।
প্রতিদিন সকাল ৯টায় বৈঠক শুরু হতো কয়েকটা এলাকা নিয়ে। জেলা ও উপজেলার সংখ্যা হিসেবে।
২০০৬ সালের জুন মাসের ৩ তারিখ থেকে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত ধানমন্ডি ৩/এ সড়কের অফিসে সভা হয় ৪৮০ উপজেলা, পৌরসভাগুলো ও ৭৩টি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে এ বৈঠক শুরু করি। যাতে সকলে মন খুলে কথা বলতে পারে তার জন্য ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ করে নেওয়া হয়। সভাপতিম-লীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ, সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত থাকতেন। তাঁদের সময় ও সুযোগমতো যে যখন পারতেন থাকতেন। নিজ এলাকা হলে তাঁদের আগ্রহ বেশি থাকত। তবে অনেকে নিয়মিত থেকে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। দিনের পর দিন এ বৈঠক চলে।
দশটা প্রশ্ন, কমপক্ষে পাঁচ জন প্রার্থীর নাম এবং কোন প্রার্থীকে কত নম্বর দিবেন তা উল্লেখ করে দশটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হতো। শুরুতেই নেতাদের হাতে ১০০ নম্বরের প্রশ্নপত্র দেওয়া হতো যা তারা পূরণ করে জমা দিতেন। এক ঘন্টা সময় ধরা হতো। কমপক্ষে পাঁচ জন প্রার্থী সম্পর্কে তথ্য ও নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এরপর পর্যায়ক্রমে সকলের বক্তব্য দেবার সুযোগ দেওয়া হতো এবং সকলেই মনখুলে বক্তব্য দিতেন। আমরা তা নোট করে নিতাম। চা, নাস্তা, দুপুরের খাবার বিকেলের চায়ের ব্যবস্থা থাকত।
সবাই মন খুলে সংগঠন, নির্বাচন, প্রার্থী, দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থা সকল বিষয়েই আলোচনা করেছেন। এই সকল তথ্য সংগ্রহ করে কোন কোন এলাকায় কোন কোন প্রার্থী কত নম্বর পেল ইত্যাদি নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করা হয়।
একটা বিষয় খুবই লক্ষণীয় ছিল আমাদের তৃণমূল পর্যায়ের নেতাদের প্রার্থী সম্পর্কে মূল্যায়ন যা পেয়েছিলাম আর বিভিন্ন পর্যায়ে সার্ভে করে যে রিপোর্ট পেয়েছি তা ৯০% ভাগের ওপর মিল ছিল।
সকল প্রতিবেদন তথ্য দ্বারা রিপোর্ট তৈরি করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টরি বোর্ডের নিকট উপস্থাপন করি। সাথে সাথে সকল রিপোর্টগুলোও হাতের কাছে রাখি। সকলের হাতেই একটা করে খাতা দিয়ে দেই যাতে বোর্ড সদস্যরা তাদের মতামত লিপিবদ্ধ করতে পারেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি বোর্ড বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মনোনয়ন প্রথমে ঠিক করে।
আগ্রহী প্রার্থীদের কাছে নির্বাচনী ফরম বিক্রি করা হয়। ফরম বিক্রি করা হয়। ফরম ক্রয় ও জমা দেওয়া হয়। প্রার্থী যাঁরা হতে চান তাঁদের ফরম কিনতে হয় টাকা জমা দিয়ে এবং রশিদ নিতে হয়। এভাবে প্রথমে নিজেদের দলের মনোনয়ন নির্দ্দিষ্ট করি।
১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ এর নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে তিনশত আসনকে চারভাগে ভাগ করি।
এ, বি, সি ও ডি। এই চার ভাগে ভাগ করে রাখি এ কারণে যে নির্বাচনে ঐক্য করতে হলে কোন সিট কি অবস্থায় আছে তা জানতে সুবিধা হবে।
২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ ঐক্য, মহাজোট ঐক্যে সিট ভাগের সময় এই তথ্যগুলো কাজে আসবে। এই হিসাব বিবেচনায় রেখেই সিট ভাগ করা হয়েছিল। যে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড দলের মনোনয়ন ঠিক করে সেখানে মনোনয়ন বাণিজ্যের সুযোগ কোথায় ছিল? পার্লামেন্টারি বোর্ড এগারটা (১১) সভা করে। তারপর নিজ দলের আসনে প্রার্থী ঠিক করে। এরপর ঐক্য, মহাজোট ঐক্য করা হয়।
১৪ দলের থেকে রাশেদ খান মেনন, অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মদ, হাসানুল হক ইনু, নুরুল ইসলাম, দিলীপ বড়–য়াসহ সকল নেতার নিজ নিজ দলের প্রার্থীদের তালিকা সরবরাহ করেন।
জাতীয় পার্টি ও এলডিপির কর্নেল অলির পক্ষেও তালিকা দেওয়া হয়। ঐক্যের সিট বন্টন জলিল সাহেবের বাসায় বসে করা হয়। সেখানে সকল তথ্যসহ ড. আলাউদ্দীনের টিমও সহযোগিতা করার জন্য উপস্থিত থাকতেন। শরীক দলের প্রতিনিধিরা মিলে মহাজোটের নমিনেশন ঠিক করে দেয়। এভাবে মহাজোটের নির্বাচনী প্রস্তুতি নেওয়া হয়। ১/১১ পূর্বে যখন নমিনেশন ঠিক করা হয় তখন অবশ্য ড. কামাল হোসেন ও বদরুদ্দোজা চৌধুরীর দলও এই মহাঐক্যজোটে নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা দেয়। তবে ২০০৮ এর নির্বাচনের ঐক্যে আর তাঁরা ছিলেন না।
প্রতিটি সভায় বক্তাদের বক্তব্যেও নোট নেয়া হতো। আমি নিজের নোট নিয়ে থাকি। সবসময়ে দলের একজন সমস্যা দ্বারা মিনিটস লেখা হয়। প্রদত্ত প্রতিবেদন, প্রশ্নের উত্তর থেকে প্রাপ্ত প্রার্থীর নাম ও প্রাপ্ত নম্বর নির্বাচনী এলাকা অনুযায়ী খাতায় লেখা হয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডেও সকল তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে যা সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক হয়। দলের কার্যকরী সংসদসহ সকল সভায় পূর্ব সভার মিনিটস অসুমোদন করাতে হয়। কোনো সংশোধন থাকলে তা উত্থাপন করা এবং সে বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দলটির কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে আর কোন কোন অরাজনৈতিক দল এত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হয় কিনা তা জানতে ইচ্ছা করে।
কারাগার, ঢাকা
তারিখ : ৭ জুন ২০০৮
বাংলা ইনসাইডার