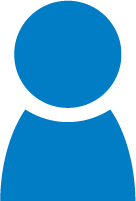বাইগার নদীর তীর ঘেঁষে ছবির মতো সাজানো সুন্দর একটি গ্রাম। সে গ্রামটির নাম টুঙ্গীপাড়া। বাইগার নদী এঁকে-বেঁকে গিয়ে মিশেছে মধুমতী নদীতে। এই মধুমতী নদীর অসংখ্য শাখা নদীর একটি নদী বাইগার নদী। নদীর দুপাশে তাল,তমাল, হিজল গাছের সবুজ সমারোহ। ভাটিয়ালি গানের সুর ভেসে আসে হালধরা মাঝির কণ্ঠ থেকে, পাখির গান আর নদীর কলকল ধ্বনি এক অপূর্ব মনোরম পরিবেশ গড়ে তোলে ।
প্রায় দু`শ বছর পূর্বে মধুমতী নদী এই গ্রাম ঘেঁষে বয়ে যেত। এই নদীর তীর ঘেঁষেই গড়ে উঠেছিল জনবসতি। প্রাকৃতিক আমোঘ নিয়মে ধীরে ধীরে নদীটি দূরে সরে যায়। চর জেগে গড়ে ওঠে আরও অনেক গ্রাম। সেই দু`শ বছর আগে ইসলাম ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নিয়েই আমাদের পূর্ব-পুরুষরা এসে এই নদীবিধৌত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সুষমামণ্ডিত ছোট্ট গ্রামটিতে তাদের বসতি গড়ে তোলেন । এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে। অনাবাদী জমিজমা চাষবাস শুরু করেন এবং গ্রামের বসবাসকারী কৃষকদের নিয়ে একটা আত্মনির্ভরশীল গ্রাম হিসেবেই এই গ্রামটিকে বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রামরূপে গড়ে তোলেন। যাতায়াত ব্যবস্থা প্রথমে শুধু নৌকাই ছিল একমাত্র ভরসা। পরে গোপালগঞ্জ থানা স্টিমার ঘাট হিসেবে গড়ে ওঠে। আমাদের পূর্ব-পুরুষরা টুঙ্গীপাড়া গ্রামে জমি-জমা ক্রয় করে বসতির জন্য কলকাতা থেকে কারিগর ও মিস্ত্রি এনে দালান বাড়ি তৈরি করেন। যা সমাপ্ত হয় ১৮৫৪ সালে। এখনও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই দালানের ধ্বংসাবশেষ। ১৯৭১ সালে যে দুটো দালানে বসতি ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আগুন দিয়ে সে দুটোই জ্বালিয়ে দেয়। এই দালান কোঠার বসবাস শুরু হবার পর ধীরে ধীরে বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে আর আশপাশে বসতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এই দালানেরই উত্তর-পূর্ব কোণে টিনের চৌচালা ঘর তোলেন আমার দাদার বাবা শেখ আবদুল হামিদ। আমার দাদা শেখ লুৎফর রহমান এই বাড়িতেই সংসার গড়ে তোলেন। আর এখানেই জন্ম নেন আমার আব্বা, ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। আমার আব্বার নানা শেখ আবদুল মজিদ আমার আব্বার আকিকার সময় নাম রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান। আমার দাদীর দুই কন্যা সন্তানের পর প্রথম পুত্র সন্তান। আমার আব্বা, আর তাই আমার দাদীর বাবা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দাদীকে দান করেন এবং নাম রাখার সময় বলে যান, “মা সায়রা, তোর ছেলের নাম এমন রাখলাম যে নাম জগৎ জোড়া খ্যাত হবে ।”
আমার আব্বার শৈশব কেটেছিল টুঙ্গীপাড়ার নদীর পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, মেঠো পথের ধুলোবালি মেখে। বর্ষার কাদাপানিতে ভিজে। বাবুই পাখি বাসা কেমন করে গড়ে তোলে। মাছরাঙা কিভাবে ডুব দিয়ে মাছ ধরে। কোথায় দোয়েল পাখির বাসা। দোয়েল পাখির সুমধুর সুর আমার আব্বাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করত। আর তাই গ্রামের ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে করে মাঠে-ঘাটে ঘুরে প্রকৃতির সাথে মিশে বেড়াতে তাঁর ভালো লাগত । ছোট্ট শালিক পাখির ছানা, ময়না পাখির ছানা ধরে তাদের কথা বলা ও শিস দেওয়া শেখাতেন। বানর ও কুকুর পুষতেন, তারা তাঁর কথামতো যা বলতেন তাই করত। আবার এগুলো দেখাশোনার ভার দিতেন ছোট বোন হেলেনের ওপর। এই পোষা পাখি, জীবজন্তুর প্রতি এতটুকু অবহেলা তিনি সইতে পারতেন না। মাঝে মাঝে এ জন্য ছোট বোনকে বকাও খেতে হতো। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ঘেঁষে একটা সরু খাল চলে গেছে, যে খাল মধুমতী ও বাইগার নদীর সংযোগ রক্ষা করে। এই খালের পাড়েই ছিল বড় কাছারী ঘর। আর এই কাছারী ঘরের পাশে মাস্টার, পণ্ডিত ও মৌলভী সাহেবদের থাকার ঘর ছিল। এরা গৃহশিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাঁদের কাছে আমার আব্বা আরবি, বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্ক শিখতেন।
আমাদের পূর্ব পুরুষদেরই গড়ে তোলা গিমাডাঙ্গা টুঙ্গীপাড়া স্কুল। তখন ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাড়ি থেকে প্রায় সোঁয়া কিলোমিটার দূর। আমার আব্বা এই স্কুলেই প্রথম লেখাপড়া করেন। একবার বর্ষাকালে নৌকা করে স্কুল থেকে ফেরার সময় নৌকাডুবি হয়ে যায়। আমার আব্বা খালের পানিতে পড়ে যান। এরপর আমার দাদী তাঁকে আর ঐ স্কুলে যেতে দেন নি। আর একরত্তি ছেলে, চোখের মণি, গোটা বংশের আদরের দুলাল, তার এতটুকু কষ্ট যেন সকলেরই কষ্ট! সেই স্কুল থেকে নিয়ে গিয়ে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে ভর্তি করে দেন। গোপালগঞ্জ আমার দাদার কর্মস্থল ছিল। সেই থেকে গোপালগঞ্জেই তিনি পড়ালেখা করতে শুরু করেন। মাঝখানে একবার দাদা মাদারীপুর বদলি হন। তখন কিছুদিনের জন্য মাদারীপুরেও আব্বা পড়ালেখা করেন। পরে গোপালগঞ্জেই তাঁর তার কৈশোর বেলা কাটে।
আমার আব্বার শরীর ছিল বেশ রোগা। তাই আমার দাদী সব সময়ই ব্যস্ত থাকতেন কিভাবে তাঁর খোকার শরীর ভালো করা যায়। আদর করে দাদা-দাদীও খোকা বলেই ডাকতেন। আর ভাইবোন গ্রামবাসীদের কাছে ছিলেন `মিয়া ভাই` বলে পরিচিত। গ্রামের সহজ সরল মানুষদের সঙ্গে অত্যন্ত সহজভাবে তিনি মিশতেন। আমার দাদী সব সময় ব্যস্ত থাকতেন খোকার শরীর সুস্থ করে তুলতে। তাই দুধ, ছানা, মাখন ঘরেই তৈরি হতো। বাগানের ফল, নদীর তাজা মাছ সব সময় খোকার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত থাকত। কিন্তু আমার আব্বা ছোট্ট বেলা থেকেই ছিপছিপে পাতলা ছিলেন, তাই দাদীর আফসোসেরও সীমা ছিল না যে কেন তার খোকা একটু হৃষ্টপুষ্ট নাদুস-নুদুস হয় না। খাবার বেলায় খুব সাধারণ ভাত, মাছের ঝোল, সবজিই তিনি পছন্দ করতেন। খাবার শেষে দুধ-ভাত-কলা ও গুড় খুব পছন্দ করতেন। আমার চার ফুফু ও এক চাচা ছিলেন। এই চার বোনের মধ্যে দুই বোন বড় ছিলেন। ছোট্ট ভাইটির যাতে কোনো কষ্ট না হয় এজন্য সদা সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন বড় দুই বোন। বাকিরা ছোট্ট কিন্তু দাদা-দাদীর কাছে খোকার আদর ছিল সীমাহীন। আমাদের বাড়িতে আশ্রিতের সংখ্যাও ছিল প্রচুর । আমার দাদার বা দাদীর বোনদের ছেলেমেয়ে বিশেষ করে যারা পিতৃহারা-মাতৃহারা তাদেরকে দাদা-দাদী নিজেদের কাছে এনেই মানুষ করতেন। আর তাই প্রায় সতেরো আঠারো জন ছেলেমেয়ে একই সঙ্গে বড় হয়ে উঠে।
আব্বার যখন দশ বছর বয়স তখন তাঁর বিয়ে হয় । আমার মায়ের বয়স ছিল মাত্র তিন বছর । আমার মা পিতৃহারা হবার পর তাঁর দাদা এই বিয়ে দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি মা ও খালার নামে লিখে দেন । আমার খালা মায়ের থেকে তিন চার বছরের বড়। আত্মীয়ের মধ্যেই দুই বোনকে বিয়ে দেন এবং আমার দাদাকে (গার্জিয়ান) মুরুব্বি করে দেন। আমার মার যখন ছয়-সাত বছর বয়স তখন তাঁর মা মারা যান এবং তখন আমার দাদী কোলে তুলে নেন আমার মাকে । আর সেই থেকে একই সঙ্গে সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মানুষ হন।
আমার আব্বার লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতি দারুণ ঝোঁক ছিল। বিশেষ করে ফুটবল খেলতে খুব পছন্দ করতেন। মধুমতী নদী পার হয়ে চিতলমারী ও মোল্লারহাট যেতেন খেলতে । গোপালগঞ্জে স্কুলের টিম ছিল। এদিকে আমার দাদাও খেলতে পছন্দ করতেন । আব্বা যখন খেলতেন তখন দাদাও মাঝে মাঝে খেলা দেখতে যেতেন। দাদা আমাদের কাছে গল্প করতেন যে, `তোমার আব্বা এত রোগা ছিল যে বলে জোরে লাখি মেরে মাঠে গড়িয়ে পড়ত।` আব্বা যদি ধারে কাছে থাকতেন তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করতেন। আমরা তখন সত্যিই খুব মজা পেতাম । এর পেছনে মজার ঘটনা হলো মাঝে মাঝে আব্বার টিম ও দাদার টিমের মধ্যেও খেলা হতো। এখনও আমি যখন ঐ সমস্ত এলাকায় যাই, অনেক বয়স্ক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয় যারা আব্বার ছোটবেলার কথা বলেন। আমাদের বাড়িতে এই খেলার অনেক ফটো ও কাগজ ছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। ফলে সব শেষ হয়ে যায়।
তিনি ছোটবেলা থেকে অত্যন্ত হৃদয়বান ছিলেন। তখনকার দিনে ছেলেদের পড়াশোনার তেমন সুযোগ ছিল না। অনেকে বিভিন্ন বাড়িতে জায়গির থেকে পড়াশোনা করত। চার পাঁচ মাইল পথ হেঁটে স্কুলে আসতে হতো। সকালে ভাত খেয়ে স্কুলে আসত । আর সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় অনেকদূর হেঁটে তাদের ফিরতে হতো । যেহেতু আমাদের বাড়িটা ছিল ব্যাংকপাড়ায় আব্বা তাদেরকে বাড়িতে নিয়ে আসতেন। স্কুল থেকে ফিরে দুধভাত খাবার অভ্যাস ছিল এবং সকলকে নিয়েই তিনি খাবার খেতেন। দাদীর কাছে শুনেছি আব্বার জন্য মাসে কয়েকটা ছাতা কিনতে হতো-কারণ আর কিছুই নয়। কোন ছেলে গরিব, ছাতা কিনতে পারে না, দূরের পথ রোদ বা বৃষ্টিতে কষ্ট হবে দেখে, তাদের ছাতা দিয়ে দিতেন। এমনকি পড়ার বইও মাঝে মাঝে দিয়ে আসতেন।
দাদীর কাছে গল্প শুনেছি, যখন ছুটির সময় হতো, তখন দাদী আমগাছের নিচে এসে দাঁড়াতেন। খোকা আসবে দূর থেকে, রাস্তার উপর নজর রাখতেন। একদিন দেখেন তার খোকা গায়ের চাদর জড়িয়ে হেঁটে আসছে পরনের পায়জামা-পাঞ্জাবি নেই। কি ব্যাপার? এক গরিব ছেলেকে তার শত ছিন্ন কাপড়ে দেখে সব দিয়ে এসেছেন।
আমার দাদা-দাদী অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ছিলেন। আমার আব্বা যখন কাউকে কিছু দান করতেন তখন কোনোদিনই বকা ঝকা করতেন না বরং উৎসাহ দিতেন । আমার দাদা ও দাদীর এই উদারতার আরও অনেক নজির রয়েছে।
স্কুলে পড়তে পড়তে আব্বার বেরিবেরি রোগ হয় এবং চোখ খারাপ হয়ে যায়। ফলে চার বছর লেখাপড়া বন্ধ থাকে৷ তিনি সুস্থ হবার পর পুনরায় স্কুলে ভর্তি হন। এই সময় আব্বার একজন গৃহশিক্ষক ছিলেন, তীর নাম ছিল হামিদ মাস্টার । তিনি ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় এবং বহু বছর জেল খাটেন। পরবর্তী পর্যায়ে আব্বা বিভিন্ন সময় যখন জেলে থাকতেন অথবা পুলিশ গ্রেফতার করতে আসত, আমার দাদী মাঝে মাঝেই সেই মাস্টার সাহেবের নাম নিতেন আর কাঁদতেন। এমনিতে আমার দাদা-দাদী অত্যন্ত উদার মনের মানুষ ছিলেন। ছেলের কোনো কাজ কখনো তাঁরা বাধা দিতেন না বরং উৎসাহ দিতেন। অত্যন্ত মুক্ত পরিবেশে আমার বাবার মনের বিকাশ ঘটেছে। প্রতিটি কাজ যখনই যেটা ন্যায়সঙ্গত মনে হয়েছে আমার দাদা তা করতে নিষেধ না করে বরং উৎসাহ দিয়েছেন।
আব্বার একজন স্কুলমাস্টার ছোট্ট একটা সংগঠন গড়ে তোলেন এবং বাড়ি বাড়ি ঘুরে ধান, টাকা, চাল, জোগাড় করে গরিব মেধাবী ছেলেদের সাহায্য করতেন। অন্যতম সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন এবং অন্যদের উৎসাহ দিতেন। যেখানেই কোনো অন্যায় দেখতেন সেখানেই তিনি প্রতিবাদ করতেন। একবার একটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি প্রথম সরকার সমর্থকদের দ্বারা ষড়যন্ত্রের শিকার হন ও গ্রেফতার হয়ে কয়েকদিন জেলে থাকেন।
কৈশোরেই তিনি খুব বেশি অধিকার সচেতন ছিলেন। একবার যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা গোপালগঞ্জে সফরে যান এবং স্কুল পরিদর্শন করেন। সেই সময় সাহসী কিশোর মুজিব তাঁর কাছে স্কুলঘরে বর্ষার পানি পড়ার অভিযোগ তুলে ধরেন এবং মেরামত করাবার অঙ্গীকার আদায় করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
গোপালগঞ্জ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে তিনি কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়তে যান। তখন বেকার হোস্টেলে থাকতেন। এই সময় তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন। হলওয়ে মনুমেন্ট আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন সক্রিয়ভাবে । এই সময় থেকে তাঁর রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু হয়। ১৯৪৬ সালে তিনি বিএ পাস করেন। পাকিস্তান-ভারত ভাগ হবার সময় যখন দাঙ্গা হয়, তখন দাঙ্গা দমনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। কাজ করে যেতেন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে । আমার মেজো ফুফু তখন কলকাতায় থাকতেন। ফুফুর কাছে শুনেছি মাঝে মাঝে অভুক্ত অবস্থায় হয়তো দুদিন বা তিন দিন কিছু না খেয়ে কাজ করে গেছেন । মাঝে মাঝে যখন ফুফু খোঁজ খবর নিতে যেতেন তখন ফুফু জোর করে কিছু খাবার খাইয়ে দিতেন। অন্যায়কে তিনি কোনোদিনই প্রশ্রয় দিতেন না। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে তিনি কখনো পিছপা হননি।
পাকিস্তান হবার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। তখন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে সমর্থন দেন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করতে গিয়ে গ্রেফতার হন। অল্প কয়েকদিন পর মুক্তি পান। এই সময় পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করার কথা ঘোষণা দেন মুহম্মদ আলী জিন্নাহ এবং উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দিলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি বাঙালি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ছাত্রসমাজ এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে । এই আন্দোলনে ১৯৪৯ সালে আমার আব্বা গ্রেফতার হন। আমি তখন খুবই ছোট্ট আর আমার ছোট ভাই কামাল কেবল জন্মগ্রহণ করেছে। আব্বা ওকে দেখারও সুযোগ পাননি।
একটানা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি বন্দি ছিলেন। সেই সময় আমাদের দুই ভাইবোনকে নিয়ে আমার মা দাদা-দাদীর কাছেই থাকতেন। একবার একটা মামলা উপলক্ষে আব্বাকে গোপালগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হয়। কামাল তখন অল্প অল্প কথা বলা শিখেছে। কিন্তু আব্বাকে ও কখনো দেখে নাই, চেনেও না। আমি যখন বার বার আব্বার কাছে ছুটে যাচ্ছি `আব্বা আব্বা` বলে ডাকছি ও শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে। গোপালগঞ্জ থানায় একটা বড় পুকুর আছে, যার পাশে বড় খোলা মাঠ। ঐ মাঠে আমরা দুই ভাইবোন খেলা করতাম ও ফড়িং ধরার জন্য ছুটে বেড়াতাম। আর মাঝে মাঝেই আব্বার কাছে ছুটে আসতাম । অনেক ফুল পাতা কুড়িয়ে এনে থানার বারান্দায় কামালকে নিয়ে খেলতে বসেছি। ও হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, `হাসু আপা তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।` কামালের সেই কথা আজ যখন মনে পড়ে আমি তখন চোখের পানি রাখতে পারি না! আজ ও নেই, আমাদের আব্বা বলে ডাকারও কেউ নেই। ঘাতকের বুলেট শুধু আব্বাকেই ছিনিয়ে নেয় নি; আমার মা, কামাল, জামাল, ছোট্ট রাসেলও রেহাই পায় নি। রেহাই পায় নি কামাল-জামালের নব পরিণীতা বধু সুলতানা ও রোজী, যাদের হাতের মেহেদীর রং বুকের রক্তে মিশে একাকার হয়ে গেছে। খুনিরা এখানেই শেষ করে নি, আমার একমাত্র চাচা শেখ নাসের, তরুণ নেতা আমার ফুফাতো ভাই শেখ মণি, আমার ছোট্ট বেলার খেলার সাথী শেখ মণির অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজুকে খুন করেছে। এই খুনিরা একই সাথে আক্রমণ করেছে আবদুল রব সেরনিয়াবাত (আমার ফুফা), তার তেরো বছরের কন্যা বেবী, দশ বছরের ছেলে আরিফকে, তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর চার বছরের শিশু পুত্র বাবুও খুনিদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। কর্নেল জামিল, যিনি আমার পিতার জীবন রক্ষার জন্য ঘুম থেকে উঠে ছুটে এসেছিলেন-তাঁকেও তারা হত্যা করে। এ কেমন বর্বর নিষ্ঠুরতা? আজও গুলির আঘাতে পঙ্গু হয়ে আছেন আমার মেজো ফুফু ।
সেদিন কামাল আব্বাকে ডাকার অনুমতি চেয়েছিল, আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে আব্বার কাছে নিয়ে যাই। আব্বাকে ওর কথা বলি। আব্বা ওকে কোলে তুলে নিয়ে অনেক আদর করেন। আজ আর তারা কেউই বেঁচে নেই__আজ যে বারবার আমার মন আব্বাকে ডাকার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মায়ের স্নেহ, ভাইদের সান্নিধ্য পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি, কিন্তু শত চিৎকার করলেও তো কাউকে আমি পাব না। কেউ তো আর সাড়া দিতে পারবে না। তাদের জীবন নৃশংসভাবে বুলেট দিয়ে চিরদিনের মতো যে ঘাতকেরা স্তব্ধ করে দিল, তাদের কি বিচার হবে না?
রচনাকাল : ১৩ আগস্ট ১৯৯১
সূত্র: শেখ হাসিনা রচনা সমগ্র ১