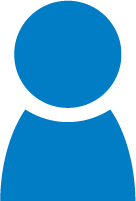বেনজীর-আজিজ কার সৃষ্টি—এ নিয়ে এখন রাজনীতির মাঠ গরম। বিএনপিসহ বিরোধী দলগুলো এখন এই ব্যক্তিদের নিয়ে সরকারকে চাপে ফেলার চেষ্টা করছে। বিএনপি বলছে, বহু বেনজীর আছে সরকারের ভেতর। সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর পদে বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব পালন করা ব্যক্তিদের নিয়ে এই বিতর্ক নতুন নয়। আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে বিতর্কিত ব্যক্তিদের নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েও। পুলিশের সাবেক প্রধান বেনজীর আহমেদ ৬ জুন দুর্নীতি দমন কমিশনে হাজির হননি। আইনজীবীর মাধ্যমে তিনি সময় চেয়েছেন। দুর্নীতি দমন কমিশন তাকে ১৫ দিন সময় দিয়েছে। কিন্তু ১৫ দিনের মধ্যে তিনি দুদকে উপস্থিত হবেন কি না, তা নিয়ে আমি সন্দিহান। সাবেক সেনাপ্রধান আজিজ আহমেদকে নিয়েও চলছে বিতর্ক। বিরোধী দল বলছে, ‘আজিজ-বেনজীর সরকারের সৃষ্টি।’ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলছেন, ‘তারা আওয়ামী লীগের কেউ নন। যোগ্যতার বলেই তারা এসব গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন। তাদের অপরাধের দায় সরকার নেবে না।’ আজিজ-বেনজীর বিতর্কের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরখাস্ত দুই কর্মকর্তার নানা অপকর্মের কাহিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মুখরোচক বিষয় হিসেবে আলোচিত হচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে, এসব স্পর্শকাতর পদে কীভাবে নিয়োগ হয়? নিয়োগ পাওয়ার পর তারা কী করছেন না করছেন, তার খোঁজ কে রাখে? তারা তো দায়িত্বে থেকেই অপকর্ম করেছেন। সরকার তখন তাদের জবাবদিহির আওতায় আনেনি কেন? তখনই যদি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতো, তাহলে হয়তো তারা ‘দানব’ হয়ে উঠত না। আজকে এ ধরনের সমালোচনাও হজম করতে হতো না।
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা হিসেবে গাজী হাফিজুর রহমান লিকু দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিতীয় মেয়াদে এসেও তার চুক্তি নবায়ন করা হয়েছিল। প্রথম মেয়াদে থাকা অবস্থাতেই তাকে নিয়ে নানা বিতর্ক ছিল। তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিলেন—এমন বিস্তর অভিযোগ আছে। সবাই এসব জানত। তার পরও তাকে দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল একই পদে। কেন? লিকুর অপকর্মের কাহিনি কি প্রধানমন্ত্রীকে কেউ জানিয়েছিল? তাকে আর দায়িত্ব দেওয়া ঠিক হবে না, এই পরামর্শ প্রধানমন্ত্রীকে কেউ দিয়েছিল?
শুধু লিকু নয়, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস বিভাগের একজন কর্মকর্তার নজিরবিহীন কাণ্ড পুরো জাতিকে স্তম্ভিত করেছে। ওই কর্মকর্তারও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে থেকে ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, নানা রকম অনিয়ম করার সাহস তারা পান কোত্থেকে? যেখানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী একজন সৎ, নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব। শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বে তিনি একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। এ রকম একজন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যারা কাজ করেন তাদের সততা, নৈতিকতা ও আদর্শিক অবস্থান প্রশ্নাতীত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এসব স্পর্শকাতর পদে দায়িত্ব নিয়ে অনেকে দুর্নীতির দোকান খুলছেন, স্বেচ্ছাচারিতার মহোৎসব করছেন। কীভাবে তারা ‘ফ্রাঙ্কেস্টাইন’ হচ্ছেন, তা খতিয়ে দেখা দরকার। এখনই তাদের চিহ্নিত না করলে ভবিষ্যতে বড় ক্ষতি হবে।
গুরুত্বপূর্ণ পদে ‘ভুল’ ব্যক্তিকে নিয়োগ দিয়ে বিপদে পড়ার ইতিহাস পুরোনো। সব সরকারই চাটুকারদের খপ্পরে পড়েছে। মতলববাজরা সব সরকারকেই বিভ্রান্ত করে গুরুত্বপূর্ণ পদ বাগিয়ে নিয়েছে। এতে ওই সরকারেরই সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে। ভুল ব্যক্তিরা দেশ, জনগণ এবং সরকারের জন্য বিপজ্জনক। ইতিহাসে এটি বারবার প্রমাণিত। কিন্তু আমরা ইতিহাস থেকে শিখি না।
খুনি খন্দকার মোশতাক আজীবন অযোগ্য, কুচক্রী, ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় এই খুনি ষড়যন্ত্র করেছিলেন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে, বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। এ কথা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সবাই জানতেন। কিন্তু তার পরও মোশতাককে স্বাধীনতার পর গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী করা হয়। তাজউদ্দীনকে হটিয়ে তিনিই হন বঙ্গবন্ধুর কাছের মানুষ। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরে খুনি মোশতাক নানা ছলাকলা করে বঙ্গবন্ধুর কাছে আসেন, বঙ্গবন্ধুর কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রকারী কখনোই বঙ্গবন্ধুর আপন লোক ছিলেন না। ইতিহাসে নিকৃষ্টতম ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে যে ইতিহাসধিক্কৃত। খুনি মোশতাক পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট কী করেছেন, তা জাতি জানে। ভুল লোককে বিশ্বাস করলে, গুরুত্ব দিলে পরিণতি কী হয়—খুনি মোশতাক সম্ভবত তার সবচেয়ে জ্বলন্ত উদাহরণ। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিতে বারবার বিভিন্ন ভুল লোককে, অযোগ্য, আদর্শহীন, লোভাতুর, মতলববাজদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে বিপদ ডেকে আনা হয়েছে। এখনো চারপাশে তাকালে দেখা যায় অনেক ভুল লোক নানা ছলাকলা করে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়ে যাচ্ছেন। তাদের নিয়োগ কীভাবে হচ্ছে, তা নিয়ে কেউ কথা বলে না। সবাই গোপনে হা-হুতাশ করে। তারা রাষ্ট্র এবং সরকারের জন্য বিপজ্জনক।
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন জিয়াউর রহমান। হত্যা, ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জিয়া তার অবৈধ ক্ষমতা পোক্ত করতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি নির্বিচারে হত্যা করেছিলেন প্রতিপক্ষকে। কোনো শত্রু রাখতে চাননি। যে তার বিরুদ্ধে ন্যূনতম শব্দ উচ্চারণ করেছে, তাকে তিনি ফাঁসিতে ঝুলিয়েছেন, নির্মমভাবে হত্যা করেছেন। জিয়াউর রহমান তার ক্ষমতাকে নিষ্কণ্টক করতে চেয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি কোনো মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাকে সেনাপ্রধান করেননি। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত এক দুর্নীতিবাজ সামরিক কর্মকর্তাকে সেনাপ্রধান করেছিলেন। কিন্তু সেই দুর্নীতিবাজ এরশাদই জিয়াউর রহমানের ঘাতক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। জিয়াউর রহমান হত্যার পেছনে এরশাদের হাত আছে কি না, তা পরিষ্কার হতো মঞ্জুর হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় পেলে। কিন্তু সেই মামলার রায় আজও হয়নি। এরশাদ তার জীবদ্দশায় এই মামলার রায় বাধাগ্রস্ত করতে সব চেষ্টা করেন। বিএনপিও রহস্যময় কারণে জিয়া হত্যার মূল রহস্য উদ্ঘাটনে আগ্রহ দেখায়নি।
হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বিশ্বাস করতেন আমলাদের। রাজনীতিবিদদের তিনি মোটেই আমলে নিতেন না। আমলাদের ওপর নির্ভর করেই তিনি ৯ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। আমলাদের ক্ষমতাবান করেছিলেন। কিন্তু এরশাদের পতনের পর তার প্রিয় দুই আমলা এম কে আনোয়ার ও কেরামত আলী ডিগবাজি দেন। এরশাদভক্ত এই দুই আমলার বিএনপিতে যোগ দিতে সময় লেগেছে এক সপ্তাহের কম। শুধু আমলা কেন, এরশাদের চারপাশে থাকা কোনো চাটুকারই শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে থাকেনি। ডিগবাজি দিয়েছে। ব্যারিস্টার মওদুদ, শাহ মোয়াজ্জেমের মতো চাটুকাররা বদলে যেতে সময় নেননি।
১৯৯১ সালে খালেদা জিয়া বিশ্বাস এবং আস্থা রেখেছিলেন ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার ওপর। প্রচণ্ড ক্ষমতাবান মন্ত্রী ছিলেন হুদা। বিরোধী দলকে নোংরা, অশ্লীল এবং কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করাই ছিল তার প্রধান কাজ। এই নাজমুল হুদাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফর্মুলা দিয়ে বোমা ফাটান। সরকারকে এক বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। নাজমুল হুদা খালেদা জিয়ার দুর্দিনে তার পাশে থাকেননি। সুদিনে দুর্নীতি করেছেন।
১৯৯৬ সালে দীর্ঘ ২১ বছর পর ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হন। শেখ হাসিনা চেয়েছিলেন দেশকে একটি সুশাসন দিতে, জবাবদিহি নিশ্চিত করতে। এ কারণেই তিনি ১৯৯১ সালে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদকে রাষ্ট্রপতি করেছিলেন। এটি ছিল একটি ভুল সিদ্ধান্ত। এই ভুল ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি করার পরিণাম কী হয়েছে, তা আওয়ামী লীগের অজানা নয়। ২০০১ সালে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের পেছনে বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের ভূমিকা কী ছিল, তা ইতিহাস সাক্ষী। বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের কারণেই আওয়ামী লীগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সবচেয়ে বেশি।
২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় এসেছিল বিপুল বিক্রমে। বিএনপি-জামায়াত জোট ভূমিধস বিজয় পেয়েছিল ২০০১ সালের অক্টোবরের নির্বাচনে। ওই নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর বিএনপি-জামায়াত চেয়েছিল ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে। এ কারণে একের পর এক দলীয়করণ করেছিল গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে। রাষ্ট্রীয় প্রায় সব প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করেছিলেন তারেক রহমান হাওয়া ভবনের মাধ্যমে। নির্বাচন কমিশনকে বানিয়েছিলেন এক তামাশার কেন্দ্র। এম এ আজিজের মতো অযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে বিএনপি নিজেদের ক্ষতি করে। ক্ষমতা পোক্ত রাখার জন্য খালেদা জিয়া, তারেক রহমান সাতজনকে ডিঙিয়ে জেনারেল মইন উ আহমেদকে সেনাপ্রধান করেছিলেন। ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের মতো একজন ব্যক্তিত্বহীনকে রাষ্ট্রপতির পদে আসীন করেছিলেন। খালেদা জিয়া ভেবেছিলেন, এমন চাটুকার বঙ্গভবনে থাকলে তিনি নিরাপদ। এসব করেই বিএনপি তার সর্বনাশ ডেকে আনে। আজ বিএনপি হাজারবার অনুশোচনা করে কেন তারা মইন উ আহমেদকে সেনাপ্রধান করেছিল। ইয়াজউদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি করার বেদনায় অনেকে এখনো আর্তনাদ করে ওঠেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এ ধরনের উদাহরণ অনেক দেওয়া যায়। ভুল ব্যক্তি কখনোই কারও জন্য উপকারী হয় না। তারা নিজের আখের গোছানো ছাড়া কিছুই করতে পারে না। কোনো কাজেই আসে না। ষড়যন্ত্র করে, না হয় বিপদে সটকে পড়ে। ভুল ব্যক্তিরা সবসময় অযোগ্য হয়, আদর্শহীন হয়। তারা কোনো সময় ত্যাগ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত থাকে না, তারা কোনো সময় রুখে দাঁড়ায় না। সুসময়ে তাদের মিষ্টি কথায় মজেছেন তো ঠকেছেন। দুঃসময়ে দেখা যায় তাদের আসল রূপ।
অতীতে ভুল ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ দেওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা আওয়ামী লীগ সরকারের কম নয়। প্রধান বিচারপতি হিসেবে সুরেন্দ্র কুমার সিনহার মতো দুর্নীতিবাজকে নিয়োগ দিয়েছিল আওয়ামী লীগ। এই সিনহাকে এক-এগারোর সময় দুর্নীতির দায়ে বিচারপতি পদ থেকে অপসারণের জন্য বঙ্গভবনে চায়ের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। পরে ড. কামালের কৃপায় তিনি বেঁচে যান। এরকম অবিশ্বাসী, বহুরূপী মানুষ আওয়ামী লীগের চরম ক্ষতি করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার পরও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অযোগ্য, চাটুকার, দুর্নীতিবাজদের নিয়োগদানের প্রতিযোগিতা অব্যাহত আছে। কেউ কেউ মনে করতেই পারেন, গুরুত্বপূর্ণ, স্পর্শকাতর পদের নিয়োগ প্রধানমন্ত্রীর পছন্দেই হয়। কাজেই এখানে অন্য কারও কিছু করার নেই। আমি এ ধরনের বক্তব্যের সঙ্গে একদম একমত নই। এটি প্রধানমন্ত্রীর ইমেজ নষ্টের আরেকটি ষড়যন্ত্র। আমি মনে করি, প্রধানমন্ত্রীর পছন্দ থাকতেই পারে এবং প্রধানমন্ত্রীর পছন্দ-অপছন্দ এসব নিয়োগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রধানমন্ত্রী যাকে পছন্দ করছেন তার ঠিকুজি উদ্ধার করা সংশ্লিষ্টদের দায়িত্ব। কাকে নিয়োগ দেওয়া হবে, তার একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা উচিত। যোগ্যতার পাশাপাশি তার আদর্শিক অবস্থান, সততা এবং অতীত কার্যক্রম নিরীক্ষা জরুরি। যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করছেন, যারা বিভিন্ন সংস্থায় আছেন তাদের প্রধান কর্তব্য হলো সঠিক, যোগ্য এবং আদর্শবান ব্যক্তিরা এসব পদে যাচ্ছেন কি না, তা নজরদারিতে রাখা। চাটুকারিতা আর ‘জি হুজুর’ না করে সঠিক তথ্য প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া। লক্ষ রাখা, এমন কোনো ব্যক্তি কোনো পদে যাচ্ছেন না তো, যার ব্যক্তিগত ইমেজ বা অতীত প্রশ্নবিদ্ধ। পাশাপাশি স্পর্শকাতর পদে দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তিদের নিবিড় পর্যবেক্ষণ জরুরি।
আমি মনে করি, যোগ্যতার চেয়ে একজন ব্যক্তির আদর্শিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। একজন সৎ মানুষ অসৎ ব্যক্তির চেয়ে দায়িত্ববান হন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী কোনো ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুকন্যার জন্য নিরাপদ নয়। রাজাকারের সন্তানরা কোনো দিন আওয়ামী লীগের পক্ষের হবে না। উচ্চপদে বসলেই তারা সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীকে বিব্রত করে অস্বস্তিতে ফেলে। দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ পদে বসালে তা সরকারের জন্যই ক্ষতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। বেনজীর তার সর্বশেষ উদাহরণ। টানা সাড়ে ১৫ বছর ক্ষমতায় আছে আওয়ামী লীগ। দেশে এখন সবাই আওয়ামী লীগ। সরকারের পক্ষে চাটুকারিতা করা মতলববাজদের অভাব নেই। আওয়ামী লীগে ভালোর জন্য দায়িত্বশীল এবং সঠিক সমালোচনাকারীদের সংখ্যা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। দলে সরকারের মধ্যে এখন সত্য বলার লোকের অভাব। সবাই তোষামোদে ব্যস্ত। কেউ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেন না। ভুল ধরিয়ে দেওয়ার মতো সাহসী মানুষ এখন নেই বললেই চলে। এর ফলে অযোগ্য, চাটুকার, দুর্নীতিবাজ, আদর্শহীন মতলববাজরা সরকারের চারপাশে ঢুকে পড়েছে বন্যার পানির মতো। সর্বনাশের বীজ বোনা হচ্ছে সবার অলক্ষ্যে।